ইতিহাস
ইতিহাস
প্রাচীন যুগ তথ্যের স্বল্পতার কারণে প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠন করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। এ অসুবিধা আরও বেশি করে অনুভূত হয় প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায়- অর্থাৎ প্রাচীনতমকাল থেকে খ্রিস্টীয় চার শতকে বাংলায় গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এ সময়ের ইতিহাসের উপাদানের জন্য নির্ভর করতে হয় বৈদিক, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের অপর্যাপ্ত তথ্য ও প্রাপ্তিসাধ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনাদির ওপর। গুপ্তযুগ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য আমরা প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি ও সাহিত্যাকারে লিখিত তথ্যাদি পাই। এসব তথ্যে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।
পটভূমি জানা যায় যে, সর্বপ্রাচীনকালে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত এবং যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী বাস করত সে অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হতো। এভাবে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ় ও গৌড় নামক প্রাচীন জনপদসমূহ অনার্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা এ সব নামের অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেঘনার ওপারে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। এ জনপদের নাম পুরোপুরি বর্ণনাত্মক এবং জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা বর্জিত। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হরিকেল নামে পরিচিত ছিলো। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে অনার্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে এ সকল জনপদের কথা জানা যায়।
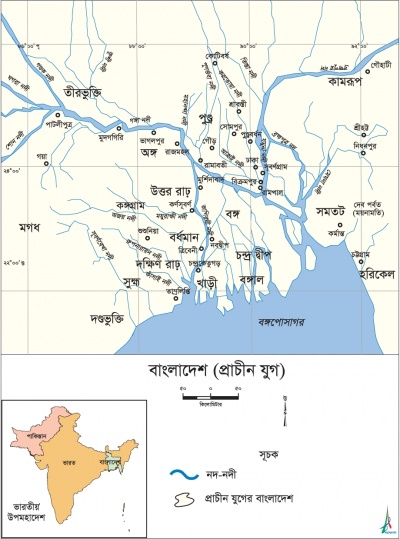
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগে প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর্য-প্রভাব অনুভূত হয়। উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছাতে আর্যদের আরও বেশি সময় লাগে। তাই বাংলার অধিবাসীগণ আর্যায়নের প্রভাব বিলম্বে উপলব্ধি করে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে আর্যরা পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে এবং সমগ্র বাংলাকে আর্যায়িত করতে তাদের প্রায় এক হাজার বছর সময় লাগে। ইতোমধ্যে আর্যদের প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলেও উত্তরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন যাত্রার ফলে আর্য প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে আর্যপূর্ব অর্থাৎ অনার্য উপাদানগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পায়। এমনকি, ক্ষীণ আর্য প্রভাবাধীনেও বাংলার লোকেরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে অনার্য ও আর্যপূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্যাবলীও ধরে রাখতে পেরেছিল।
পাথরের তৈরী হাতিয়ারই মানব বসতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের তৈরী হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ হাতিয়ার ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী কখন প্রথম বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলো তা যথার্থভাবে, এমনকি অনুমানেও নির্ধারণ করা কঠিন। এটা সম্ভবত ঘটেছিল দশ হাজার বছর (বা তারও) আগে। নিষাদ বা অস্ট্রিক কিংবা অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর অনার্য লোকেরাই এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আজকের কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও তিববতি-বর্মি ভাষাভাষী আরও দুটি জাতি বাংলায় বসতি স্থাপন করে।
বর্ধমান জেলার অজয় নদের উপত্যকায় পান্ডু রাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনাদি এবং অজয়, কুনার ও কোপাই নদীর তীরবর্তী অন্যান্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করে। পান্ডু রাজার ঢিবি একটি বাণিজ্যিক বন্দরের ধ্বংসাবশেষ। এ বন্দরের সাথে শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহেরই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত না, বরং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের সাথেও এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। খ্রিস্টীয় চার শতক থেকে পরবর্তী সময়ের প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই এ সময়কার বাংলার ইতিহাসকে ক্রমান্বয়িক আর্যায়িতকরণ ও আর্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগ বলা হয়।
গ্রিক ও ল্যাটিন উৎস থেকে (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) ‘গঙ্গারিডি’ (গ্রিক) বা গঙ্গারিডাই (ল্যাটিন) নামক পূর্ব ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্যের কথা জানা যায়। এ রাজ্য সামরিক দিক থেকে খুবই শক্তিশালী ছিল। পন্ডিতগণ বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গঙ্গার (ভাগীরথী ও পদ্মা) মোহনার কাছে গঙ্গারিডাই-র অবস্থান নির্দেশ করেন।
বগুড়া জেলার মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন পুন্ড্রনগর হিসেবে চিহ্নিত। এ পুন্ড্রনগরে প্রাপ্ত মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি বাংলার অংশ বিশেষের ওপর মৌর্য শাসনের (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) প্রমাণ বহন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় বারো শতক পর্যন্ত সমগ্র প্রাচীন যুগে এ নগরে নগরকেন্দ্রিক প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) উল্লেখ আছে যে, সারা ভারতে বঙ্গের (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) মিহি সুতিবস্ত্র উল্লেখযোগ্য একটি বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য ছিল। গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকগণও (মোটামুটি একই সময়ের) এ কথা উল্লেখ করেছেন। তাই একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বাংলায় মিহি সুতিবস্ত্র বয়নের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কালের। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায় যে, পোড়ামাটির ফলক তৈরিও বাংলার একটি প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্য। খনন কাজের ফলে পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকসমূহ বাংলার এ শিল্পের প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়।
গুপ্ত শাসন খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন থেকে খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান পর্যন্ত সময়ের বাংলার ইতিহাস অস্পষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকের কতকগুলি সুদৃশ্য পোড়ামাটির মূর্তি মহাস্থান, তাম্রলিপ্তি ও চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, শুঙ্গ ও কুষাণ আমলে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি এবং টলেমির বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলার সমগ্র বদ্বীপ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিলো।
ধারনা করা হয়, সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে (খ্রিস্টীয় চার শতক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভের প্রাক্কালে বাংলা কতগুলি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আনুমানিক চার শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রায় সবকটাই সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে চলে আসে। সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালীসহ মেঘনার অপর তীরের এলাকা) তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে থাকলেও করদরাজ্যে পরিণত হয়। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পূর্বাঞ্চলে তাঁর অধিকৃত এলাকাসমূহ সুসংহত করেন। ছয় শতকের শেষের দিকে নামের শেষে ‘গুপ্ত’ উপাধিধারী একজন রাজা কর্তৃক (বৈণ্যগুপ্ত) এ অঞ্চল শাসিত হতো বলে মনে হয়। পাঁচ শতকের গুপ্ত সম্রাটগণের (কুমারগুপ্ত থেকে বুধগুপ্ত) বেশ কয়েকটি তাম্রশাসন উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে। এ থেকে এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শাসনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাম্রশাসনগুলি সুবিন্যস্ত স্থানীয় প্রশাসনের অস্তিত্বেরও সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সম্রাটগণ স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্বের দাবিদার। স্থানীয় প্রশাসন কাঠামোর যে প্রমাণ গুপ্ত তাম্রশাসনগুলিতে পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রথম নিদর্শন। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।
শশাঙ্ক খ্রিস্টীয় ছয় শতকের শেষের দিকে পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের অধীনে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার অংশ বিশেষে গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়। সাত শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্ক গৌড়ে ক্ষমতা দখল করেন। মগধ তার রাজ্যের অংশ ছিল। এ বিষয়ে তেমন কোনো বিরোধ নেই যে, তিনিই ছিলেন বাংলার প্রথম অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজা। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কই প্রথম যিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারকল্পে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি পরবর্তীকালের পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল ও দেবপাল-এর আক্রমণাত্মক উত্তর ভারতীয় নীতির অগ্রদূত। কর্ণসুবর্ণ ছিল তার রাজ্যের রাজধানী।
মাৎস্যন্যায়ম শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য যুগের শুরু হয়। মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে গৌড়ের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এ সময়ে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খ্রিঃ) পর বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়, তার মন্ত্রীরা বলপূর্বক তার রাজ্য দখল করে নেয় এবং চৈনিক দূত ওয়াঙ-হিউয়েন সে অভিযাত্রার পর তিববতের ক্ষমতাধর রাজা শ্রং-সান-গ্যাম্পো কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দুটি নতুন রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে- গৌড় ও মগধে (পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ বিহার) পরবর্তী গুপ্ত বংশ এবং বঙ্গ ও সমতটে (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) খড়গ রাজবংশ। কিন্তু এ দুটি রাজবংশের কোনোটাই বাংলায় শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।
খ্রিস্টীয় আট শতকের প্রথমার্ধে পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কনৌজ রাজ যশোবর্মণের (৭২৫-৭৫২ খ্রি.) আক্রমণ। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য অচিরেই যশোবর্মণের গৌরবকে ম্লান করে দেন। গৌড়ের পাঁচ জন রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন বলে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহন উল্লেখ করেছেন। এ থেকে গৌড়ের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে স্থানীয় প্রধানগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ লিপ্ত হন। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণ রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং তাতে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশ বছর বাংলায় কোনো স্থায়ী সরকার ছিলো না বললেই চলে। সমগ্র দেশ অভ্যন্তরীণ কলহ- কোন্দলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে। গোপাল-এর উত্থানের আগে খ্রিস্টীয় আট শতকের মাঝামাঝি সময়ের রাজনৈতিক অবস্থাকে পাল আমলের একটি লিপিতে (খালিমপুর তাম্রশাসন) মাৎস্যন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অরাজকতা ও নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের আবির্ভাব হয়। পাল তাম্রশাসনে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, গোপাল উল্লিখিত অরাজক অবস্থার (মাৎস্যন্যায়ম) অবসান ঘটান। পাললিপিতে দাবি করা হয় যে, পাল বংশ আট শতকের মাঝামাঝি সময়ে গোপাল কতৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রায় চার শত বছর বাংলা শাসন করে। আঠারো প্রজন্মের সুদীর্ঘ এ শাসনামলে পাল বংশের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের উত্থানপতন পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজাদের শাসন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল। পাল রাজাদের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা যায়- যেমন (১) ধর্মপাল (আ. ৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপাল-এর (আ. ৮২১-৪৬১ খ্রি.) অধীনে পাল বংশের উত্থান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার যুগ। এরপরে আসে (২) স্থবিরতার যুগ (আ. ৮৬১-৯৯৫-১০৪৩) শাসনামলে এ স্থবিরতার যুগের অবসান ঘটে এবং পাল বংশের পুরনো গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কারণে তাকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পাল বংশের শেষ অধ্যায় হলো অবনতি ও অবক্ষয়ের যুগ। অবশ্য রামপাল (আ. ১০৮২-১১২৪), তার তেজোদ্দীপ্ত শাসন দ্বারা সাময়িকভাবে এ অবক্ষয়ের যুগকে রোধ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্য বেশি দিন টিকে থাকেনি। বারো শতকের তৃতীয় চতুর্থাংশে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।
পাল বংশের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল ধর্মপাল ও দেবপালের তেজোদ্দীপ্ত শাসনকাল। এ যুগের পাল রাজারা উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। উত্তর ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁরা পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের সাথে এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
ধর্মপাল ছিলেন একজন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিক্রমশীলা মহাবিহার (কলগং থেকে ৬ মাইল উত্তরে এবং বিহারের ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পূর্বে পাথরঘাটা নামক স্থানে) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। নবম থেকে বারো শতক পর্যন্ত এটি ছিল সমগ্র ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম। পাহাড়পুরের (বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়) সোমপুর মহাবিহার ধর্মপালের অপর একটি বিশাল স্থাপত্য কর্ম।
ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপাল পিতার অনুসৃত আক্রমণশীল নীতি অব্যাহত রাখেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁর সময়েও অব্যাহত থাকে। তিনি হয়ত প্রাথমিক কিছু সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুর্জর-প্রতিহারগণ কনৌজ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়। তবে পাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং উত্তর-পূর্বে কামরূপএর দিকে বিস্তার লাভ করে।
ধর্মপাল ও দেবপালের শাসনামল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির যুগ। এ দুজন শাসক বাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল এবং বিহারে পাল সাম্রাজ্য সংহত করেন। তাঁদের আমলে প্রথমবারের মতো বাংলা উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বাংলা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ সময় সর্বত্র বিজয় সূচিত হয়। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় স্থবিরতার যুগ। এ স্থবিরতা ক্রমশ পাল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়।
পাল সাম্রাজ্যের স্থবিরতা পাঁচজন রাজার শাসনামলব্যাপী একশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ চলে। ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে যে শৌর্যবীর্য ও শক্তির প্রকাশ ঘটে, এ আমলে তা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। এ সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের আদৌ কোনো চেষ্টা করা তো হয়ই নি, বরং বৈদেশিক হামলা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার শক্তিও পাল রাজাদের ছিল না। দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কম্বোজগণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অংশবিশেষে অনেকটা স্বাধীন হয়ে ওঠে। কিছুকালের জন্য পাল সাম্রাজ্য শুধু বিহারের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিলালিপি থেকে কম্বোজ গৌড়পতিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়।
প্রথম মহীপাল (আ. ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের হারানো শৌর্য অনেকটা ফিরিয়ে আনেন এবং সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাংলার হূতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং পালবংশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন। কিন্তু মহীপাল ও রামপালের মধ্যবর্তী রাজাদের রাজত্বকালে এ বংশের গৌরব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। উত্তর ভারতের শক্তিসমূহের পুনঃপুনঃ আক্রমণ (কলচুরি ও চন্ডেলা) পাল রাজাদের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় এ মহীপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭৫-১০৮০ খ্রি.) পালবংশের এ দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ সময় কৈবর্ত প্রধান দিব্য এক সামন্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে (উত্তর বাংলা) স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উত্তর বাংলায় দিব্য-র সাফল্য এ প্রবণতার উজ্জ্বল উদাহরণ।
রামপালের (আনু. ১০৮২-১১২৪ খ্রি.) শৌর্যবীর্য ও শক্তি ছিল পাল বংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোকচ্ছটা। তিনি উত্তর বাংলায় পাল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পালদের রাজ্য বিস্তারের সক্ষমতা প্রমাণ করেন। কিন্তু এ সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এতোই দুর্বল ছিলেন যে সাম্রাজ্যের ক্রমাগত পতন রোধে তাঁরা ব্যর্থ হন। এ পরিস্থিতিতে সম্ভবত পালদের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা বিজয়সেন শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পান এবং বারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে পালদের বাংলা থেকে উৎখাত করেন। এভাবে বিজয়সেনের নেতৃত্বে বাংলায় এক নতুন শক্তি সেনবংশের উদ্ভব হয়। সেনগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে আগত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।
প্রায় চারশ বছর স্থায়ী পাল বংশের শাসন বাংলায় একটি সুদৃঢ় সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ বয়ে আনে। এ শাসন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। পালগণ একটা সফল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাদের ভূমিভিত্তিক সাম্রাজ্য কৃষি নির্ভর ছিল। পাল অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন গুরুত্ব পায় নি। ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্ভবত দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ কিংবা বড়জোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে প্রসারিত ছিল। আট শতকের পর তাম্রলিপ্তি বন্দরের পতন সমুদ্রপথে বাংলার বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব থেকে পালদের বঞ্চিত করে।
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের দীর্ঘ শাসন বাংলায় এক ধরনের উদার ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করে। এ আমলে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রীতি ও সহাবস্থান লক্ষ করা যায়।
পাল যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডল সহিষ্ণুতা নীতি এবং পারস্পরিক সহ-অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এ মনোভাব বাংলার ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।
শিল্পকলার ক্ষেত্রে বহুবিধ সাফল্যের জন্যও পালযুগ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্যরীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে। এ স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের পরবর্তী স্থাপত্য কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বাংলার পোড়ামাটির ফলক শিল্প এ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। পালদের ভাস্কর্য শিল্প পূর্ব-ভারতীয় শিল্প রীতির একটা বিশেষ পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়। পাল যুগেই বাংলার ভাস্করগণ তাদের শৈল্পিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। এ যুগের সাহিত্য কর্মের অতি সামান্য অংশই কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তথাপি উত্তর বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম এক অসামান্য শ্লোক সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে আছে। রামচরিতমের শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি দ্ব্যর্থবোধক। পরবর্তী যুগের কাব্য সংকলনে দশ ও এগারো শতকের কবিদের রচিত অনেক শ্লোক স্থান পেয়েছে। এ যুগে তালপাতায় লেখা কিছু সচিত্র বৌদ্ধ পান্ডুলিপি চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। এ সকল সাফল্যের বিষয় বিবেচনা করে পাল যুগকে সংগত কারণেই বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ হিসেবে গণ্য করা যায়।
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ প্রাচীন যুগে বেশ কিছুকাল ধরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল বলে মনে হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর থেকে শুরু করে সেনবংশের উত্থান পর্যন্ত বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল উত্তর ও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে আত্তীকৃত ছিল না, যদিও সময়ে সময়ে তা করার চেষ্টা করা হয়েছে।
খ্রিস্টীয় ছয় শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের উদ্ভব হয়। ছয়টি তাম্রলিপিতে এ রাজ্যের তিনজন রাজা যথাক্রমে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শশাংকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা নির্ণয় করা যায় না। এ অঞ্চলে ‘ভদ্র’ উপাধিধারী একটি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল বলে পন্ডিতগণ ধারণা করেন।
খ্রিস্টীয় সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরবর্তী গুপ্তগণ যখন গৌড়ের শাসন ক্ষমতা দখল করেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়গ বংশের অভ্যুদয় ঘটে। খড়গ বংশের রাজাগণ তিন পুরুষ ধরে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) শাসন করেছেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত-বাসক (কুমিল্লার নিকটবর্তী বড় কামতা)। তাম্রশাসন থেকে লোকনাথ ও শ্রীধারণ রাত নামক দুজন অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত প্রধানের কথা জানা যায়। এঁরা খ্রিস্টীয় সাত শতকে সমতটের কয়েকটি অংশে রাজত্ব করেন।
খ্রিস্টীয় আট শতকে দেব রাজবংশএর অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা একটি বড় ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁদের রাজধানী ছিল ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের দেবপর্বত (শহরটির সঠিক অবস্থান এখনো নির্ণয় করা যায় নি)। চারপুরুষ ধরে দেববংশীয় রাজাগণ (শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব) সমতট শাসন করেন। তাঁরা ছিলেন উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং বিহারের উপর কর্তৃত্বকারী প্রথম দিকের পাল রাজাদের সমসাময়িক। দেব বংশীয় রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতী অঞ্চল বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ময়নামতিতে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার (বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দবিহার ও ভোজ বিহার উল্লেখযোগ্য। দেববংশের রাজাগণ এগুলি তাঁদের রাজধানী দেবপর্বতের সন্নিকটে নির্মাণ করেছিলেন। ক্রুশাকৃতির কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণের শৈল্পিক রীতি পূর্ণতা পায় পাহাড়পুর বিহারে। এ নির্মাণ কৌশল শুরু হয়েছিল ময়নামতী অঞ্চলে। এখানে এ রীতির আদি ও অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ পরিলক্ষিত হয়। ময়নামতীতে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উন্নতমানের মৃৎফলকও রয়েছে। ময়নামতীতে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ এ অঞ্চলে ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করছে।
খ্রিস্টীয় নয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় হরিকেল রাজ্যের উদ্ভব হয়। সম্ভবত চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হরিকেল রাজাদের পর চন্দ্র রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে। এ বংশের শাসকগণ পাঁচ পুরুষ ধরে (ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র) প্রায় ১৫০ বছর (আনু. ৯০০-১০৫০ খ্রি.) শাসন করেন। সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটসহ বঙ্গ ও সমতটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঢাকার দক্ষিণে বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজধানী। চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাঁরা ছিলেন উত্তর ও পশ্চিম বাংলার সমসাময়িক পাল রাজাদের সমকক্ষ। শ্রীচন্দ্র ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময়ে চন্দ্র সাম্রাজ্য সীমান্তের ওপারে কামরূপ (আসাম) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁর তাম্রশাসনগুলিতে গৌড়ের সাথে যে সংঘাতের উল্লেখ রয়েছে তা সম্ভবত এ অঞ্চলের কম্বোজ বংশীয় রাজাদের সাথে ঘটেছিল। এ সংঘর্ষ সম্ভবত পরোক্ষভাবে প্রথম মহীপালের রাজত্বের শুরুর দিকে পালগণ কর্তৃক তাদের পিতৃরাজ্য (রাজ্যম্ পিত্র্যম্) পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দিয়েছিল।
এগারো শতকের শেষ দিকে পাল সাম্রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ এর সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মণ রাজবংশীয়রা এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। বর্মণ রাজবংশএর পাঁচজন রাজা (জাতবর্মণ, হরিবর্মণ, শ্যামলবর্মণ, ভোজবর্মণ) একশ বছরের কিছু কম সময় (আনু. ১০৮০-১১৫০ খ্রি.) রাজত্ব করেন। বর্মণরা সেনদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বর্মণগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদেরও রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূল দিয়ে পরিচালিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা এর সত্যতা প্রমাণ করে। নয় থেকে এগারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আরব বণিক ও নাবিকদের বিবরণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে সমন্দর বন্দর দিয়ে সমুদ্র পথে ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের কথা জানা যায়। আরবদের বর্ণিত এ সমন্দর বন্দরটিকে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি কোনো স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ এ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে রৌপ্য মুদ্রা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় রূপার পাত সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এ আমলের তথ্যাদি থেকে নৌযান নির্মাণের কারখানার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এ থেকে ক্রমপ্রসারমান সামুদ্রিক বাণিজ্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।
সেন বংশীয় শাসন বারো শতকের শেষের দিকে বিজয়সেন সেন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্নাটের বাসিন্দা। পাল সম্রাট রামপালের শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের একজন সামন্ত নরপতিরূপে বাংলার রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। রামপালের পর পাল বংশের অবক্ষয়কালে বিজয়সেন স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মণদের পরাভূত করেন এবং অতঃপর উত্তর ও পশ্চিম বাংলা থেকে পালদের বিতাড়িত করেন। উত্তর বিহার এবং তদসন্নিহিত অঞ্চলেও তিনি স্বীয় অধিকার বিস্তারের প্রয়াস পান। তেরো শতকের প্রারম্ভে মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পালগণ কোনোক্রমে দক্ষিণ বিহারে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।
সেনগণ বাংলায় একশ বছরেরও বেশিকাল ধরে (আনু. ১০৯৭-১২২৩ খ্রি.) কর্তৃত্ব করেন। এ বংশের পাঁচজন নৃপতি (বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন) এ সময়ে রাজত্ব করেন। এটা লক্ষণীয় যে, মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর আক্রমণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অংশবিশেষে সেন শাসনের অবসান ঘটায় (১২০৪ খ্রি.)। লক্ষ্মণসেন পিছু হটে এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাদের অধিকৃত অঞ্চলে চলে আসেন। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দু পুত্র এখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। আরও লক্ষণীয় যে, বিজয়সেন বর্মণ ও পালদের ক্ষমতাচ্যুত করে সমগ্র বাংলাকে একক শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন এবং ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং এক অর্থে বলা যায় যে, শুধু সেন আমলেই সমগ্র বাংলা একক শাসনাধীনে আসে। পূর্ববর্তী চার শতক ধরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বাংলার ইতিহাসে গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলেছিল। চন্দ্র ও বর্মণদের রাজধানী বিক্রমপুর সেনদের সময়েও রাজধানী ছিল। এ বংশের প্রথম তিনজন রাজা বিজয়সেন (আনু. ১০৯৭-১১৬০ খ্রি.), বল্লালসেন (আনু. ১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) ও লক্ষ্মণসেন (আনু. ১১৭৮-১২০৬ খ্রি.) ছিলেন এ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। শেষ দুজন নরপতির (বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেন) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অত্যন্ত সীমিত অঞ্চলের উপর আধিপত্য ছিল। সেন রাজাগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদের রাজত্বকাল বাংলায় হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্ণপ্রথার কঠোরতার ওপর ভিত্তি করে বল্লালসেন গোঁড়া হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা বিন্যস্তকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। যে সমাজ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আবহে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রীতির মধ্যে এগিয়ে চলছিল সে সমাজে হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে সমাজ ব্যবস্থার এ পরিবর্তনকে ধরা যেতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, সেনদের দ্বারা গোঁড়া হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বৌদ্ধ ধর্মের জন্য ছিল একটা প্রচন্ড আঘাত। এ কারণেই সঠিকভাবে বলা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এ আঘাত দূরদেশ থেকে আগত ইসলামের মাধ্যমে আসেনি, এসেছে নিকটবর্তী ধর্মের ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। এ কথা সত্য যে, মুসলমানদের বাংলায় আগমনের আগেই বৌদ্ধ ধর্ম মারাত্মকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। বাংলায় এ হিন্দু- বৌদ্ধ বৈরিতা এবং সেন আমলে হিন্দু গোঁড়া ধর্মমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ ঘটনা পরম্পরা বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকতে পারে।
অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও সেন আমল গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সেন রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কিছুটা তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট আবহের কারণে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চার সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বাংলার অবদানের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে জয়দেব এর গীতগোবিন্দ। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব ছিলেন অন্যতম অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁর সভায় অপরাপর গুণী ব্যক্তি ছিলেন কবি ধোয়ী (পবনদূত প্রণেতা), উমাপতিধর, গোবর্ধন (আর্যা-সপ্তশতীর লেখক) ও শরণ। এ পাঁচজনকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন হিসেবে গণ্য করা হয়।
শ্রীধরদাসের সংকলন সদুক্তিকর্ণামৃত সমকালীন ও পূর্ববর্তী যুগের কাব্যকৃতির রত্নভান্ডার বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এতে রয়েছে দশ থেকে বারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা। এ যুগে ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহনের আবির্ভাব ঘটে। রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন লেখক হিসেবে কম কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। এ যুগেই রচিত হয় হলায়ূধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব। এ ছাড়াও এযুগে আরও সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বারো শতকের সেন শাসনাধীন বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।
এ যুগে শৈল্পিক কৃতিত্বের অপর ক্ষেত্র হচ্ছে ভাস্কর্য। সেনযুগে বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। বাংলার ভাস্কর্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র ধারাও এ যুগে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। [আবদুল মমিন চৌধুরী]
গ্রন্থপঞ্জি RC Majumdar (ed), History of Bengal, vol-1, Dhaka, 1948; Abdul Momin Chowdhury, Dynastic History of Bengal, Dhaka, 1968; RC Majumdar, History of Ancient Bengal, Kolkata, 1974; নিহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৪০০ বা.স।
সুলতানি শাসন তেরো শতকের সূচনালগ্নে (১২০৪-০৫) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তবে এর অনেক আগে থেকেই বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল; অবশ্য সে যোগাযোগের স্বরূপ ছিল বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় এবং তা উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।
বখতিয়ার খলজীর সামরিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করার পর ভারতে মুহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবকের সাথে বদাউনে গিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তার সৈন্যবাহিনী আরও শক্তিশালী করেন এবং ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে বাংলা আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মনসেনের সাময়িক রাজধানী নদীয়া অধিকার করেন। এখানে অগাধ ধনসম্পদ, অগণিত পরিচারক-পরিচারিকা ও বহুসংখ্যক হাতি বখতিয়ারের হস্তগত হয়। অতঃপর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী গৌড় দখল করে সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং প্রায় দু বছরকাল বিজিত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।
বখতিয়ার তার রাজ্যে এক ধরনের গোত্রীয় সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করেন। অধিকৃত এলাকাকে তিনি কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করে সেগুলির ভার তার বিশ্বস্ত সেনাপতিদের ওপর অর্পণ করেন। এ প্রশাসনিক ইউনিট ইকতা নামে পরিচিত ছিল এবং এ ইকতার শাসনকর্তাকে মুকতা বলা হতো। প্রশাসনিক বিন্যাস ছাড়াও বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নামাযের জন্য মসজিদ, মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা এবং ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে সুফিদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।
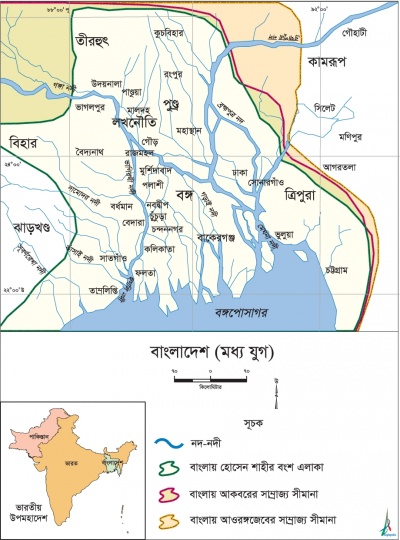
অতপর বখতিয়ার তিববত অভিযানে বের হন। তিববত অভিমুখে রওনা হওয়ার পূর্বে বিজিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিকালের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। উড়িষ্যা (জাজনগর) থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি মুহম্মদ শিরাণ খলজীকে সীমান্ত এলাকা প্রহরার জন্য একদল সৈন্য সহ বীরভূম জেলার লখনৌতির অভিমুখে প্রেরণ করেন। ত্রিহুত ও অযোধ্যার দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি ইওজ খলজীকে পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্ব দেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রংপুরের উপকণ্ঠে তিনি আলী মর্দান খলজীকে মোতায়েন করেন। অবশ্য এ তিববত অভিযানে বখতিয়ারের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ব্যর্থ অভিযান শেষে চরম হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেবকোটএ ফিরে এসে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন অথবা আলী মর্দান খলজী কর্তৃক নিহত হন।
সমসাময়িক ও আধুনিক তথ্যাদির ভিত্তিতে বখতিয়ারের অধিকৃত রাজ্যের ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। অযোধ্যার মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত তাঁর মূল জায়গির ছাড়াও দক্ষিণ বিহার এবং উত্তর বিহারে গঙ্গা নদীর উত্তর তীরবর্তী ভূখন্ড তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। বাংলা অঞ্চলে রাজমহল, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলাগুলি তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া নদী লখনৌতি রাজ্যের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করে।
প্রাথমিক যুগ (১২০৬-১২২৭) আকস্মিক মৃত্যুর কারণে বখতিয়ার তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যেতে পারেন নি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর আলী মর্দান, হুসামউদ্দীন ইওজ ও মুহম্মদ শিরাণ খলজী সিংহাসন দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।
১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওজ খলজীর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাপর্ব বলে অভিহিত করা যায়। বখতিয়ারের মৃত্যু এতই আকস্মিক ছিল যে, তিনি এ সময়ে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কোনো মনোযোগই দিতে পারেননি। ফলে আলী মর্দান, হুসামউদ্দীন ইওয়াজ এবং মুহম্মদ শীরন সিংহাসনের জন্য নিজেরাই কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে প্রথম ছয় বছর বখতিয়ারের সেনাপতিদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলে। ১২১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যন্ত ছিল ইওয়াজ খলজীর শাসনকাল। মুসলিম বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক ইওয়াজ খলজী পরিকল্পিতভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনের সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার চেষ্টা করেন। গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীর শাসনকাল বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই মুসলিম বাংলার প্রথম শাসক যিনি সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম পরিকল্পিতভাবে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান এবং তিনিই যুদ্ধ ও রণকৌশলের ধরনে নতুন দিকে সূত্রপাত করেন। তার গৃহীত নীতির ফলে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলিম শাসন সুসংহত হয়।
ইওয়াজ খলজীর অধীনস্থ মুসলিম রাজ্য দক্ষিণ বিহার ছাড়াও বাংলার এক ব্যাপক অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উত্তরে মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলা, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পাবনা, নদীয়া, ও যশোর জেলার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম ও বর্ধমান জেলা তার রাজ্যভুক্ত ছিল। (জেলাগুলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব পরিসীমায় বোঝানো হয়েছে)।
দিল্লি সালতানাতের অধীনে লখনৌতি রাজ্য (১২২৭-১২৮৮/৮৯) ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওয়াজের মৃত্যু এবং ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়কে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ও সুসংহত করণের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন লখনৌতির শাসনকর্তা হিসেবে ইওয়াজের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বাংলা ও বিহারের সাথে তার অধীনস্থ অযোধ্যা প্রদেশকে সংযুক্ত করেন এবং লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার অধীনস্থ রাজ্যের বিস্তৃতি এবং নিজে দিল্লি সুলতানের পুত্র বিধায় স্বভাবতই সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তার শাসনাধীন রাজ্যের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইলতুৎমিশ তাকে ‘মালিক-উস-শরক’ (প্রাচ্যের নৃপতি) উপাধি দেওয়ার ফলে এ গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। দেড় বছর কাল তিনি এ সম্মিলিত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর আমলে ইওজ খলজী সূচিত রাজ্য সংহতকরণ নীতি অব্যাহত থাকে।
১২২৯ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর দওলত শাহ বিন মওদুদ নামক একজন সেনানায়ক ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আববাসীয় খলিফা, দিল্লির সুলতান এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খলজী সহকর্মীর এ কর্মকান্ড মেনে না নিয়ে বিদ্রোহী হন এবং দওলত শাহকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন (১২২৯-৩০)। তিনিও ক্ষমতায় বেশি দিন থাকতে পারেননি। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ লখনৌতি আক্রমণ করে তাকে দমন করেন। অতঃপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন মাসুদ জানীকে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। মালিক সাইফউদ্দীন আইবককে পৃথকভাবে বিহারে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।
বলবনী বংশ (১২৮৮/৮৯-১৩০০) বুগরা খান এবং কায়কাউস ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। বুগরা খানের শাসনামলের শেষের দিকে বাংলার মুসলিম রাজ্য চারটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো- বিহার, উত্তর বাংলার লখনৌতি-দেবকোট অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাতগাঁও-হুগলি অঞ্চল এবং পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও অঞ্চল। বুগরা খানের পর তাঁর কনিষ্ট পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন (১২৯১-১৩০০)। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম আধিপত্য বাংলার পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। তিনি বং-এর রাজস্ব থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
কায়কাউস প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। সম্ভবত তিনি সাম্রাজ্যকে বিহার ও লখনৌতি নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ফিরুজ আইতিগীন এবং লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন জাফর খান বাহরাম আইতিগীন। লখনৌতি প্রদেশ তখন উত্তরে দেবকোট হতে দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উভয় প্রদেশের শাসনর্কতা ‘সিকান্দর-ই-সানী’ (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) উপাধি গ্রহণ করেন। কায়কাউস নিজেও জাঁকাল উপাধি ধারণ করেন। এ সকল উপাধি বাংলার জৌলুস ও ক্ষমতার পরিচায়ক।
শামসুদ্দীন ফিরুজ ও তাঁর বংশ (১৩০১-১৩২৪) কায়কাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরুজ (১৩০১-১৩২২) লখনৌতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে ভুলক্রমে বলবনী বংশের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। বখতিয়ারের পরে তাঁর শাসনকালেই মুসলিম রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটে। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে লখনৌতি রাজ্য বিহার, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে লখনৌরে সীমাবদ্ধ ছিল। কায়কাউসের রাজত্বকালে হুগলি জেলার সাতগাঁও ও বঙ্গের সোনারগাঁও অভিমুখে যে রাজ্যবিস্তার প্রক্রিয়া শুরু হয় ফিরুজ শাহের শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর রাজত্বকালে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিজিত হয়।
ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ফিরুজ তাঁর পুত্র শিহাবউদ্দীন বুগদাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে যান। কিন্তু শিহাবউদ্দীনের ভাই গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে সিংহাসনচ্যূত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মনে হয় তিনি নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম ছাড়া অন্যান্য ভাইদের হত্যা করেন। নাসিরউদ্দীন কোনো ক্রমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান এবং কয়েকজন আমীরের মাধ্যমে দিল্লির সাহায্য চেয়ে পাঠান।
তুগলক হস্তক্ষেপ এ ঘটনা বাংলায় হস্তক্ষেপের জন্য তুগলকদের কাঙিক্ষত সুযোগ এনে দেয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দিল্লির সুলতান তাঁর পালক পুত্র বাহরাম খান ওরফে তাতার খান ও নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমের অধীনে এক শক্তিশালী বাহিনী গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে বাহাদুর পরাজিত ও বন্দি হন। গিয়াসউদ্দীন তুগলক বাংলায় মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। সমগ্র রাজ্যকে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এ তিনটি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। তিনি নাসিরুদ্দীন ইবরাহিমকে যৌথ নামে মুদ্রা মুদ্রণের বিশেষ ক্ষমতাসহ লখনৌতির শাসনকর্তা পদে বহাল করেন। বাহরাম খান সোনারগাঁও ও সাতগাঁয়ের গভর্নর নিযুক্ত হন। বন্দি বাহাদুরকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।
গিয়াসউদ্দীন তুগলকের উত্তরাধিকারী মুহম্মদ বিন তুগলক বাংলার শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি বাহাদুরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে সোনারগাঁও-এ বাহরাম খানের সঙ্গে যুগ্ম-শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাহাদুরের ওপর আরোপিত শর্ত ছিল যে, তার ছেলেকে জিম্মি হিসেবে দিল্লিতে প্রেরণ, নিজ ও সুলতানের যৌথনামে মুদ্রা প্রচলন এবং উভয়ের নামে খুতবা পাঠ করতে হবে। কদর খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। সাতগাঁওকে পৃথক প্রদেশ হিসেবে ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।
গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর তার পুত্রকে দিল্লিতে প্রেরণ ব্যতীত অপর সকল শর্তই পূরণ করেন। ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিজ ও তুগলক সুলতানের যৌথনামে সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু রাখেন। অবশ্য ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার আনুগত্য অস্বীকারের চেষ্টা করেন। বাহরাম খান অন্যান্য আমীরদের সহায়তায় বাহাদুরকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দিল্লিতে পাঠান হয় এবং ভবিষ্যত বিদ্রোহীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্য দিল্লিতে প্রকাশ্যে তা ঝুলিয়ে রাখা হয়।
পরবর্তী দশ বছর (১৩২৮-১৩৩৮) লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও যথাক্রমে কদর খান, ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়া ও বাহরাম খান কর্তৃক শাসিত হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে তাঁরই বর্ম-রক্ষক ফখরউদ্দীন সোনারগাঁও-এ ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। এ ঘটনা ক্ষমতা দখলের নতুন ধারাবাহিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় যার ফলে বাংলায় ইলিয়াসশাহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করে যা দুশ বছর অব্যাহত ছিল (১৩৩৮-১৫৩৮)। [দেলওয়ার হোসেন]
গ্রন্থপঞ্জি JN Sarkar (ed), History of Bengal, vol. II, Dhaka, 1948; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাসের সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৭৭; Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. 1A, Riyadh, 1985; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (বাংলা), কলকাতা, ১৯৮৮।
ইলিয়াসশাহী শাসন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ ১৪১২ থেকে ১৪৩৫/৩৬ পর্যন্ত তেইশ বছরের বিরতিসহ প্রায় দেড় শ’ বছর (১৩৪২-১৪৮৭) বাংলা শাসন করে। ইলিয়াসশাহী আমল নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সালতানাত সুসংহত হয় এবং এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ আমলে মুসলিম শাসনব্যবস্থা একটি রূপ লাভ করে। শিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। মুসলিম শাসকগণ স্থানীয় জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে দেশের শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশ গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এভাবে বিদেশি মুসলিম শাসন বাঙালি মুসলিম শাসনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া এ আমলেই শুরু হয়। সর্বোপরি সমগ্র রাজ্য যা এতদিন একক কোনো নামে পরিচিত না হয়ে বঙ্গ, গৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে পরিচিত ছিল তা বাঙ্গালাহ নামে অভিহিত হয়।
ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হাজী ইলিয়াস ছিলেন সিজিস্তানের একজন অভিজাত। প্রথমে তিনি দিল্লির মালিক ফিরুজের অধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি সাতগাঁওএর শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মালিক পদে উন্নীত হন এবং ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তিনি সাতগাঁয়ের অধিকর্তা হন। অতঃপর হাজী ইলিয়াস আলী মুবারকের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘর্ষে (১৩৩৯-১৩৪২ খ্রি.) অবতীর্ণ হয়ে অবশেষে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন আবুল মুজাফফর ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাংলায় ইলিয়াস শাহী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ সালতানাত প্রায় দেড় শত বছর স্থায়ী হয়েছিল (১৩৪২-১৪৮৭ খ্রি.)। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ ফকরউদ্দীন মুবারক শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করতে সক্ষম হন। ফলে সমগ্র বাংলা তাঁর কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ইলিয়াস শাহ একজন দৃঢ়চেতা ও দক্ষ শাসক ছিলেন এবং তার বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বলে তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালাহ, শাহ-ই-বাঙালিয়ান ও সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় ষোলো বছর রাজত্ব করার পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।
ইলিয়াস শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকান্দার শাহ প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তিনি পান্ডুয়ার নিকটবর্তী গোয়ালপাড়ায় তাঁর পুত্র আজম শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ১৩৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজম শাহ ‘সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ’ উপাধি ধারণ করে ৭৯২ হিজরিতে (১৩৯১-৯২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহন করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। আইনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ৮১৩ হিজরিতে (১৪১০-১১ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র সাইফুদ্দীন হামজাহ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস (৮১৩ হি./১৪১০-১১ খ্রি-৮১৪ হি/১৪১২ খ্রি.) বাংলা শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং তারই প্ররোচনায় সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন তার প্রভুকে হত্যা করে নিজেই বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। যখন এ ঘটনা ঘটছিল, তখন সম্ভবত মুহম্মদ শাহ বিন হামজাহ শাহ বাংলার কোনো এক অঞ্চলে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। সম্ভবত তিনি তাঁর অবস্থান রক্ষা করতে পারেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রাজা গণেশ ও শিহাবউদ্দীনের কাছে পরাজিত হন। এভাবে ইলিয়াস শাহী শাসনের বিরতি ঘটে।
সুলতান সাইফউদ্দীন হামজা শাহের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ ৮১৪ হিজরি (১৪১২ খ্রি.) থেকে ৮১৭ হিজরি (১৪১৪ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ ও রাজা গণেশের মধ্যকার সুসম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। শিহাবউদ্দীন রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে আটক রেখে তার ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি সুলতান শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ উপাধি ধারণ করে নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজা গণেশ সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করেন (৮১৭হি./১৪১৪ খ্রি.)। শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ কোনো রকমে দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান এবং সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কিন্তু রাজা গণেশ তাকে আক্রমণ করে নিহত করেন এবং নিজেই ৮১৭ হিজরিতে (১৪১৪ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।
রাজা গণেশের বংশ বাংলার শাসক হয়েই রাজা গণেশ মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে পান্ডুয়ার সুফি-দরবেশ নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এতে রাজা গণেশ ভীত হয়ে দরবেশের কাছে এ মর্মে আবেদন জানান যেন ইবরাহিম শর্কী বাংলা থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। রাজা গণেশ তার পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে এবং তাকে সিংহাসনে বসাতে সম্মত হলে দরবেশ তার প্রস্তাব মেনে নেন। ৮১৮ হিজরিতে (১৪১৫ খ্রি.) এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ইবরাহিম শর্কী দরবেশের অনুরোধে বাংলা ত্যাগ করেন।
যদু জালালউদ্দীন আবুল মুজাফফর মুহম্মদ শাহ নামে ৮১৮ হিজরিতে মুদ্রা চালু করেন। তিনি মাত্র এক বছর ও কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাঁর পিতা রাজা গণেশ ৮১৯ হিজরিতে (১৪১৬-১৭ খ্রি.) সিংহাসন দখল করে নেন এবং জালালউদ্দীনকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করান। এবারে রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেব উপাধি ধারণ করে ৮২১ হিজরি (১৪১৮ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ভ্রাতা যদু কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন (৮২১ হি./১৪১৮ খ্রি)। এ সময়ে যদু পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে প্রায় পনের বছর রাজত্ব করে ৮৩৭ হিজরিতে (১৪৩৩ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান জালালউদ্দীনের পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ৮৩৯ হিজরি (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আহমদ শাহের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ সকলকেই হতাশ করে। এ অবস্থায় নাসির খান ও সাদী খান নামে তার দুজন ক্রীতদাস তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেন। এর অব্যবহিত পরেই নাসির খান ও সাদী খান সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হন এবং এ বিবাদে নাসির খান তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি মাত্র কয়েকদিন বাংলা শাসন করার সুযোগ পান। শীঘ্রই অভিজাতবর্গ তার ক্ষমতার বিরোধিতা করেন এবং তাকে হত্যা করেন।
পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশ শামসুদ্দীন আহমদ শাহের হত্যার পর সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাতবর্গ সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসিরউদ্দীনকে ৮৩৯ হিজরিতে (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এভাবে ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সুলতান নাসিরউদ্দীন ‘আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহ’ উপাধি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে প্রায় চবিবশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ৮৬৪ হিজরিতে (১৪৫৯-৬০ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ন্যায়বান, উদার, বিদ্বান ও বিজ্ঞ সুলতান ছিলেন। হাবশী ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এ কারণে তিনি বহুসংখ্যক হাবশীকে নিয়োগ দান করেন। এ হাবশী ক্রীতদাসরা বাংলার রাজনীতিতে খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বারবক শাহ ৮৭৯ হিজরিতে (১৪৭৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পরে তার পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ সিংহাসনে বসেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শরীয়া আইন কঠোরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধানসমূহ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য আলেমদের নির্দেশ দেন। ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর (সম্ভবত ৮৮৬ হি./১৪৮১ খ্রি.) অভিজাতগণ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সিকান্দরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কয়েকদিন নামমাত্র রাজত্ব করার পর অভিজাতগণ তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের পুত্র ফতেহ শাহকে সিংহাসনে বসান। তিনি জালালউদ্দীন মুজাফফর ফতেহ শাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে হাবশী ক্রীতদাসগণ দরবারে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দরবারের গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ পদ দখল করে নেয়। ফতেহ শাহ বারবক নামে তার এক ক্রীতদাস কর্তৃক ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) নিহত হন। ফতেহ শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটে।
১৩৪২ থেকে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ, নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, ইউসুফ শাহ ও জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ-এর আমলে বাংলার সালতানাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বলতে গেলে, সমগ্র বাংলা এবং পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিকটবর্তী কিছু এলাকা বাংলা সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।
ইলিয়াস শাহী বংশ যথানিয়মে পরম্পরা অনুসারে যোগ্য শাসকদের তৈরি করেছে। এ শাসকগণ তাদের সহিষ্ণুতা ও শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রায় সত্তর বছর শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল তাদের বড় কৃতিত্ব; পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল আরও বড় কৃতিত্বের কাজ। এ সবই তাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে।
গ্রন্থপঞ্জি Ziauddin Barani, Tarikh-i-Firuz Shahi, Calcutta, 1862; Yahiya bin Ahmad, Tarikh-i-Mubarak Shahi, Calcutta, 1931; আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭; ABM Shamsuddin Ahmed, Bengal under the Rule of the Early Iliyas Shahi Dynasty, Unpublished Thesis, Dhaka University, Dhaka, 1987।
হাবশী শাসন জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালের শেষের দিকে হাবশী ক্রীতদাসগণ বাংলার শাহী দরবারে একটি বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হয়। ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে শাহজাদা নামে এক হাবশী খোজা ও ক্রীতদাসদের নেতা ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করে। এভাবে বাংলায় হাবশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলায় হাবশী (আবিসিনীয়) শাসন ৮৯৩ হিজরি (১৪৮৭ খ্রি.) থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় চার জন সুলতান পর পর দেশ শাসন করেন। তারা হলেন বারবক শাহ শাহজাদা, সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ, দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ও শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ।
বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে শাহজাদা সুলতান বারবক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অপসারণের নীতি ছিল তার শাসনকালের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ নীতি তাকে রক্ষা করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মালিক আন্দিল কর্তৃক নিহত হন। বারবক শাহের রাজত্বকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়।
মালিক আন্দিল অভিজাতদের সম্মতিতে ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৮৭ খ্রি.) সাইফউদ্দীন আবুল মুজাফফর ফিরুজ শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ গরীব ও নিঃস্বদের প্রতি তাঁর বদান্যতা ও করুণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ন্যায়বান, উদার ও হিতৈষী শাসক ছিলেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং প্রজাদের জন্য শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করেন। তিনি শিল্পকলা ও স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে মনে হয় যে, তিনি বাংলার এক বিশাল অঞ্চল শাসন করেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর তিনি ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯০ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন কিংবা গোপনে নিহত হন।
সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহের পর দ্বিতীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হাবাশ খান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। এতে সিদি বদর দীউয়ানা নামে অপর এক হাবশী ক্রীতদাস ঈর্ষান্বিত হন এবং শেষ পর্যন্ত পাইকদের সহায়তায় তিনি হাবাশ খান ও মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন। মাহমুদ শাহ মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেছিলেন।
দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের হত্যার পর সিদি বদর ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯০ খ্রি.) শামসুদ্দীন আবু নছর মুজাফফর শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য তিনি গৌড় নগরের অনেক পন্ডিত, ধার্মিক ও অভিজাতদের হত্যা করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি তাঁর স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিরাট অংশ ভেঙ্গে দেন এবং সৈন্যদের বেতন হ্রাস করেন। নির্মম হলেও মুজাফফর শাহ একেবারে হূদয়হীন অত্যাচারী শাসক ছিলেন না। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সুফি-দরবেশদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৮৯৬ হিজরি (১৪৯০ খ্রি.) থেকে ৮৯৯ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় তিন বছর স্থায়ী ছিল। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সমগ্র উত্তর বাংলা এবং বাংলার সীমান্তবর্তী বিহারের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মুজাফফর শাহের নিপীড়নমূলক শাসনের ফলে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি হারান। ফলে তার আরব বংশোদ্ভূত প্রধান উজির সৈয়দ হুসাইনের নেতৃত্বে এক গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয়। মুজাফফর শাহ নিহত হন এবং তাঁর হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হাবশী শাসনের অবসান ঘটে। [এ.বি.এম. শামসুদ্দীন আহমদ]
হোসেনশাহী শাসন বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে হোসেনশাহী আমল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ আমল ছিল বাংলার স্বাধীন সালতানাতের খ্যাতির সর্বোচ্চ পর্যায়। রাজ্যের সম্প্রসারণ, প্রশাসনের সুস্থিতকরণ এবং ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় অগ্রগতি দ্বারা হোসেনশাহী শাসনামল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ আমলে উত্তর ভারত থেকে বাংলার চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে সহায়তা করে। সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ এ আমলকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিল। এটা ছিল স্থানীয় প্রতিভার পুস্পোদ্মম, যা পূর্ববর্তী আমলে ছিল অবদমিত। এ আমলে বাংলায় নতুন ধরনের কোনো শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও চারুকলা ও স্থাপত্যের বিদ্যমান নমুনা ছিল এ আমলের শিল্প বিকাশের উন্নত নিদর্শন এবং এতে এ আমলের সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে। হোসেনশাহী শাসকরা তাদের বহিরাগত পরিচয় পরিহার করে নিজেদের স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার চেষ্টা করেন এবং এ সময়ে দেশিয় সংস্কৃতির ধারায় মুসলিম মানসের কমবেশি বিকাশ ঘটে। এ সময়ে বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। এ আমলের শেষ দিকে মুগল শাসন শুধু বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য তখন শুরু হওয়ার পথে। পরবর্তী শতকগুলিতে দেশের জীবনধারার রূপদানকারী নতুন শক্তিগুলির প্রাথমিক কিছু লক্ষণ এ আমলে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে অর্থে এ আমল ছিল বাংলার ইতিহাসের গঠনযুগ।
হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহকে হত্যা করে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মুজাফফর শাহের অধীনে উজির পদে নিয়োজিত ছিলেন। মুজাফফরের জীবনের করুণ পরিণতিতে হোসেনের ভূমিকা ছিল এবং ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে নেতৃস্থানীয় অভিজাতগণ তাকে সুলতান নির্বাচিত করে। তার রাজত্বকালে বাংলার সালতানাতের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কামরূপ ও কামতা জয় করে তার সৈন্যবাহিনী আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আরও উত্তরে অগ্রসর হয়। উড়িষ্যারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন এবং ‘কামরূপ ও কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ী’ আখ্যান তার মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেন। তিনি ত্রিপুরার একাংশ তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। চট্টগ্রাম ছিল তার রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ প্রতিনিধিদল বাংলায় আসে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেনের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। তার রাজত্বকালে দেশে নিরবছিন্ন শান্তি বিরাজ করছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্ত তাকে ‘নৃপতি-তিলক’, ‘জগৎ-ভূষণ’ ও ‘কৃষ্ণ-অবতার’ রূপে আখ্যাত করেছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তার নীতি ছিল সহিষ্ণু ও উদার। তিনি তাদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন এবং তাদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র নুসরত সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ উপাধি ধারণ করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে নুসরত ত্রিহুত (উত্তর বিহার) পর্যন্ত তার রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। পরাজিত কতিপয় আফগানকে আশ্রয়দান করলেও পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভের পর পূর্ব ভারতের দৃশ্যপটে অবতীর্ণ বাবুরএর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ তিনি চতুরতার সঙ্গে পরিহার করতে চেষ্টা করেন। নুসরত তার নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাহমুদ লোদী কর্তৃক আফগান দলপতিদের নিয়ে গঠিত মুগল-বিরোধী জোটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পরিহার করেন। কিন্তু এসব কৌশল সত্ত্বেও নুসরত বাবুরের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে পারেন নি। গোগরার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নুসরত বাবুরের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলাকে আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। দৌরাহ্র যুদ্ধে (১৫৩১) নুসরত আফগানদের সঙ্গে যোগদানে বিরত থাকেন। হুমায়ুন এ যুদ্ধে মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বাধীন আফগানদের পরাজিত করেন। নুসরতের রাজত্বকালে কামরূপ ও কামতার ওপর বাংলার নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত অক্ষুণ্ণ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে ব্যস্ততার কারণে আসামের প্রতি নজর দেওয়ার কোনো সুযোগ তার হয় নি। বাংলার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে পর্তুগিজদের দুটি প্রতিনিধিদল নুসরতের দরবারে আসেন। তার রাজত্বকালে পর্তুগিজরা বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ছিল। চট্টগ্রামের দূরবর্তী উপকূলীয় এলাকায় চট্টগ্রামের গভর্নরদের বহুবার পর্তুগিজ হুমকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।
নুসরত শাহ মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি তার ভাইদের এবং আফগানদের সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করেন। খ্যাতিমান পিতার তুলনায় তাকে দুর্বল চিত্তের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাও মনে রাখা উচিত। আফগান রাজনীতির অনিশ্চিত প্রকৃতি ও মুগলদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তার অবস্থানগত দুর্বলতার প্রধান কারণ। নুসরত বাংলা সাহিত্যের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সাহিত্যে বারবার তার নাম উল্লেখিত হয়েছে। কথিত আছে যে, গৌড়ে তার পিতার সমাধি জিয়ারতকালে তার এক ক্রীতদাস তাকে হত্যা করে।
নুসরত শাহের রাজত্বকালে হোসেনশাহী শাসনে যে অবক্ষয় ও ভাঙন শুরু হয়, তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে তা চরমে পৌঁছে। নুসরত তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহমুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেও অভিজাতদের একটি অংশ তার তরুণ পুত্র ফিরুজকে আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ |আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ]] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে (১৫৩২)। ফিরুজের রাজত্বকাল মাত্র নয় মাস স্থায়ী হয়েছিল (১৫৩২-৩৩) এবং তিনি তার পিতৃব্য মাহমুদের হাতে নিহত হন। ছন্দোবদ্ধ প্রেমকাহিনী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা শ্রীধর বারবার ফিরুজের নাম এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগের উল্লেখ করেছেন।
শেষ হোসেনশাহী সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ তার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কেন্দ্রবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে রোধ করতে পারেন নি। দূরবর্তী অঞ্চলের গভর্নরগণ কার্যত স্বাধীন হয়ে ওঠেন। তার সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের শাসনকর্তা খোদাবখশ কর্ণফুলি নদী ও আরাকান এর পর্বতমালার মধ্যবর্তী এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে সামন্ত রাজার ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাহমুদের নাজুক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ত্রিপুরার রাজা বাংলার অংশবিশেষ দখল করে তার রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালান। শেরশাহ শূর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বাংলা অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত খোদাবখশ সম্ভবত আরাকান ও ত্রিপুরাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
বিহারে শেরখান শূরের উত্থানের সময় থেকেই মাহমুদের সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সমস্যা শুরু হয়। মাহমুদ বিহারে শেরখানের প্রতিদ্বন্দ্বী জালাল খান লোহানীর পক্ষে বিহার আক্রমণের জন্য ইবরাহিম খানের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠান। সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) ইবরাহিম পরাজিত হন এবং জালাল খান মাহমুদের শরণাপন্ন হন। এতে করে বিহারে শেরখানের কর্তৃত্বের পথ প্রশস্ত হয়। গুজরাটে হুমায়ুনের ব্যস্ততার (১৫৩৫) সুযোগে শেরখান ভাগলপুর পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেন। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে শেরখান তেলিয়াগড়ে উপস্থিত হন। পর্তুগিজ সৈন্যদের সহায়তায় মাহমুদের সৈন্যদল তাকে প্রতিহত করে। ঝাড়খন্ড হয়ে শেরখান গৌড়ের উৎকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। মাহমুদ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং শেরখান তার রাজ্য তেলিয়াগড়ি-এ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মাহমুদ পর্তুগিজদের স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকারসহ চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওএ তাদের দুর্গ ও বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দান করেছিলেন। এতে বাংলায় পর্তুগিজদের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।
১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারে শেরখানের অবস্থান ছিল নিরাপদ এবং তিনি তেলিয়াগড়ে গিরিপথ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। দ্বিতীয়বারের মতো শেরখান গৌড়ে উপস্থিত হন এবং বার্ষিক কর হিসেবে মাহমুদের কাছে এক বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেন। মাহমুদ এতে অসম্মতি জানালে শেরখান গৌড় অবরোধ করেন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আফগানরা গৌড় দখল করে নেয়। শেষ মুহূর্তে মাহমুদ শেরখানের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌড়ে আফগানরা তার দু পুত্রকে হত্যা করলে মাহমুদ মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটে। মাহমুদ তখনকার বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপুর্ণ যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর এক যুগের সূচনা হয়। সতেরো শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলার জনজীবনে এ অবস্থা বিরাজ করছিল। [আবদুল মমিন চৌধুরী]
গ্রন্থপঞ্জি JN Sarkar (ed), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলকাতা, ১৯৬২; আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৮৭; MR Tarafdar, Husain Shahi Bengal, 2nd revised ed, Dhaka, 1999।
আফগান শাসন (১৫৩৯-১৫৭৬) বাংলায় ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে মুগল বিজয়ের ফলে। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুগল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খানের কাছ থেকে শেরখানের (যিনি চৌষার যুদ্ধে জয়লাভের পর শেরশাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন) বাংলা দখলের বহু পূর্বেই আফগানরা বাংলার সুলতানদের অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। জৌনপুরের শার্কি সুলতানদের মতো বাংলার সুলতানগণও বিভিন্ন বিভাগে আফগানদেরকে নিয়োগ করতেন। সুতরাং শেরশাহ যখন বাংলা অধিকার করেন, তখন আফগানেরা অচেনা বলে বিবেচিত হয়নি। ফলে তারা সিংহাসনে নিজেদের লোক দেখতে পান- প্রথমে বাংলা ও বিহারে এবং পরে ভারতীয় সাম্রাজ্যে।
শাসনকর্তাদের (গভর্নরস) অধীনে বাংলা (১৫৩৯-১৫৫৩) সাম্রাজ্য গড়ার কাজে বাংলার গুরুত্বকে যথার্থভাবে অনুধাবন করে শেরশাহ বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য প্রথম গভর্নর খিজির খানকে চাকরিচ্যুত করেন এবং চট্টগ্রামসহ বাংলাকে ছোট ছোট কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে প্রত্যেক ইউনিটকে এক একজন মুক্তার অধীনে ন্যস্ত করেন। তিনি সকল মুক্তার ওপর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজী ফজীলতকে নিয়োগ করেন। শেরশাহের পরিকল্পনা খুবই ফলপ্রসূ হয় এবং আফগানরা বাংলায় এমন স্থায়ীভাবে নিবাসিত হয়।
শেরশাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩) সমগ্র বাংলার উপর তার দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থাকে আরও কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টায় তিনি কাজী ফজীলতকে পদচ্যুত করেন এবং সেখানে শাসনকর্তা হিসেবে তার আত্মীয় মুহম্মদ খান শূরকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত করেন। নতুন শাসনকর্তা, (১৫৪৬-১৫৪৮) খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান খান ওরফে কালিদাস গজদানী নামক এক বিদ্রোহীকে কঠোরভাবে দমন করার পদক্ষেপ নিয়ে তার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে যখন অযোগ্য আদিল শাহ ইসলাম শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরুজ শাহকে হত্যা করে দিল্লির আফগান সিংহাসন দখল করেন, তখন বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ শূর জবরদখলকারী কর্তৃত্বকে মেনে নেয়াটাকে মর্যাদা সম্পন্ন নয় বলে মনে করে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। বাংলায় কররানী আফগানদের উত্থানের মধ্য দিয়ে তার বংশের রাজত্বকালের অবসান ঘটে।
কররানী বংশ (১৫৬৩-১৫৭৬) ষোলো শতকের তৃতীয় চতুর্থাংশে পূর্ব ভারতে নতুন আফগান বংশের উত্থানপতন পরিলক্ষিত হয়। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে শেরশাহের উত্থানের সময় থেকে শেরশাহ, ইসলাম শাহ প্রমুখ আফগান সুলতানদের অমাত্য ও সাহিব-ই-জামা (Sahib-e-Jama) জামাল খান কররানীর পুত্র তাজ খানের ছিল দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক জীবন। রাজনৈতিক খ্যাতির শীর্ষে তার উত্থান হয়েছিল, যখন তিনি ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে জবরদখলকারী তৃতীয় গিয়াসউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বদাউনী তাকে আফগানদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন।
তাজ খানের পরে তার ভাই সুলায়মান কররানী ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে (৯৮০ হি.) তার মৃত্যুপর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় তার দক্ষতা তার জন্য যশ ও গৌরব বয়ে এনেছিল। সুলায়মানের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে গৌড় থেকে তান্ডায় তার রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ, গৌড়ের আবহাওয়া মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। উচ্চাভিলাষী সুলায়মান কররানী ফতেহ খান বাতনীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। ফতেহ খান দক্ষিণ বিহারে প্রভাবশালী ছিলেন এবং তার সদরদপ্তর ছিল রোহটাস দূর্গে। কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে সুলায়মান ফতেহ খানকে শান্ত করেন। ফতেহ খান সুলায়মানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং এ চাকরিতে তিনি সুলায়মানের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণদন্ডে দন্ডিত না হওয়া পর্যন্ত তার অধীনে নিয়োজিত ছিলেন।
১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৭৫ হি.) মুকুন্দদেবকে পরাজিত করে উড়িষ্যা বিজয় ছিল সুলায়মান কররানীর আর একটি গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ সামরিক কীর্তি। অতঃপর সুলায়মান কররানী ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার অধিকার করেন। আফগানরা তেজপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং কুচরাজধানীর চতুর্পার্শ্বস্থ ও সীমান্ত এলাকার অনেক স্থান দখল করে।
সুলায়মান কররানীর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা মুগলদের সাথে তাঁর সম্পর্ক আড়াল করে রাখে। তিনি একজন দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কুশলী পরিচালক ছিলেন। মুগলদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আকবরের নিকট নানা ধরনের উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এমন কি, তিনি বাহ্যিকভাবে মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করে বলতেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ এবং তাঁর নামে মুদ্রা প্রবর্তন করবেন।
পূর্বভারতের আফগান সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ সুলতান সুলায়মান কররানী সম্ভবত ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে (৯৮০ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তান্ডায় সমাহিত আছেন। তাঁর পুত্র বায়েজীদ কররানী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি লোদী খান কররানীসহ সকল নেতৃস্থানীয় অভিজাতবর্গের সহযোগিতায় সবরকমের রাজকীয় ক্ষমতা ধারণ করেন। যুবরাজ হিসেবে বায়েজীদ ইতঃপূর্বে ভবিষ্যতের জন্য অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি নির্যাতন ও হয়রানি করার নীতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে দরবারের নির্যাতিত ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হয়ে একমাসের মধ্যেই তাকে হত্যা করে এবং তাঁর ছোট ভাই দাউদ খান কররানীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।
দাউদ কররানী ক্ষমতা লাভ করেই দেখতে পান যে, আফগান অভিজাতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিরোধ বিরাজমান। তিনি প্রথমত ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাঁর শাসন শুরু করেন। দাউদ তাঁর চাচা খাজা ইলিয়াস কররানীর পুত্র হাঁসুকে (রাজহত্যাকারী) শাস্তি দেন। তিনি নিজ নামে খুতবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রবর্তন করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এতে সম্রাট আকবর খুবই অসন্তুষ্ট হন। দাউদ কররানী প্রভাবশালী অভিজাত লোদী খানকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি আরও একজন ক্ষমতাশালী অভিজাত গুজর খানকে শান্ত করেন। যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে বায়েজীদ কররানীর পুত্রকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। দাউদ খান কররানী তার সেনাপতি লোদী খানকে হত্যা করেন। লোদীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর পুত্র ইসমাইলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মুগল শাসনকর্তা মুনিম খানের নিকট নিয়ে যান। পরিস্থিতির এ নাটকীয় পরিবর্তন মুনিম খানকে পাটনা অবরোধ করার সুযোগ করে দেয়। এ অবস্থায় দাউদ কররানী অনতিবিলম্বে পাটনা পরিত্যাগ করেন এবং গর্হি, তান্ডা ও সাতগাঁও-এর মধ্য দিয়ে দূরবর্তী উড়িষ্যার কটকে পৌঁছেন। মুগল সৈন্যবাহিনী অতি দ্রুত তাকে সেখানে অনুসরণ করে। ফলে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠে। কটকের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তুকারয়ের যুদ্ধের (৩ মার্চ, ১৫৭৫ খ্রি.) অবসান ঘটে। এ চুক্তি অনুসারে দাউদ খান মুগল সামন্ত হতে সম্মত হন এবং মুগলদের বিরুদ্ধে আর কখনও বিদ্রোহ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন।
মুনিম খানের মৃত্যুর কারণে বিখ্যাত বৈরাম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র /ভাগিনেয় হোসেন কুলী খান নতুন শাসনকর্তা হিসেবে মুগল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রবলবাবে উত্তেজিত ছিল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধ দাউদের ভাগ্যকে রুদ্ধ করে দেয়। তিনি বন্দি হন এবং তাকে খান-ই-জাহানের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। খান-ই-জাহান তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। [মোহাম্মদ ইব্রাহিম]
গ্রন্থপঞ্জি JN SARKAR (ed.), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; M.A. Rahim, History of the Afghans in India, Karachi, 1961; M. IBRAHIM, Afghan Rule in Eastern India (1535-1612), Unpolished Ph.D Thesis, Aligarh Muslim University, India, 1986।
মুগল শাসন (১৭৫৭ পর্যন্ত)' ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে খান জাহানের কাছে কররানী আফগান সুলতান দাউদ খান এর পরাজয়ের পর বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দাউদ খানের বিরুদ্ধে খান জাহানের জয় লাভের পর মুগলরা বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর-এর সুবাহদার ইসলাম খান চিশতি সমগ্র বাংলা (চট্টগ্রাম ছাড়া) মুগলদের কর্তৃত্বাধীনে আনেন।
দাউদ খানের পরাজয়ের সঙ্গেই বাংলায় সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু এর অর্থ কোনোভাবেই এ নয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কতিপয় সামরিক দলপতি ও ভূঁইয়াদের কেউ কেউ রাজা উপাধি গ্রহণের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দলপতি হিসেবে তাঁরা মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত ভূঁইয়ারা ছিলেন সর্বাধিক খ্যাত।
রাজা, ভূঁইয়া ও জমিদার, যারা মুগলদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক, প্রায় ৩৬ জন। বহু দশক ধরে বারো ভূঁইয়ারা মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করেন। বারো-ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান যিনি ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অন্য ভূঁইয়াদের নিয়ে জোট গঠন করেন এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব দেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বারো ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুগলদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাহদার ইসলাম খান চিশতির নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহিনীর নিকট শেষ পর্যন্ত তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।
জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের পর ইসলাম খান অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক প্রতিরোধকারীদের দমনের কাজ শুরু করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর বারো ভূঁইয়ারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে পরাজিত ভূঁইয়া ও দলপতিদের তাদের রাজ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তার পরিবর্তে তাদের মুগলদের অধীনে কাজ করতে প্রণোদিত করা হয়। ভুলুয়া জয় করে এর শাসক রাজা অনন্ত মানিক্যকে ফেনী নদীর অপর তীরে আরাকানের দিকে বিতাড়িত করে ইসলাম খান সিলেটের খাজা উসমান খান আফগানের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। এর সাথেই মুগল শক্তির সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে।
জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দুবছর বাংলার প্রশাসনকে বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় মগদের হামলার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানএর প্রথম সুবাহদার কাসিম খান জুইনি (নূরজাহানের বোন মনিজা বেগমের স্বামী) ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের দখল থেকে হুগলি পুনরুদ্ধার করেন। মুগল কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শর্তে পরে তাদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। সুবাহদার ইসলাম খান মাশহাদি কামরূপ সীমান্তে অহোম রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবেলা করে তাঁকে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেন। এরপর আসেন শাহজাদা শাহ সুজা। তিনি বিশ বছর (১৬৩৯-১৬৫৮) সুবাহদার ছিলেন এবং সে সময় এ প্রদেশ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে তাঁর চার পুত্র দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এদের প্রত্যেকেই অন্যের দাবি অস্বীকার করে সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন। শুজা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রথমে দারা ও পরে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হয়ে তিনি বাংলা থেকে পালিয়ে আরাকানের রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সংগৃহীত ধনরত্ন হস্তগত করার উদ্দেশ্যে আরাকানের রাজা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।
শাহ শুজাকে অনুসরণ করে বাংলায় আসা মীরজুমলাকে সুবাহদার নিযুক্ত করা হয়। ঢাকায় অবস্থান গ্রহণ করে মীরজুমলা কুচবিহারের রাজার বিদ্রোহ দমন করতে এবং উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কামরূপের একাংশ দখলকারী আসামের রাজাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। তিনি কুচ রাজধানী কমলাপুর দখল করে রাজা প্রাণনারায়ণকে বিতাড়িত করেন এবং এরপর আসামের দিকে অগ্রসর হন। অহোম রাজা তাকে প্রতিহত করতে পারেন নি। সুবাহদার অহোম রাজধানী গড়গাঁও দখল করে সামনের দিকে অগ্রসর হন। বর্ষাকালে তিনি গড়গাঁওয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যাভাবে মুগলরা কষ্ট ভোগ করে এবং বহু সৈনিক ও ঘোড়া মারা যায়। বর্ষার সময় অহোম সেনাবাহিনী তাদের নাজেহালও করে। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করাকে মীরজুমলা বিচক্ষণতা বলে মনে করেছিলেন। সন্ধিটি তাঁর অনুকূলে ছিল; অহোম রাজা তাঁকে সোনা, রুপা এবং তাঁর রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু ফেরার পথে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ মীরজুমলা খিজিরপুর এর (নারায়ণগঞ্জের নিকট) অদূরে মৃত্যুবরণ করেন।
পরবর্তী সুবাহদার নিযুক্ত হন শায়েস্তা খান। নতুন সুবাহদার ছিলেন নূরজাহান-পরিবারের সদস্য। তিনি ছিলেন আসফ খানের পুত্র এবং শাহজাহানের সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভাই, সম্রাট আওরঙ্গজেবএর মাতুল। তিনি শুধু সম্ভ্রান্ত বংশীয়ই ছিলেন না, একজন ফারসি কবি, পন্ডিত ও দক্ষ সেনাপতিও ছিলেন। বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণের আগে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন। এক বছরাধিককাল বিরতিসহ তিনি ২২ বছর বাংলা শাসন করেন। এ বিরতিকালে আজম খান কোকা (ফিদাই খান) ও শাহজাদা মুহম্মদ আজম পরপর সুবাহদার হয়েছিলেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শায়েস্তা খান প্রথম বাংলায় আসেন এবং ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর দায়িত্বের প্রথম মেয়াদকাল পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর কার্যকাল শুরু হয় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর এবং ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তা শেষ হয়। প্রথম বার বাংলায় আসার সময়ই তাঁর বয়স ৬৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং ২৪ বছর পর বাংলা ত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। ষাটোর্ধ্ব বয়স হলেও তিনি বলবত্তার সঙ্গে বাংলা শাসন করেন, তবে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী ইংরেজ বণিক উইলিয়ম হ্যাজেস তাঁকে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। শায়েস্তা খান তাঁর সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বয়োপ্রাপ্ত ও গুণবান পুত্রকে নিয়ে আসেন। এঁরা দেশ শাসনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পুত্ররা ছিলেন বুজুর্গ উমেদ খান, আকিদাত খান, জাফর খান, আবু নসর খান ও ইরাদাত খান। তারা বিভিন্ন সরকার বা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং পুত্ররা পিতার শাসন কাজের অংশীদার হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন করেন।
চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য বাংলায় শায়েস্তা খান সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। সুযোগ পেলেই আরাকানের মগ রাজা পর্তুগিজ জলদস্যুদের সহযোগিতায় মুগলদের বাংলা প্রদেশ আক্রমণ করতেন। উপরন্তু, পর্তুগিজ জলদস্যুরা উপকূলীয় অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং পুরুষ নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করত। পর্তুগিজদের দস্যুতা ছিল এক নিয়মিত হুমকি। কাজেই আরাকানের রাজার কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান, উপকুলীয় অঞ্চলকে জলদস্যুদের হুমকি থেকে রক্ষা এবং একে সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করা ছিল শায়েস্তা খানের কর্মসূচি। অল্পকাল পরে তিনি চট্টগ্রাম জয় করে সমগ্র অঞ্চলকে আরাকানিদের হামলা থেকে মুক্ত করেন।
শায়েস্তা খানের স্থলাভিষিক্ত হন আওরঙ্গজেবের পালক ভাই খান জাহান বাহাদুর উপাধিধারী মীর মালিক হোসেন। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক এবং সুবাহদার পদমর্যাদার যোগ্য ছিলেন না। তাঁর দায়িত্বের মেয়াদকাল ছিল এক বছরেরও কম। শাহজাহানের আমলের প্রধান আমীর বিখ্যাত আমীর উল-উমারা আলী মর্দান খানের পুত্র ইবরাহিম খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর আমলে বেনারসের শোভা সিংহ বিদ্রোহী হয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে লুটতরাজ শুরু করেন। উড়িষ্যার এক আফগান দলপতি রহিম খান তার সঙ্গে এ লুটতরাজে যোগ দেন এবং দুজনে রাজমহল পর্যন্ত বর্ধমান, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় লুটতরাজ ও হামলা চালান। তারা হুগলি দুর্গ আক্রমণ করলে তথাকার ফৌজদার পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। সুবাহদার ইবরাহিম খান ছিলেন শান্ত স্বভাবের লোক। বিদ্রোহীদের দমন করতে তিনি তেমন কিছুই করতে পারেন নি। সে যাই হোক, চুঁচুড়া থেকে ওলন্দাজ কোম্পানি প্রথম বিদ্রোহীদের পথরোধ করে এবং তাদের হুগলি থেকে বিতাড়িত করে। সুবাহদার ইবরাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান মুগলদের পক্ষে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি বর্ধমান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণার পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইবরাহিম খানকে অপসারণ করে স্বীয় পৌত্র শাহজাদা আজিমউদ্দীনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। পরবর্তীকালে আজিম-উস-শান উপাধিতে ভূষিত আজিমউদ্দীন ছিলেন শাহজাদা মুহম্মদ মুয়াজ্জমের পুত্র। শাহজাদা মুয়াজ্জম ‘শাহ আলম বাহাদুর শাহ’ উপাধি ধারণ করে পরবর্তীকালে (১৭০৭-১৭১২) সম্রাট হয়েছিলেন। ঢাকা যাওয়ার পথে আজিমউদ্দীন প্রথমে বর্ধমানে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দেন এবং উদ্বাস্ত্ত জমিদারদের পুনর্বাসিত করেন। বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় আজিমউদ্দীন সম্ভাব্য যে-কোন পন্থায় অর্থ সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। নগদ অর্থ উপহারের বিনিময়ে তিনি প্রথমে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম তিনটি মালিকদের কাছ থেকে ক্রয়ের অনুমতি দান করেন। এভাবে তিনি পরবর্তী অর্ধ-শতকের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।
দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর বিবাদ আজিম-উস-শান এর সুবাহদারির এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর উপস্থিতি পরিহার করার জন্য মুর্শিদকুলী খান তাঁর দীউয়ানি মুর্শিদাবাদে এবং পরবর্তীকালে সুবাহদার তাঁর নিজামত পাটনায় স্থানান্তরিত করেন। এভাবে ঢাকা মুগল বাংলার রাজধানীর গৌরব হারিয়ে ফেলে। বহু পন্ডিত প্রমাণ করেছেন যে, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় সরকারি প্রতিনিধিদের দফতর স্থানান্তরের ফলেই ঢাকা ও এর সংশ্লিষ্ট পূর্ব বাংলার উন্নতি হ্রাস পেতে থাকে।
সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুর্শিদকুলী খান বাংলা সুবাহর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। তিনি উড়িষ্যার সুবাহদার এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এ তিনটি প্রদেশের দীউয়ান এবং মুর্শিদাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কটক এ পাঁচটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহ আলম বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তাঁকে দক্ষিণ ভারতে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আবার বাংলার দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়। এ সময় থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলায় অবস্থান করেন। তিনি বাংলার অর্থনীতিকে গতিশীল করে তুলেছিলেন এবং রাজকীয় খাজনা নিয়মিত প্রদান করতেন। এ কারণে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাহদার হন। তাঁর সুবাহদারি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল। বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ নিতে আসা বিদেশিরা দেশের আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিল।
কেন্দ্রকে নিয়মিত কর প্রদান করলেও মুর্শিদকুলী খান প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নওয়াব হয়ে ওঠেন। ফলে মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ বাংলার নওয়াব হন। কিন্তু অচিরেই তাঁর পিতা সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই ওই বছর বাংলার নওয়াব হন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় সুজাউদ্দীন খান তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে মসনদের জন্য মনোনীত করে যান। সরফরাজ ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খান তাঁকে উচ্ছেদ করেন।
আলীবর্দী খানের শাসনামল প্রতি বছর মারাঠা হামলার জন্য স্মরণীয়। মারাঠাদের প্রভাবাধীন মীর হাবিবকে কার্যত উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়ে এবং মারাঠাদের চৌথ হিসেবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন। আলীবর্দী ছিলেন একজন দয়ালু ও কুশলী শাসক। তিনি নীতিপরায়ণ মানসিক প্রকৃতি গড়ে তোলেন এবং সমকালীন অন্যদের মতো তিনি লাম্পট্য ও মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন না। জগৎ শেঠ ব্যাংক-মালিক পরিবারের উত্থান ছিল তাঁর শাসনকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ এর মাধ্যমে সংঘটিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এ শেঠরাই ছিলেন মূলত দায়ী। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে আলীবর্দী খান মারা যান। তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।
বাংলার সিংহাসনে বসার সময় নতুন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। শীঘ্রই তিনি নিজেকে স্থানীয় ও বিদেশি শত্রু বেষ্টিত দেখতে পান। নিজ পরিবারেই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন তাঁর মায়ের বড় বোন ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নেসা)। পুর্ণিয়ায় বসবাসকারী তাঁর খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ ছিলেন তাঁর অপর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া ছিলেন আলীবর্দীর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান। তিনি ছিলেন আলীবর্দীর এক সৎ-বোনের স্বামী। সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল জগত শেঠের পরিবার। এরা বাংলার অর্থ-বাজার নিয়ন্ত্রণ করত এবং দরবারে তাদের বহু সমর্থক ছিল। সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যারা অনেকটা প্রকাশ্যেই নওয়াবকে উপেক্ষা করত। নওয়াবের কোনো অনুমতি না নিয়েই তারা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম সুরক্ষিত করে তুলছিল এবং অন্যান্য সামরিক প্রস্ত্ততি নিচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম অপরাধী ও দেশের আইন ভঙ্গকারীদের এক নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়েছিল।
ইংরেজদের আইনের অধীনে আনতে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে ফুলতায় চলে যায় এবং মাদ্রাজ থেকে অতিরিক্ত সাহায্যে বলীয়ান হয়ে তারা কলকাতায় ফিরে আসে। নওয়াবের অসন্তুষ্ট কর্মচারী মীরজাফর, জগতশেঠ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মীরজাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার অঙ্গীকারে এবং মীর জাফরের ইংরেজদের আঞ্চলিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের স্বীকৃতির শর্তে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সদস্যবর্গ মীর জাফরের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করতে রাজি হয়। এ চুক্তির ফলে এবং মীরজাফর ও অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় বলীয়ান হয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ক্লাইভ পলাশীতে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। সিরাজও কোম্পানি সেনাবাহিনীর মোকাবেলার জন্য সেস্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি বন্দি হন এবং রাজধানীতে এনে তাঁকে হত্যা করা হয়। গোপন চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্লাইভ মীর জাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে মুগল সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে যদিও প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে ইংরেজদের আরও এক যুগ লেগেছিল।
মুগল রাজস্ব প্রশাসন মুগল রাজস্ব প্রশাসন ছিল বিশদভাবে পরিকল্পিত। একে সাধারণ প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছিল। সাধারণ প্রশাসনকে বলা হতো নিজামত এবং রাজস্ব প্রশাসনকে বলা হতো দীউয়ানি। প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ এবং শান্তি বজায় রাখাসহ সাধারণ প্রশাসন ছিল নাজিম বা সুবাহদারের হাতে, এবং রাজস্ব প্রশাসন ছিল দীউয়ানের হাতে। পদমর্যাদায় শেষোক্ত জন ছিলেন সুবাহদারের চেয়ে নিচে। তবে আর্থিক ও রাজস্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন সুবাহদারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তিনি কেন্দ্রীয় দীউয়ানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। রাজকীয় স্বার্থ এবং রায়ত, জমিদার, তালুকদারদের অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে জড়িতদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের পৃথকীকরণের নিয়ম করা হয়েছিল। সম্রাট মাঝে মাঝে এসব নিয়মসম্বলিত নির্দেশ জারি করতেন। রাজস্ব চিত্রের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় টোডরমলের বন্দোবস্তে। কিন্তু এটি একটি কাগুজে বিবরণের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কারণ ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল যখন এ বন্দোবস্ত করেছিলেন তখন বাংলার বৃহত্তর অংশ ছিল মুগল নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, টোডরমল শুধু প্রাক-মুগল যুগে প্রচলিত রাজস্ব-চিত্রের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। বাংলাকে টোডরমল ১৯টি সরকারে (৮৪ বছর পরে মুগল নিয়ন্ত্রণে আসা চট্টগ্রামও এতে অন্তর্ভুক্ত) এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। রাজস্ব আবার মাল বা ভূমি-রাজস্ব এবং সায়ের এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। ভূমি-রাজস্ব বাদ দিয়ে শুল্ক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কর সায়েরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুগল পদ্ধতিতে ভূমি খালসা ও জায়গির এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। খালসা ভূমি দীউয়ান ও তার কর্মচারীদের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হতো। জায়গির ছিল ওই সব ভূমি যেগুলি তাদের কাজের বিনিময়ে সামরিক বা বেসামরিক কর্মচারীদের দেওয়া হতো, অর্থাৎ তাদের বেতন জায়গিরের মাধ্যমে দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে নওয়ারা (নৌ-বাহিনী), খেদা (হাতি ধরা), আমলা-ই-আসামের (পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক ঘাঁটি) মতো প্রতিষ্ঠানকেও ভূমি দেওয়া হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দরবেশ ও সুফিদের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্যও ভূমি দান করা হতো। রাজস্ব প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল জমিদারদের উদ্ভব। তারা রায়ত ও সরকার এর মধ্যে দালাল হিসেবে কাজ করতেন। রাজস্ব আদায় করা সরকারের জন্য কোনো বড় সমস্যা ছিল না। প্রধান সমস্যা ছিল রায়ত কর্তৃক প্রদেয় রাজস্বের হার এবং আদায়কারী বা জমিদার কর্তৃক সরকারি কোষাগারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা। আবহাওয়ার অবস্থা, বন্যা ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ভূমিক্ষয়, আবাদযোগ্য জমির অনাবাদী জমিতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি কারণে শস্যহানির প্রতি লক্ষ রেখে দীউয়ান ও তার কর্মচারীরা রাজস্ব নির্ধারণের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাকাবী বা কৃষিঋণ মঞ্জুরির ব্যাপারেও তারা সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা এবং একই সঙ্গে রায়তদের সুখী ও তৃপ্ত রাখা যাতে তারা উন্নতি লাভ করে আরও বেশি জমি কর্ষণযোগ্য করে তুলতে পারে, এ দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মুগল রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
খালসা ও জায়গির উভয় শ্রেণীর জমি থেকে টোডরমলের বন্দোবস্তে বাংলার মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার চেয়ে সামান্য বেশি। জাহাঙ্গীরের আমলে সমগ্র বাংলা (চট্টগ্রাম ছাড়া) এবং কামরূপ মুগল শাসনাধীন হয়, টোডরমলের বন্দোবস্ত সেখানে কার্যকর করা হয় এবং জমির প্রকৃত গুণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়। টোডরমলের বন্দোবস্তের ৭৬ বছর পরে শাহ শুজার ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্তে রাজস্ব প্রায় ১৫.৫% বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বন্দোবস্ত করেন ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান এবং এ সময়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল আরও ১০%। মুর্শিদকুলীর ব্যবস্থা মালজামিনি নামে পরিচিত যার সম্ভাব্য অর্থ এ যে, তিনি রাজস্ব আদায় এবং নিয়মিত ও সময়মত তা রাজকোষে জমা প্রদানের জন্য জমিদারদের জামিন হতে বাধ্য করেন। রাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলী খান ছিলেন কঠোর যা মাঝে মাঝে নৃশংসতার পর্যায়ে পৌঁছাত। মুর্শিদকুলী খান বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। কিন্তু তাঁর এ চাকলা ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন টিকেনি। তিনি পুণ্যাহ প্রথাও প্রবর্তন করেন। বাংলা বছরের শেষ দিকে এক নির্দিষ্ট দিনে পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হতো এবং জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্যদের সেদিন তাদের প্রদেয় অর্থ মিটিয়ে দিতে বলা হতো। পুণ্যাহ ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে জমিদারি বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত (১৯৫১) টিকে ছিল। মুর্শিদকুলী খান আবওয়াব-ই-খাসনবিসি নামে এক নতুন করও প্রবর্তন করেছিলেন। মুগল সম্রাটগণ সব সময়ই আবওয়াব ধার্য করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কারণ জমিদারদের ওপর ধার্য করা হলেও জমিদাররা সেটা রায়তদের কাছ থেকে আদায় করতেন। পরবর্তী নাজিমগণ মুর্শিদকুলী খানকে অনুসরণ করেন। শুজাউদ্দীন, আলীবর্দী ও মীর কাসিম সকলেই আবওয়াব ধার্য করেন এবং মীর কাসিমের আমলে সরকারের রাজস্ব আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল।
মুগলদের আগমনের ফলে বাংলা তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছু নতুন শক্তির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে। এসব শক্তি বাংলার জীবন ও চিন্তাধারায় রূপান্তর ঘটায়। জনৈক পন্ডিত চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘বহির্জগত বাংলায় এসেছিল এবং বাংলা নিজের দেশ ছেড়ে বহির্জগতে চলে গিয়েছিল’। আগের আমলে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বাংলা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা এক শাসন, এক আইন, এক সরকারি ভাষা, অভিন্ন সরকারি কর্মচারী-কাঠামো ও মুদ্রা ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন মুগল সরকারের একটি অংশে অর্থাৎ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শুরুতেই বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা বাংলায় আসে। তবে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠা ও শান্তির সম্ভাবনার ফলে চাকরির সুযোগের আশাও বৃদ্ধি পায়। ফলে উলামা, শিক্ষক, কবি, চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীদের মতো শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনকারী বিদ্যানুরাগী মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় বাংলায় আসেন। শিয়া রাজনৈতিক নেতা, সুবাহদার, দীউয়ান ও অন্যান্যদের সঙ্গে শিয়া উলামা ও পন্ডিতগণ আসেন। কয়েকজন অত্যন্ত নামকরা মুগল সুবাহদার ছিলেন শিয়া। মুর্শিদকুলী খান বস্ত্তত এক শিয়া শাসক-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন যাঁরা প্রতিভাবান ও ধার্মিক শিয়াদের স্বাগত জানাতে ছিলেন সদা-প্রস্ত্তত। সুবাহদার বা অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাকে নিজেদের স্থায়ী বাসভূমি করেছেন, বা জীবনের কিছু অংশ বাংলায় কাটিয়েছেন এমন বহু ফারসি কবির নাম পাওয়া যায়। ফারসি সরকারি ভাষায় পরিণত হয় এবং এদেশে শুধু ফারসি সাহিত্যই সৃষ্টি হয় নি, স্থানীয় বাংলা ভাষাকেও ফারসি ভাষা প্রভাবিত করে। বাঙালি কবিরা ফারসি বিষয়বস্ত্ত গ্রহণ করেন এবং বহুসংখ্যক ফারসি শব্দ স্থানীয় ভাষায় ঢুকে পড়ে। রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বিভাগ আগের চেয়ে বিস্তৃততর হওয়ায় এবং অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ ফারসিতে রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে জমিদার, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী, অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় ব্যক্তিদের ফারসি ভাষা শিখতে হতো। বাংলার সুলতানদের মতো নয়, মুগল সুবাহদারগণ বাংলায় আসতেন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। ফলে স্থানীয় ভাষা শেখার প্রবণতা বা সময় কোনোটাই তাদের ছিল না, যার ফলে দরবারে নিয়োজিত স্থানীয় জমিদারের প্রতিনিধিদের ফারসি ভাষায় দক্ষ হতে হতো। মুগল শাসনামলের প্রথম দিকে রাজস্ব বিভাগের উচ্চতর পদগুলি উত্তর ভারত থেকে আসা খত্রি, লালা ইত্যাদির মতো মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে এসব উচ্চ পদ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। মুর্শিদকুলী খানের সময় প্রধান কানুনগো ছিলেন দর্পনারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণ এবং টাকশালের প্রধান ছিলেন রঘুনন্দন। সুজাউদ্দীনের সময় দীউয়ান ছিলেন রায় রায়ান আলম চাঁদ। তিনি উপদেষ্টা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আলীবর্দীর সময় জানকীরাম, দুর্লভরাম, রামনারায়ণ, কিরত চাঁদ, উম্মিদ রায়, বীর দত্ত, রামরাম সিংহ ও গোকুল চাঁদ ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী। সিরাজউদ্দৌলার সময় ছিলেন নন্দকুমার, উমিচাঁদ ও অন্যান্যরা। ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠের মতো মাড়োয়ারি ব্যাংক-মালিক পরিবারগুলি আসতে থাকে। বর্ধমানের জমিদারের মতো কিছু কিছু জমিদারও আসেন উত্তর ভারত থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাংলার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং বাংলা আন্ত:প্রাদেশিক বাণিজ্যে অধিক পরিমাণে অংশ নিতে থাকে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাংলার পণ্য পাটনা, আগ্রা, দিল্লি ও মুলতানের বাজারে পৌঁছে এবং সমুদ্র-বাণিজ্য এসব পণ্য পৌঁছে দেয় বালাশোর, কটক, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে।
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে। মুসলিম আমলের প্রথম দিকে বাংলার পণ্যের খুব অল্প অংশই অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যেত। এসব পণ্যের বিদেশি ক্রেতারা ছিল চীন, মালয়, আরব ও পারস্যদেশীয়। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথমে পর্তুগিজরা এসে ষোল শতকের প্রথম পাদে বাণিজ্য শুরু করে। তারা প্রথম চট্টগ্রামে আসে এবং বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। তবে আকবর এর অনুমতি নিয়ে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে বসতি স্থাপনের সময় থেকে তারা উন্নতি করতে থাকে। সমুদ্রপথে পর্তুগিজরা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু শীঘ্রই পর্তুগিজদের অধঃপতন ঘটে। সতেরো শতকের প্রথম পাদে তাদের শক্তি ও বাণিজ্যের অবনতি শুরু হয়। জলদস্যুতা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কাজকে প্রশ্রয় দেওয়ায় তারা মুগলদের প্রতিশোধমূলক নিগ্রহের সম্মুখীন হয়। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতাই ছিল তাদের পতনের প্রধান কারণ। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরো শতকের গোড়ার দিকে করমন্ডল উপকূলে তাদের ঘাঁটি মসলিপত্তম থেকে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অনুসরণ করে। মুগল সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়ে উভয় কোম্পানিই তাদের বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে। ওলন্দাজরা ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলির কাছে চুঁচুড়ায় এবং ইংরেজরা হুগলিতে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। পরে ইংরেজরা কলকাতায় চলে যায় এবং ফরাসি কোম্পানি এসে চন্দরনগরে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সব কোম্পানিই নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে তোলে এবং সুবাহদার আজিমুদ্দীনের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা মালিকদের কাছ থেকে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এ তিনটি গ্রাম ক্রয় করে কলকাতা নগরের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে আসে অস্টেন্ড কোম্পানি এবং সতেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার বহির্বাণিজ্য খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কোম্পানিগুলি বাংলা থেকে বারুদ তৈরির উপাদান শোরা রপ্তানি করত। এ শোরা দক্ষিণ বিহারের লালগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাংলা থেকে রপ্তানি করা অন্যান্য পণ্যের মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম সুতি সামগ্রী, মোটা সুতি বস্ত্র, রেশম ও রেশমি বস্ত্র, নীল, লাক্ষা ও চাল (এশীয় দেশসমূহের জন্য এবং জাহাজ স্থির রাখার কাজে তলদেশে স্থাপিত ভর হিসেবে)। কাজেই মুগল শাসনামল বাংলার বহির্বাণিজ্যের বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে। রপ্তানির বিপরীতে বিদেশি কোম্পানিগুলির আমদানি ছিল নগণ্য। কারণ দুর্লভ পণ্য ছাড়া বিদেশি কোম্পানিগুলির আমদানিকৃত অন্যান্য পণ্য স্থানীয় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। সুতরাং বিদেশি কোম্পানিগুলি প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপার পিন্ড আমদানি করে বাঙালি উৎপাদকদের হাতে তুলে দেয়। দেশের অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। প্রথমত মুদ্রার প্রচলন বহু গুণে বেড়ে যায়। আগে সমগ্র উড়িষ্যায় এবং বাংলার বহু অংশে ভূমি-রাজস্ব শুধু উৎপন্ন শস্যে আদায় করা যেত। তাই সংগ্রহকারীদের পক্ষে সরকারকে নগদ অর্থে রাজস্ব পরিশোধ করা ছিল কঠিন, কারণ শস্যকে টাকায় রূপান্তরিত করা ছিল কষ্টসাধ্য, বিরক্তিকর এবং কখনও কখনও তাতে প্রচুর লোকসান দিতে হতো। এখন থেকে বাংলা অন্যান্য দেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এমন বিপুল পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারত যা ছিল পূর্বে অচিন্তনীয়। বাংলায় টাকার এবং শ্রমের মূল্যও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে শ্রমের এ মূল্য বৃদ্ধিকে দ্রব্যমূল্যের নিরিখে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি বলা যায় না। উচ্চবিত্ত মানুষ প্রকৃতই আরও ধনী হয়ে ওঠে এবং অধিক পরিমাণে বিলাস দ্রব্যের অধিকারী হয়। সরকারি কর্মচারী ও রাজস্ব আদায়কারী দালালেরা অঢেল ধন সম্পদের মালিক হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ যে, বিপুল পরিমাণে স্থানীয় পণ্য রফতানি হওয়ার ফলে শিল্পজাত ও উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলার সুতি সামগ্রী, রেশম ও রেশমি সুতা, চাল, চিনি ইত্যাদির এক বিশাল বাজার এখন উন্মুক্ত হয়। বিদেশি কোম্পানির প্রতিনিধিরা এবং একক ক্রেতারা হাতে প্রচুর অর্থ নিয়ে বাংলার উৎপাদনকারীদের বিক্রির জন্য আনা প্রায় যে কোনো পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রস্ত্তত থাকত। বিদেশি রপ্তানিকারকরাও দেশে দক্ষতার সঙ্গে এবং সুলভে শিল্পজাত উৎপাদন সংগঠনে সাহায্য করেছিল। তারা প্রতিটি বাণিজ্য কেন্দ্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করত এবং শ্রমিক ও কারিগরদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করত। এ ছাড়া তাদের কুঠিতে কারখানা স্থাপন করত, যেখানে স্থানীয় শ্রমিকরা ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারত। তারা দেশিয় কারিগরদের উন্নততর কৌশল শেখানোর জন্য নিজেদের দেশ থেকে বস্ত্রাদি রঞ্জক ও সুতা প্রস্ত্ততকারীদের নিয়ে আসত। এভাবে তারা বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল।
পরিপূর্ণ বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর বাংলায় মুগলদের শান্তিপূর্ণ অধিকার বজায় থাকে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষের দিকে শোভা সিংহের বিদ্রোহ ছাড়া (যা অতি অল্প সময়েই দমন করা হয়েছিল) মুগলদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো বড় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নি। আরাকানের মগদের সহযোগিতায় পর্তুগিজদের জলদস্যুতাও ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম জয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। মুগলদের আগে অবশ্য বাংলা এক বিদ্রোহী প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। দিল্লির তদানীন্তন শাসকরা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে নীতি অনুসরণ না করে মুগলরা সম্রাটের পুত্র ও আত্মীয় এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ও বিশ্বস্ত বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ করেন। সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রদেশের পরিচালনার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং সুবাহদারের পদ শূন্য হলে বিহারের সুবাহদারকে শূন্য পদ পূরণের জন্য পাঠানো হতো। বাংলায় মুগল শাসন শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করে। বহির্বাণিজ্য, সোনা ও রুপার অন্ত:প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে এক ‘জান্নাত-উল-বিলাদে’ পরিণত করে। উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা এ নামে বাংলাকে অভিহিত করত। ইউরোপীয় জাহাজের জন্য এদেশ উন্মুক্ত হওয়ার সময় থেকে পর্তুগাল, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড থেকে বিদেশি পর্যটকরা বাংলায় আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন দুয়ার্তে বারবোসা, ভার্থেমা, সিজারফ্রেডারিক, সেবাস্টিয় ম্যানরিক, রালফ্ ফিচ, টমাস বাউরি, নিএকাএলা মানুচি, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার, টেভার্নিয়ার, স্ট্যাভোরিনাস প্রমুখ। তাদের প্রায় সকলেই বাংলার ধনসম্পদ, বিলাসবহুল ও অতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দেশের ধনসম্পদের প্রাচুর্য, স্থানীয় মহিলাদের সৌন্দর্য এবং নমনীয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বভাব মিলে পর্তুগিজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদের জন্ম দিয়েছে যে, বাংলা রাজ্যে প্রবেশের জন্য এক শত দরজা রয়েছে, কিন্তু নিষ্ক্রমণের কোনো দরজা নেই। [আব্দুল করিম]
ঔপনিবেশিক যুগ ১৭৫৭-১৯৪৭ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসে বাণিজ্য বসতি স্থাপন করে সতেরো শতকের মাঝামাঝি। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে কোম্পানি বঙ্গের সর্বময় কর্তা। বাণিজ্যের পাশাপাশি রাজ্য স্থাপন ছিল সমকালীন ইউরোপীয় বেনেবাদ নীতির পরিপন্থি। উল্লেখ্য যে, সমকালীন ইউরোপীয়রা সাগরের ওপাড়ে গিয়ে জনমানবশূন্য বা আদিবাসী অধ্যূষিত এলাকা দখল করে স্ব স্ব জাতির পক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করলেও বঙ্গদেশই প্রথম সভ্য দেশ যেখানে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।
ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, এ অভূতপূর্ব ঘটনা কোনো সচেতন পরিকল্পনার ফসল নয়। তাঁরা মনে করেন যে, বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পর্যায়ক্রমে এবং নানা অনভিপ্রেত ঘটনা প্রবাহের ফলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিলে দেখা যায় যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কোম্পানির বেঙ্গল কাউন্সিলকে সব সময়ই এখানে রাজ্য স্থাপণের ব্যাপারে নিরোৎসাহিত করেছে, কিন্তু তবুও কালে কোম্পানির বঙ্গরাজ্য প্রতিষ্টিত হলো। দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের মতামতকে উপেক্ষা করে যখন কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বা জোরজবরদস্তির মাধ্যমে কোনো সুবিধা আদায় করতে পেরেছে, কোর্ট তা সবসময়ই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কোর্ট কখনও ঝুঁকি নিতে চায় নি। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ঝুঁকি নিয়ে সুবিধাজনক সাফল্য দেখাতে পারলে কোট অব ডাইরেক্টর্স তা সব সময়ই মেনে নিয়েছে। বাণিজ্যের সুবিধার্থে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে রাজ্য স্থাপনের অভিলাষ ক্রমশই দাঁনা বেধে উঠেছিল আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকেই।
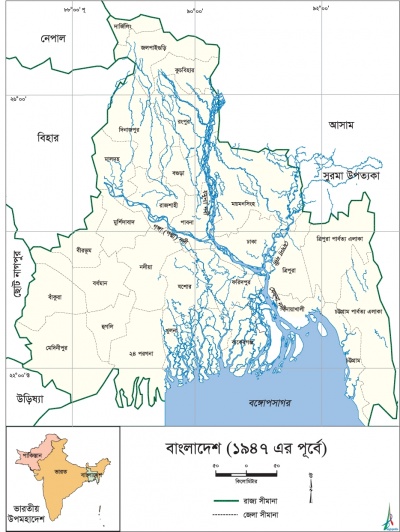
১৬৫১ সালে সুবাহ বাঙ্গালার সুবাহদার শাহ সুজার নিকট থেকে একটি নিশানের ওপর ভিত্তি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক নির্দিষ্ট তিন হাজার টাকা পরিশোধের শর্তে এ দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য শুরু করে। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার এ ব্যবস্থা শুধু কোম্পানির জন্য সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীসময়ে কোম্পানির কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যও এ সুবিধা বেআইনীভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। এর ফলে সরকারের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কে ক্রমশই অবনতি ঘটতে থাকে। এর এক পর্যায়ে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের এদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য কলকাতা আক্রমণ করেন। এ ঘটনা জন্ম দেয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি যার শেষ ফল পলাশী যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ এবং পরিশেষে ১৭৬৫ সালে দীউয়ানি লাভের মাধ্যমে সুবাহ বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য স্থাপন।
ঔপনিবেশিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের চূড়ান্ত পরাজয় কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করল। কোম্পানি নীতি গ্রহণ করল সরাসরি ক্ষমতা দখল না করে একজন নামেমাত্র নওয়াব গদিসীন রেখে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে নিয়ে দেশের রাজস্বের ওপর হিস্যা বসানো। এ নীতির অংশ হিসেবেই ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার দীউয়ানি লাভ করেন (১৭৬৫)। সম্রাট ও নওয়াবের সঙ্গে চুক্তি হয় যে, দীউয়ান হিসেবে কোম্পানি সুবা বাংলার রাজস্ব সংগ্রহ করবে। চুক্তির শর্তানুসারে কোম্পানি সুবার রাজস্ব থেকে বার্ষিক থোক ছাবিবশ লক্ষ টাকা বাদশাহকে এবং তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা নওয়াবকে প্রদান করবে এবং বাকি রাজস্ব কোম্পানি নিজে ভোগ করবে।
দীউয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ না করে এ দায়িত্ব অর্পণ করল একজন নায়েব দীউয়ানের ওপর। নায়েব দীউয়ান হিসেবে নিযুক্ত হলেন চট্রগ্রামের প্রাক্তন ফৌজদার সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খান। নাবালক নওয়াব নজমুদ্দৌলার পক্ষে নিজামত প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করা হয় রেজা খানকে। অর্থাৎ ১৭৬৫ সালের ব্যবস্থায় দৃশ্যত রেজা খানই হলেন প্রশাসনের প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অলিখিতভাবে কোম্পানিরই অদৃশ্য হাতে। দ্বৈত শাসন নামে এ ব্যবস্থায় নায়েব নাজিমএর ওপর সকল দায়িত্ব অর্পিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই, আর কোম্পানির কাছে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত, কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেই। কোম্পানি সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ করলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক ও ভারতীয় রাজন্যগোষ্ঠী তা মেনে নেবে না এ আশংকাবশতই ক্লাইভ কূটনৈতিক চাল দিয়ে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, দেশ শাসনের জন্য তখন কোম্পানির না ছিল প্রয়োজনীয় লোকবল, না ছিল কোনো অভিজ্ঞতা। তবুও ক্লাইভ দীউয়ানি চুক্তি করেন দুটি প্রধান কারণে। একটি রাজনৈতিক। সিরাজউদ্দৌলা বা মীর কাসিমের মতো নওয়াবের যেন আর আবির্ভাব না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অপর উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক। কোম্পানির প্রাচ্য বাণিজ্যের পুঁজি স্বদেশ থেকে না এনে প্রাচ্য থেকেই সংগ্রহ করা। ইতঃপূর্বে কোম্পানি এদেশে স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে আসত পণ্য কেনার জন্য। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ সরকার বিদেশে ধাতব রপ্তানির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোম্পানি চেষ্টা চালায় প্রাচ্য বাণিজ্যের জন্য প্রাচ্যদেশ থেকেই পুঁজি সংগ্রহ করার। সুবাহ বাংলার দীউয়ানি লাভ ছিল এ নীতিরই একটি অংশ।
দীউয়ানির নামে বাংলায় কোম্পানি যে শোষণ ও উৎপীড়নের রাজ্য কায়েম করল তাতে ব্রিটিশ সরকার এতদিন কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি। ১৭৬৯/৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল কোম্পানির বিষয়াদিতে হস্থক্ষেপ করার জন্য। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে পার্লামেন্ট কোম্পানির বঙ্গরাজ্য বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন বিপ্লবের পর আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রিটিশ সরকার বিকল্প কলোনি হিসেবে দৃষ্টিপাত করল ভারতের ওপর। পাস করল পিট-এর ভারত আইন (১৭৮৪) যার মাধ্যমে কোম্পানির বঙ্গ রাজ্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করা হলো। লর্ড কর্নওয়ালিসকে পার্লামেন্ট গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে এ নির্দেশ দিয়ে যে, তিনি একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গরাজ্যকে একটি শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।
নির্দেশানুসারে কর্নওয়ালিস ত্বরিৎ গতিতে ভূমি ব্যবস্থা ও প্রশাসনে অনেক সংস্কার আনয়ন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তিনি একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেন। ভূমির একচ্ছত্র মালিক করা হয় জমিদারকে। জমিদারের ওপর সরকারের রাজস্ব দাবি চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সমর্থন করে এমন একটি প্রভাবশালী অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা। এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জমিদার শ্রেণীর উদ্যোগে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা। প্রশাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজিয়ে কর্নওয়ালিস ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করে স্থাপন করেন। একটি উচ্চ বেতনভোগী পেশাগত আমলাতন্ত্র স্থাপন করে কর্নওয়ালিস ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। যথার্থই বলা হয় যে, কোম্পানির বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ক্লাইভ ও হেস্টিংস এবং এর প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠাতা কর্নওয়ালিস।
তবে বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণভাবে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত হলেও ব্রিটিশ সরকার প্রথম পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে ১৮১৩ সালে যখন পার্লামেন্ট একটি চার্টার অ্যাক্ট বলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত করে এবং দেশের শাসনভার আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। উক্ত আইনে কোম্পানির দূরপ্রাচ্য বাণিজ্য বজায় রাখে। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনে তাও বিলুপ্ত করা হয়। এরপর থেকে কোম্পানির অধিকার থাকে পার্লামেন্টের পক্ষে শুধু ব্রিটিশ ভারত শাসন করার ক্ষেত্রে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ব্রিটিশ ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে।
এমনিভাবে কোম্পানির বঙ্গ রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এমনকি প্রদেশরূপেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চেয়ে অনেক কম সুবিধাপ্রাপ্ত। উক্ত দুটি প্রদেশের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন গভর্নর ও গভর্নর-এর কাউন্সিল ছিল। কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য না ছিল স্বতন্ত্র গভর্নর, না ছিল কোনো কাউন্সিল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসিত হতো পরোক্ষভাবে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক। গভর্নর জেনারেলের পক্ষে একজন কাউন্সিলর ডেপুটি গভর্নর উপাধি ধারণ করে নামে মাত্র বঙ্গীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতব্যাপী বিস্তারের ফলে প্রশাসন ও অর্থনীতির দিক থেকে বাংলা প্রদেশ সবচেয়ে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ হয়ে পড়ল। ১৮৫৪ সাল থেকে বাংলার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু কোনো কাউন্সিল ছাড়া। সার্বিক অবস্থা আগের মতই করুণ থাকায় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির নামে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করা হয়। কিন্তু এর বিপক্ষে রাজনৈতিক চাপের মুখে ১৯১২ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করা হয়।
কিন্তু যুক্ত বাংলা প্রশাসনিক দিক থেকে আগের পর্বে ফিরে যায় নি। বাংলাকে বোম্বে ও মাদ্রাজের মতো একটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হলো। গভর্নরকে সাহায্য করার জন্য স্থাপিত হলো একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। বাংলা প্রদেশের রাজধানী হলো কলকাতা এবং কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লিতে।
বাংলা বিভাগকে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় স্বাগত জানিয়েছিল। বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের রাজনীতির ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পড়ে। মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বিকল্প হিসেবে মুসলিম নেতৃবর্গের অনেকে কংগ্রেস মতাদর্শে ঝুঁকে পড়ে। অপরদিকে, মুসলমান নেতৃত্বের অনেকে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করে মুসলিম রাজনীতি শুরু করে। বস্ত্তত, ১৯২০ এর পর থেকে বঙ্গীয় রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে ঘিরেই আবর্তিত হয় এবং পরিশেষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টে বাংলা বিভক্ত হয়।
হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী স্থাপনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেক সক্রীয় চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঐক্য কার্যকরভাবে কখনও স্থাপিত হয় নি। চিত্তরঞ্জন দাশ-এর নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে যে চুক্তি হয়েছিল তা অকার্যকর হয়ে গেল ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরপরই। এর পর প্রতিটি কাউন্সিল নির্বাচন হয়েছে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব আরও বেড়ে গেল। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বঙ্গীয় আইন সভায় দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপরই ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। দৃশ্যত অসাম্প্রদায়িক হলেও এ দলটিও ছিল মুসলিম রাজনীতি ঘেষা। অর্থাৎ উভয় দল মিলে সহজেই বঙ্গীয় আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল এবং ক্রমাগত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হলো।
১৯৩৫ সালের ভারত আইন সাম্প্রদায়িক ও তফশিলি রাজনীতির জন্ম দেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল মুসলিম ও তফশিলি রাজনীতির পক্ষে। সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির বিজয় উপমহাদেশের রাজনীতির গতিাধারা বদলে দিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল পরিবর্তিত রাজনৈতিক চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ। প্রথম স্বতন্ত্র নির্বাচন, তারপর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। স্বাভাবিক কারণেই এ হেন অভাবিত পরিবর্তনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল মেনে নিতে পারেনি। দেখা দিল অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত ও বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত সময়কালটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য ক্রান্তিকাল। নানা বাস্তব পরিস্থিতি বাংলার মুসলিম নেতৃত্ব পাকিস্তান আদর্শকে মেনে নিল। এর প্রথম পরিণতি দেশ বিভাগ ও অজস্ত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা।
ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত পলাশীর পর পর্যায়ক্রমে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলায় তথা ভারতে দুটি সংস্কৃতির সম্মিলন সূচনা করল। বিগত পাঁচ শত বছর যাবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নির্মিত পারস্পরিক সহাবস্থান ভিত্তিক বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে এখন যুক্ত হল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। কিন্তু পূর্বেকার মতো এবার স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশি সংস্কৃতির মিশ্রণ লক্ষণীয়ভাবে ঘটে নি। শাসক ইংরেজ জাতি প্রথম থেকে দেশে ইউরোপীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। ভূমি প্রশাসনেও ইউরোপীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রশাসনও প্রবর্তিত হয় ইউরোপীয় আদলে। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি এবং বিষয়ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক। অতএব, ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে যা সকল সনাতন প্রথা,প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাকে অবক্ষয়িত করে তোলে।
ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সনাতন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় এর কতিপয় উপমা দেওয়া যেতে পারে। মুগল রাষ্ট্রের সুবাহদার এর ক্ষমতা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বাধা ছিল তাঁর ক্ষমতা। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেল পায় অপরিসীম ক্ষমতা, অন্তত বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ভোগ করতেন। মুগল আমলে ছিল গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত, কাজী, কানুনগো, আমিন, থানাদার, ফৌজদার প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের স্থানীয় আমলাবর্গ। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের স্থানীয় সরকার বলতে ছিল মাত্র জেলা কালেক্টর, জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। শত শত বর্গমাইল ব্যাপী একটি জেলা পরিচালিত হতো অসীম ক্ষমতাধারী ওই তিন সাহেব সিভিলিয়ন অফিসার দ্বারা। জেলা প্রশাসনে জেলার মানুষের কোনো হাত ছিল না। মুগল রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভাগাভাগী হতো হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল শুধু শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণী। আমলাতন্ত্রের কিছু অংশ দেশিদের ভাগে আসতে থাকে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ। মুগল আমলে শিক্ষা ছিল সবার জন্য মুক্ত। টোল, পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসায় যেন সবাই মুক্তভাবে এবং বিনা পয়সায় পড়াশুনা করতে পারে সে জন্য মুগল সরকার দিত নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুযোগ সুবিধা, যেমন বৃত্তি, মহাত্রাণ, মিলাকি ও ওয়াক্ফ। মদদ-ই মাশ নামে ওসব সুযোগ সুবিধা ব্রিটিশ আমলে প্রত্যাহার করা হয়। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা এত ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাড়ায় যে, একমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত না। যে জন্য ১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায় যে, বাঙালিদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ছিল তখন মাত্র শতকরা চার ভাগ।
ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়েছে ভূমি সম্পর্ক ও গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক ঘোষণা এবং রায়তকে জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত করে গ্রামীণ ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে নেতিবাচকভাবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করা হলো। ইতঃপূর্বে ভূমির মালিকানা ছিল সরকারের ওপর ন্যস্ত। সরকার ও রায়তের মধ্যে ছিল সরাসরি সম্পর্ক। সরকারের পক্ষ থেকে জমিদার রাজস্ব সংগ্রহ করত। জমিদার ছিল সরকারের স্থায়ী স্থানীয় কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি। রায়তের খাজনার হার ছিল পরগণার নিরিখে নির্ধারিত। জমিদার তা ইচ্ছা করলেই সরকারের নির্দেশ ছাড়া পরিবর্তন করতে বা রায়তকে উৎখাত করতে পারত না। এক কথায়, তাত্ত্বিকভাবে ভূমির মালিক সরকার হলেও, বাস্তবে বংশাণুক্রমিকভাবে ভোগ দখলকার হিসেবে রায়তই ছিল জমির মালিক, আর জমিদার ছিল সরকারের পক্ষে খাজনা সংগ্রাহক মাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ সম্পর্ককে পাল্টে জমিদারকে করা হলো পাশ্চাত্য অর্থে জমির একচ্ছত্র মালিক আর রায়তকে পরিণত করা হলো তার ইচ্ছাধীন প্রজায়। এ সম্পর্কের অভিঘাতে পল্লী বাংলায় সৃষ্টি হলো সর্বময় ক্ষমতাধারী এক ভূস্বামী শ্রেণী। ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক হয়ে উঠল শোষক-শোষিতের। গ্রামীণ সম্পদ ভূস্বামীর হাতে পুঞ্জিভূত হলো। প্রজা হলো এক চিরঋৃণগ্রস্থ এক অসহায় দুর্বল শ্রেণী। অর্থের অভাবে এরা শিক্ষাবঞ্চিত এবং স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাদপদ। রাজনৈতিকভাবে এর তাৎপর্য এ যে, একচেটিয়া সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী জমিদার ছিল প্রায় সবাই হিন্দু, আর অধিকারহীন, সহায় সম্বলহীন প্রজাকুলের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। এ সম্পর্কের মাপকাঠিতে হিন্দু মুসলমানের ক্রমাবনতিশীল সম্পর্ক ও পরিশেষে দেশ বিভাগের ইস্যুগুলি অনেকাংশে ব্যাখ্যা করা যায়।
ঔপনিবেশিক শাসনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে, সচেতন এবং পরিকল্পিতভাবে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পাশ্চাত্যমুখী করা। পূর্ববর্তী কোনো শাসকগোষ্ঠী এমনতরো কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা প্রতিষ্ঠানে কখনও হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস পায় নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ধর্ম ছাড়া বাকি সব ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। ভারতীয়দের ‘সভ্য’ করা ছিল ব্রিটিশদের একটি মিশন। ওই লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও নানা সংস্কার আইন প্রবর্তন করেছে।
ব্রিটিশদের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ছিল দেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ লক্ষ্যে নানা ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয় ১৮৬১ সাল থেকে। এ প্রকল্পে পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা শুধু সমর্থন দেয় নি, বরঞ্চ এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার বাইরের জনতা এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। তারা তাদের সনাতন পঞ্চায়েত ও সালিশ ব্যবস্থাকেই অাঁকড়ে থেকেছে। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে প্রাচ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশের মানুষকে পাশ্চাত্য ব্যবস্থাদির প্রতি আকৃষ্ট করবে এ তত্ত্ব পরে সঠিক প্রমাণিত হলো। [সিরাজুল ইসলাম]
পাকিস্তান শাসন (১৯৪৭-১৯৭১) ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাসকৃত ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে বিভক্ত করে। ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশটি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামের দুটি ভূখন্ডে বিভক্ত হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অংশ হয়। এভাবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ‘পূর্ব বাংলা’ নামক প্রদেশের জন্ম হয়। ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়।
বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ৫ আগস্ট খাজা নাজিমউদ্দীন ৭৫-৩৯ ভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে পূর্ব বাংলা আইন সভার সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন এবং পূর্ব বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন (১৪-৮-১৯৪৭)। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন পূর্ব বাংলায় প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যকেই গ্রহণ করা হয় নি যা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার অভাব নির্দেশ করে।
১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হলে নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং নূরুল আমীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। নূরুল আমীন ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পূর্ব বাংলার জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি (১৯৫০) ও ভাষা আন্দোলন তাঁর আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময় ভাষার প্রশ্নটি যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে স্থান এবং নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন থেকে এ ভূখন্ডে স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনা শুরু হয়।
পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ। অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩০৯টি। এর মধ্যে ২৩৭টি (৯টি মহিলা আসনসহ) মুসলমান আসন, ৬৯টি হিন্দু আসন (৩টি মহিলা আসনসহ), ২টি বৌদ্ধ আসন এবং ১টি খ্রিস্টান আসন। ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বছর পূর্ণ হয়েছিল তাদেরকে ভোটার করা হয়েছিল। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬ জন। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম ২১ দফার ভিত্তিতে ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করে। ২১ দফায় উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন, শিক্ষা সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইন পরিষদকে কার্যকর করা ইত্যাদি।
নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২১৫টি আসন, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। খেলাফতে রাববানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করে ১২টি আসন। পরে ৭ জন স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টে এবং ১জন মুসলিম লীগে যোগ দেন। মুসলিম লীগের পরাজয়ের পেছনে বহুবিধ কারণ ছিল। ১৯৪৭ এর পর থেকে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক ত্যাগী নেতা কর্মী দল থেকে বের হয়ে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৪৭ থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তার দায় দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগকেই বহন করতে হয়। ১৯৪৭ থেকে ৫৪ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতা করে এবং ১৯৫২ সালের হত্যাকান্ড ঘটিয়ে মুসলিম লীগ বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে প্রকারান্তরে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের আসন হাতছাড়া হওয়ায় পাকিস্তান গণপরিষদে ওই দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। এর ফলে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের সুযোগ পায়। যুক্তফ্রন্ট প্রাপ্ত ২২২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা ছিল ১৪২, কৃষক-শ্রমিক পার্টির ৪৮, নেজামে ইসলামের ১৯ এবং গণতন্ত্রী দলের ১৩। যুক্তফ্রন্ট দলের প্রধান নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (আওয়ামী মুসলিম লীগ) এবং এ.কে ফজলুল হক (কৃষক-শ্রমিক পার্টি)। নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী অংশ গ্রহণ করেন নি এবং ফজলুল হককে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। শুরুতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয় এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। অবশেষে ১৫ মে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগে ফজলুল হকের আপোস হয় এবং তিনি এ দলের ৫ জন সদস্যসহ ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এ মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল মাত্র ১৪ দিন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ সরকার সুনজরে দেখে নি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার চক্রান্ত করতে থাকে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিল্পকল-কারখানায় বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। এতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় ব্যর্থ বলে দোষারোপ করা হয়। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা জন পি. কালাহান ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশ করেন যে, তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে শাসকগোষ্ঠী তাঁকে দেশোদ্রোহী ঘোষণা করে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে (১৯৫৪) যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে যা ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে।
ফজলুল হককে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় তাঁর দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুধারায় বিভক্ত হন। আওয়ামী মুসলিম লীগের ধারাটি ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ গ্রহণ করে। এ সময় (১৯৫৫) আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। অপর পক্ষে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের নিকট তাঁদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালের ৩ জুন কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ পান। নবনিযুক্ত এ মন্ত্রিসভার প্রতি প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা আছে কিনা, তা প্রমাণ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবান সংক্রান্ত আওয়ামী লীগ এর দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এমনকি পরবর্তী আট মাসেও আইন পরিষদের কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয় নি।
১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলে প্রদেশে তাঁর দলের অবস্থান দৃঢ় হয়। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার আড়াই মাস পর ফজলুল হক আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে তাঁর দলীয় মন্ত্রিসভার পতন হবে এ আশঙ্কায় তিনি ২৪ মে আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন। সাত দিন পরেই এ আদেশ প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা বহাল করা হয়। এবারও মন্ত্রিসভাকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এভাবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অসাংবিধানিক পন্থায় ৩০ আগস্ট ১৯৫৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ফজলুল হকের গভর্নর পদ লাভ এবং পূর্ব বাংলায় তাঁর দলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার বিনিময়ে তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন এবং তা রক্ষা করেন। প্রতিশ্রুতি দুটি ছিল প্রথমত গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া সংবিধান তাঁর দল সমর্থন করবে, দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা সমর্থন করবে না।
কৃষক-শ্রমিক পার্টি যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরোধিতা করায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু অধিবেশন শুরুর কয়েক ঘন্টা পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে গভর্নর অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তদস্থলে ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু ও বামদলগুলির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এ মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তেরো মাস (১২-৯-৫৬ থেকে ১৮-১০-৫৭) এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় আঠারো মাস (৬-৯-৫৬ থেকে ৩১-৩-৫৮)।
একই সঙ্গে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ, জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠন, ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানা স্থাপন, সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডি.আই.টি) প্রতিষ্ঠা এবং ‘গ্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্ল্যান’ প্রণয়ন, ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এফ.ডি.সি) প্রতিষ্ঠা, ঢাকার রমনা পার্ক গড়ে তোলা, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ঢাকা-আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ, প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্ল্যানিং বোর্ড গঠন এবং তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন। আওয়ামী লীগ সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে।
মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করলে আওয়ামী লীগ থেকে ২৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করে ন্যাপে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দেন। কিছু সংখ্যালঘু সদস্যও আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বাজেট পাস করা অসম্ভব হয়ে পড়লে সরকার গভর্নরকে বাজেট অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করে। কিন্তু ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন (৩১-৩-৫৮) এবং আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এসময় কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুনের রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিসভা আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে টিকে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নর পদ থেকে ফজলুল হককে বরখাস্ত করে (১-৪-৫৮) এবং পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব দেয়। নতুন গভর্নর আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনর্বহাল করেন (১-৪-৫৮)। আস্থাভোটে সরকার ১৮২-১১৭ ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু এর দেড় মাস পর (১৮-৬-৫৮) সরকার খাদ্য পরিস্থিতির ওপর এক ভোটাভুটিতে হেরে যায়, ফলে ১৯ জুন ১৯৫৮ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় এবং ২০ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি সরকার গঠন করে। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ ন্যাপের সমর্থন নিয়ে আইন পরিষদে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা ভোটে (১৫৬-১৪২) পরাজিত করে (২৩-৬-৫৮)। কিন্তু তখন আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ না জানিয়ে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় (২৫-৬-৫৮)। এর দুমাস পর (২৫-৮-৫৮) আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়।
এভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সাতটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে আইন পরিষদে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী একদল বিক্ষুব্ধ পরিষদ সদস্য কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়।
পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি বরখাস্ত, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ অবলুপ্ত, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত এবং মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করা হয়। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইসকান্দার মির্জাকে অপসারিত করে সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এভাবে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। সামরিক আইন জারির পর পরই আইয়ুব খান রাজনীতিবিদ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, ধনী ব্যবসায়ী, সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী, জাতীয় ও আইন পরিষদের সদস্য প্রমুখের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর Election Bodies Disqualification Order, 1959 (EBDO) এবং Public Offices Disqualification Order (PODO) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। EBDO-এর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের ৩,৯৭৮ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩,০০০ জন রাজনীতিবিদ রাজনীতি করার অধিকার হারিয়ে ছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের ১৬৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। PODO-র আওতায় যেসকল সংবাদপত্রে প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারের কথা লেখা হতো (যেমন ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার) সেগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে সরকারি-আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়।
আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসনামলের অভিনব সৃষ্টি হচেছ মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৫৯ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্র্র ছিল চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছাড়াও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবন্থায় আইয়ুব খান গ্রাম পর্যন্ত সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, যারা Electoral College হিসেবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। এভাবে জনগণ প্রেসিডেন্ট ও আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দল ও জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায় এবং সীমিতসংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার সহজ হয়। ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খান ১৩ জানুয়ারি (১৯৬০) Presidential Election and Constitutional Order, 1960 জারি করেন এবং এ অধ্যাদেশ বলে ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) হ্যাঁ - না ভোটের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং তা ৮ জুন থেকে কার্যকর হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১ মার্চ থেকে ৮ জুনের মধ্যে দেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত করেন। ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।
১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ডাকে ও রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ধর্মঘট একনাগাড়ে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। এভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান সংবিধান ঘোষণা করা মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। ১৯৬২-এর সেপ্টেম্বরে আরেকটি আন্দোলন হয়, যা ‘বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন’ নামে অভিহিত। শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে বাবুল, গোলাম মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখ নিহত হন এবং আহত হয় প্রায় আড়াইশ জন। এ আন্দোলনের ফলে সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রাখে। এ আন্দোলনের গুরুত্ব এ যে, এ সময় থেকে ছাত্ররাই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র সম্প্রদায় প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর ‘শিক্ষা দিবস’ রূপে পালন করে আসছে।
১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক আইন তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদগণ দলীয় রাজনীতি করার অধিকার ফিরে পান। সোহরাওয়ার্দী সকল দলের সমন্বয়ে আইয়ুব বিরোধী একটি ফ্রন্ট গঠনের আহবান জানান। তার উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে ৪ অক্টোবর (১৯৬২) ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট বা এন.ডি.এফ নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল এ ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফ্রন্ট গঠনের পিছনে সোহরাওয়ার্দীর আরেকটি কৌশল কাজ করেছিল। এবডো আইনে সাজাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদের জন্য রাজনীতি করা নিষিদ্ধ থাকলেও ফ্রন্টের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। তাই তিনি ফ্রন্ট গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। খুব শীঘ্র ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
১৯৬৩ এর ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করার পরবর্তী মাসেই (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪) আওয়ামী লীগ পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ইতঃপূর্বে ন্যাপ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল আত্মপ্রকাশ করে। ফলে এন.ডি.এফ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে একক প্রার্থী দেওয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে Combined Opposition Party (COP) নামক একটি জোট গঠন করে। COP মিস ফাতিমা জিন্নাহকে (মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী) প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটার ছিলেন ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী। আইয়ুব খান ওই সব গণতন্ত্রীদের বশীভূত করেন। নির্বাচনে জনগণের মধ্যে মিস জিন্নাহর পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেলেও নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান যেখানে ৪৯,৯৫১ ভোট পান, সেখানে মিস ফাতিমা পান মাত্র ২৮,৯৬১। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ সব নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, মৌলিক গণতন্ত্র যতদিন থাকবে ততদিন আইয়ুব খানকে অপসারণ করা সম্ভব হবে না।
আইয়ুব খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি বিশেষ স্বার্থ ও সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়ে। সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করার দাবি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ ভোটের দাবি উচ্চারিত হয়। নির্বাচনী ফলাফল থেকে সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষোভ কমতে না কমতেই শুরু হয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সময় এটা স্পষ্ট হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। এমনকি উক্ত যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এ প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচিছন্ন হয়ে পড়েছিল। অতএব ১৬শ কিমি ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান যে একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল তা আরেক বার প্রমাণিত হলো। ইতোমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন মহলকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে।
পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমলাগণ ছিলেন প্রশাসনের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। আমলাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ২,৯০০। করাচিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানকার সকল অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই একচেটিয়া চাকরি লাভ করে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালিদের পক্ষে সেখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেওয়ায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্যলাভ সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বাড়তেই থাকে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ ও ৩,৭০৮ জন এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬,৩১০ ও ৮২,৯৪৪ জন। ১৯৬২ সালে ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানিদের অবস্থান ছিল ২০.৮%; ১৯৬৮ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের অফিসারের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে অনুপাত ছিল ১০ : ৯০। শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা (১৩.৫%)। ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মাত্র ১০% ব্যয় হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে উন্নয়ন খাতে খরচ হয় ১৪৯৬.২ মিলিয়ন টাকা, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে খরচ করা হয় মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমে তিনটি রাজধানী শহর (করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ) নির্মাণ করা হয়। কেবল করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা, যা উক্ত সময়কালে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%, যে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদের উন্নয়নের জন্য ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হলেও ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী ও সামরিক-বেসামরিক বিভাগসমূহের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হওয়ায় চাকুরির সুবিধা ছাড়াও বিভিন্ন ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং নির্মাণ ও সরবরাহ ক্ষেত্রে যে কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা।
এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য, নির্বাচনে প্রাপ্য ফলাফল লাভে ব্যর্থতা, পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে ছয়দফা কর্মসূচিউপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৭৩৫ জনই তাৎক্ষণিকভাবে তা নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব সম্মেলন স্থান ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। লাহোরে শেখ মুজিব যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করবেন সে বিষয়ে দলের কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়।
শেখ মুজিবসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয় এবং এতে আতঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ধর পাকড় শুরু করে। ৮ মে (১৯৬৬) শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন (১৯৬৬) গোটা প্রদেশে হরতাল পালন করে। শ্রমিক শ্রেণী এ ধর্মঘটে সাড়া দেয়। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০জন নিহত হয়। ৭ জুন হরতালের পর সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৫ জুন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) গ্রেফতার হন এবং ১৬ জুন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৯,৩৩০ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির উপর নতুন করে হামলা আসে। সরকার ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেয়।
আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ ১৯৬৭ সালের ২ মে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট বা পি.ডি.এম নামক একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। পি.ডি.এম আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ আট দফা ছিল ছয় দফার বর্ধিত সংস্করণ। পি.ডি.এম-এর আট দফায় কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনই নয়, দশ বছরের মধ্যে দুপ্রদেশের বিরাজমান বৈষম্যাবলি দূর করার কর্মসূচিও দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবি ছিল একটি আঞ্চলিক দলের দাবি, অপর পক্ষে পি.ডি.এম-এর আট দফা দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। যেহেতু পি.ডি.এম-এর আট দফার মূল দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জন, সেহেতু সরকারের সকল ক্ষোভ পড়ে শেখ মুজিবের উপর। সরকার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং বিরোধী দলীয় জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে (৬-১-৬৮)। এবং একে আগরতলা ষড়যন্ত্রবলে অভিহিত করা হয়। ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। শুরু হয় নতুন করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এন.ডি.এফ, পি.ডি.এম জোটদ্বয়সহ ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে ‘ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি’ বা ডাক (DAC) গঠন করে। তবে ডানপন্থি ও বামপন্থিদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় ডাকের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালন করা কঠিন হয়।
১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে ‘ছাত্র সংগ্রাম কমিটি’ (Students Action Committee) গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ ছাড়া বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দাবিও ১১ দফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে ১১ দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। আইয়ুব বিরোধী মিটিং মিছিল সমাবেশ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণে আন্দোলন তীব্র হয়। সরকার পুলিশ, ই.পি.আর, সেনাবাহিনী দিয়ে আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা মোঃ আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা প্রক্টরিয়াল দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলে গণআন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।
সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানের উদ্ভবও ঘটে ওই সভায়। আইয়ুব খান আপস-মীমাংসার উদ্যোগ নেন। তিনি ১০-১৩ মার্চ (১৯৬৯) রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধী নেতাদের বৈঠকের আয়োজন করেন। ভাসানী ন্যাপ ও পিপলস পার্টি ওই বৈঠক বয়কট করলেও শেখ মুজিব বৈঠকে যোগদান করেন এবং ছয় দফা ও ১১ দফা দাবির পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেন। বৈঠকে ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডানপন্থি দলগুলি এ সিদ্ধান্তে খুশি হলেও আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ওয়ালী) বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে। এ দুদল ‘ডাক’ থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়।
ইতোমধ্যে আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও তীব্ররূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খান ২৪ মার্চ (১৯৬৯) তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ উক্ত নির্বাচনের ‘আইন কাঠামো আদেশ’ (Legal framework order)-এর মূল ধারাগুলি ঘোষণা করা হয়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ এ নীতিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। আইন কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ (১৩টি মহিলা আসনসহ) এবং তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭টি মহিলা আসন সহ ১৬৯টি আসন নির্ধারণ করা হয়। আদেশে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ‘শাসনতন্ত্র বিল’ নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে দেখা যায় যে, আইন কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদের অস্তিত্ব প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা হয়।
আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগ ছাড়া অন্য সকল দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিসমূহের ওপর ‘রেফারেন্ডাম’ হিসেবে অভিহিত করে। পাকিস্তানের প্রায় ১১টি দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তবে সকল শক্তিশালী রাজনৈতিক দল (যেমন আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ছিল আঞ্চলিক।
১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দুলক্ষ লোক নিহত হলে উক্ত অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণি-উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন একমাস পর অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টির মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পি.পি.পি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায় নি। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফলা ঘোষিত হওয়ার পর পরই পি.পি.পি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবি করেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধিত্বকারী পি.পি.পি-র সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। এর প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, যেহেতু এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক নয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছেন অতএব সংবিধান প্রণয়নে তা রদবদল সম্ভব নয়। এসব তর্ক-বিতর্কের মাঝে ইয়াহিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় বসবে।
কিন্তু ভুট্টো তাঁর মতামত গ্রহণের পূর্ণ অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। সকল সরকারি কর্মকান্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ৩ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে তিনি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেন– (ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে, (খ) অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং (ঘ) (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এ শর্তগুলি মানলেই কেবল তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগ যোগদান করবে কিনা।
১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সংগে বৈঠক করেন। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনায় যোগ দেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করছিলেন। অবশেষে সকল প্রস্ত্ততি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আকস্মিকভাবে গণহত্যা শুরু করে। পাকবাহিনীর এ নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, যা নয় মাস ধরে চলে। [মোঃ মাহবুবর রহমান]
বাংলাদেশ আমল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে (তিনি তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন) উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) শপথ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ।
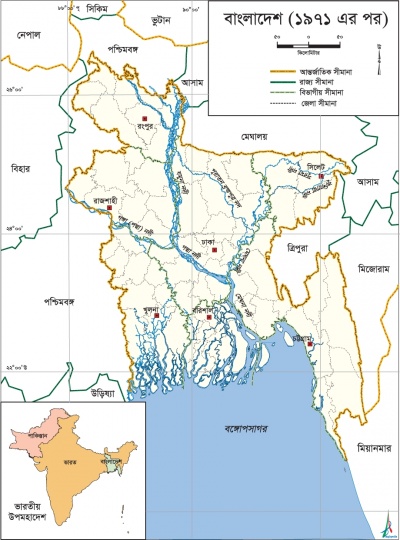
শেখ মুজিব সরকার (১৯৭১-১৯৭৫) পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত এবং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করেন। দু’মাসের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। দেশের প্রতিটি জেলায় বেসামরিক প্রশাসন সচল হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২টি লাভ করে। ন্যাপ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাতীয় লীগ ১টি করে, এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা ৫টি আসনে জয়লাভ করে। এরপর স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।
শেখ মুজিবের লক্ষ্য ছিল, ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত যে সামরিক-বেসামরিক আমলা এলিট শ্রেণী দেশ শাসন করছিল তাদের উপর রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীর নেতৃত্ব স্থাপন করা। অবশ্য সামরিক-বেসামরিক বাঙালি আমলাগণ বুঝতে পারেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সর্বাত্মক সমর্থন পেয়েছে। এখন থেকে রাজনীতিবিদগণই নেতৃত্ব প্রদান করবেন। তাছাড়া ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত অনেক সিনিয়র বাঙালি আমলা ও সামরিক কর্মকর্তা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে না আসতে পারায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও তারা বেশ দুর্বল ছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলিও দুর্বল এবং বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
শেখ মুজিব আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ‘ক্যারিশ্মা’ এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করেন। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের একটি অংশ রাষ্ট্রের চারটি মৌল নীতিকে (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা) ‘মুজিববাদ’ হিসেবে গ্রহণ করে।
যদিও সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা ছিল দুর্বল, তা সত্ত্বেও এ সময় বেশ কিছু বড় আকারের সমস্যার সমাধান হয়; যেমন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, অবকাঠামোগত পুনর্গঠন, অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া শিল্প কারখানা পরিচালনা, স্বীকৃতি এবং সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি। শিল্প কারখানা, ব্যাংক এবং বীমা স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়; যদিও রাষ্ট্রের স্বল্প সামর্থ্যের কারণে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বেশ সমস্যার সম্মুখীন ছিল।
বাংলাদেশের সামাজিক জীবনও তখন ছিল বেশ বিশৃংখল। একদিকে সমাজে ছিল পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি এবং তাদের বাঙালি সহযোগীদের বিচারের প্রবল দাবি, অন্যদিকে পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে তা বাতিল করার চাপ। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের একটি অংশ নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল যাদের ঘোষিত লক্ষ্য। দ্বিধাবিভক্ত কম্যুনিস্ট সংগঠনের অনেক গুলি গ্রুপ সারাদেশে শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কিছু মুক্তিযোদ্ধা এনজিও (বেসরকারি সংগঠন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে উদ্যোগী হন। স্বাধীন বাংলাদেশে এক বছরের মধ্যে এভাবেই এনজিও কর্মকান্ডের শুরু যা পরবর্তীকালে সমাজের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।
দেশের এ ধরনের পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি বাতিল এবং পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর শেখ মুজিব সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী বিরোধী বামপন্থি শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি আওয়ামী লীগের একান্ত অনুগত ব্যক্তিদের নিয়ে উগ্রপন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আধা-সামরিক ‘রক্ষী বাহিনী’ গঠন করেন।
আওয়ামী লীগের উপর ছিল দেশের সামগ্রিক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কাজের চাপ; কিন্তু অগ্রগতি ছিল খুবই ধীর। ফলে মানুষের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সময় আওয়ামী লীগের অনেক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ক্রমশ প্রকাশ পায়। একদিকে উগ্রপন্থি যুব নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের অধীনে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। অন্যদিকে মধ্যপন্থি অবলম্বনকারী নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত রাখার পক্ষাবলম্বন করেন। ১৯৭৪ সালের বন্যা, খাদ্য ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, বাংলাদেশকে ঋণ দানে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনিচ্ছা এবং ‘বাংলাদেশ সাহায্য সংস্থা’ গঠন করেও তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য না পাওয়ার পরিস্থিতিতে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও বিরোধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবাদপত্র ও বিচার ব্যবস্থার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেন।
১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব দেশে প্রচলিত সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ও বেআইনি ঘোষণা করে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। বাকশালের পাঁচটি ফ্রন্ট ছিল কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র এবং মহিলা। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ ঐতিহ্য ভেঙ্গে বেসামরিক আমলা এবং সেনা সদস্যগণও এ দলে যোগদানের অনুমতি পায়।
শেখ মুজিবের ভাষায় এটি ছিল ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’। একদলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের সূচনা হয়। মুদ্রামানের সংস্কার, আমদানি ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, খাদ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোগ, রফতানি প্রসারে নতুন কৌশল, শিল্পখাতে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, মূল্যমান নির্ধারণে খোলা বাজারের ভূমিকা প্রসার এমনি ধরনের বিভিন্ন সংস্কার নতুন উদ্যোগে শুরু হয়। জেলা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো, সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে একজন রাজনৈতিক প্রশাসনিক গভর্নর নিয়োগ, ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি গ্রামে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন ধীকল্প (idea)-এর সম্পূর্ণ প্রয়োগের পূর্বেই ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে গুটি কয়েক উচ্চাভিলাষী জুনিয়র সামরিক অফিসার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর উপস্থিত পরিবার পরিজন এবং তাঁর কিছু সহকর্মীকে হত্যা করে সাংবিধানিক ধারাকে ব্যাহত করে দেয়।
মুশতাক সরকার (১৯৭৫) অভ্যুত্থানকারীরা খন্দকার মুশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত করে। মুজিব সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। একদিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে আটক করা হয় এবং অন্যদিকে মুক্তি দেওয়া হয় ইসলামপন্থি সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এবং চীনপন্থি মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কয়েকজন বন্দি নেতাকে। চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। খন্দকার মুশতাক তিন মাসেরও কিছু কম সময় ক্ষমতায় বহাল ছিলেন। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যেই জেলা গভর্নরের ধারণা বাতিল করা হয় এবং বেসামরিক আমলাগণ তাদের বিদ্যমান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হন। শেখ মুজিব সরকারের আনুকূল্য পাননি এমন বেশ কয়েকজন সিনিয়র আমলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি লাভ করেন।
নভেম্বরের ৩ তারিখে কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা বিগ্রেডিয়ার (পরে মেজর জেনারেল) খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে একটি পাল্টা অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন। খন্দকার মুশতাক ও ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী জুনিয়র অফিসারদের হটিয়ে বিগ্রেডিয়ার মোশাররফ সামরিক আইন জারি করেন। ওই দিনই তিনি মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই শেখ মুজিবের হত্যাকারী সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন অংশের হাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় চারজন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহম্মদ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান নিহত হন।
খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থান নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়। তিনদিন ধরে রাষ্ট্র পরিচালনায় অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। মুশতাক রাষ্ট্রপতি তবে ক্ষমতাহীন। কারাগারে বন্দি অবস্থায় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে এক সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ৭ নভেম্বর জাসদ এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের-এর অনুসারি সিপাহিদের বিদ্রোহে মোশাররফ এবং তাঁর সহযোগীগণ নিহত হন। ওই দিনই প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন।
মুশতাকের সরকার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাধিনায়ক মনোনীত করেছিলেন। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের হাতে তিনি বন্দি হন এবং ৭ নভেম্বর একটি সিপাহি অভ্যুত্থানের ফলে তিনি মুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর একটি সামরিক আইন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেকোন বিদ্রোহীর জন্য মৃত্যু দন্ডাদেশের বিধান করা হয়। কর্নেল (অব.) তাহের এবং জাসদের কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হন। পরে কর্নেল তাহেরকে সামরিক আদালতে বিচার করে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।
জিয়া সরকার (১৯৭৫-১৯৮১) ১৯৭৫ সালের সিপাহি অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমান একজন শক্তিশালী সামরিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনজন ডেপুটি মার্শাল ল’ এডমিনিস্ট্রেটরের একজন হিসেবে প্রায় এক বছরকাল জিয়া প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্ট এবং চিফ মার্শাল ল’ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিচারপতি সায়েমের কর্তৃত্ব বজায় থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জিয়া। ১৯৭৬ সালের ২৮ নভেম্বর বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল সামরিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে জিয়া সংবিধান সংশোধন করেন এবং রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। সংসদ বাতিল করা হয়। কূটনীতিবিদ এবং আমলাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ।
জিয়া সামরিক বাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। জিয়া রক্ষী বাহিনীকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে তিনি তাঁর ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দেন।
উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জিয়া রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ থাকলেও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ‘কলাবরেটর অর্ডার’ বাতিল এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ সময় ‘দালাল আইন’-এ আটককৃত অনেক ব্যক্তি মুক্তি পান। নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলি এ সময় পুনর্জীবিত হয়। জিয়া, ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিরও সমর্থন লাভ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভের পর ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে ২৩টি দল রাজনীতি করার অনুমতি লাভ করে।
১৯৭৭ সালের সংবিধান (সংশোধনী) আদেশে বাংলাদেশ সংবিধানে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য: (ক) বাংলাদেশের নাগরিক ‘বাঙালি’ নয় ‘বাংলাদেশী’ বলে পরিচিত হবে; (খ) ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ এবং সংবিধান শুরু করা হয় ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ দিয়ে; (গ) সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার হিসেবে; (ঘ) রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক সংহত ও সংরক্ষণ করবে; (ঙ) সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।
এক বছরের মধ্যে জিয়া রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগো দল) গঠন করেন। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সকল রাজনৈতিক মতাদর্শী মহল থেকেই তিনি সদস্য সংগ্রহ করেন। অবসরপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এ দলে যোগ দেন। সামরিক শাসনের অধীনে কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের গণভোট; ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালে সংসদীয় নির্বাচন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৭, আওয়ামী লীগ ৩৯, মুসলিম লীগ এবং ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ ২০, জাসদ (সিরাজ) ৮, আওয়ামী লীগ (মিজান) ২, গণফ্রন্ট ২, জাতীয় লীগ ২, এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা ১৬টি আসন পায়। নব গঠিত সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ৪ বছরের সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদান করা হয়।
চার বছরের সামরিক শাসনে জিয়া দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সকলের অংশগ্রহণে খাল খননের মতো উন্নয়ন কর্মকান্ড হাতে নেন এবং ‘গ্রাম সরকার’ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনকালে বেশ কয়েকটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এমনি এক অভ্যুত্থানে ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়া চট্টগ্রামে নিহত হন।
সাত্তার সরকার (১৯৮১-১৯৮২) জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর উপ-রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সামরিক বাহিনীর চাপে সাত্তারের সরকার প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধানকে সদস্য করে একটি ‘জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল’ গঠন করে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারি, সংবিধান স্থগিত, সাত্তার সরকারকে বরখাস্ত, সংসদ বাতিল এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। নৌ এবং বিমান বাহিনী প্রধানদ্বয় এরশাদের ডেপুটি নিযুক্ত হন। এরশাদ সামরিক আইনে পরবর্তী ৪ বছর দেশ শাসন করেন।
এরশাদ সরকার (১৯৮২-১৯৯০) বেসামরিক আমলা এবং সামরিক সদস্যদের নিয়ে এরশাদের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। তিনি যথার্থই একজন সামরিক একনায়কের মতো আচরণ শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে সংবিধান সংশোধনের (৮ম সংশোধনী) মাধ্যমে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করেন। প্রায় সব সেক্টরেই বেসরকারি বিনিয়োগকে তিনি উৎসাহিত করেন।
এরশাদ দু’বার রাজনৈতিক দল গঠন করেন ১৯৮৩ সালে ‘জন দল’ এবং ১৯৮৬ সালে ‘জাতীয় পার্টি’। জাতীয় পার্টি গঠিত হয় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক আমলা এবং বিভিন্ন দল থেকে আগত রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে। এরশাদের আমলে অনেকগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এগুলির মধ্যে ছিল স্থানীয় সরকার নির্বাচন (১৯৮৪), গণভোট (১৯৮৫), জাতীয় সংসদ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (১৯৮৬) এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৮৮)। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি পায় ১৫৫টি আসন। আওয়ামী লীগ ৭৪, জামায়াতে ইসলাম ১০, সিপিবি ৫, ন্যাপ ঐক্য ৫, মুসলিম লীগ ৪, জাসদ (রব) ৪, বাকশাল ৩, জাসদ (সিরাজ) ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) ৩, ন্যাপ (মোজাফফর) ২, এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা ৩২টি আসন লাভ করে। ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১, সম্মিলিত বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ব্যতীত) ১৯, ফ্রিডম পার্টি ২, জাসদ (সিরাজ) ৩, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ২৫টি আসন পায়। বিএনপি এরশাদ আমলের সকল নির্বাচন বয়কট করে। আওয়ামী লীগ ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ নিলেও ১৯৮৮ সালের নির্বাচন বয়কট করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এরশাদ উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন।
১৯৮৩ সালে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং তা এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছে ১৯৮৭ সালে এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৯০ সালে। এ সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি’র ছাত্র সংগঠন দুটি সহ অন্যান্য সকল ছাত্র সংগঠন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। সিভিল সোসাইটি বিশেষ করে পেশাজীবী সংগঠনসমূহ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একাধিকবার জরুরি অবস্থা জারি করেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সিনিয়র অফিসারগণ এরশাদের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করলে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করেন। বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত একজন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে এ দায়িত্ব গ্রহণ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করেন। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এভাবেই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জনগণের আন্দোলনের ফলে সরকার পরিবর্তন হয়।
৯০ দিনের মধ্যে সাহাবুদ্দীন আহমদের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়। দেশি ও বিদেশি সকল মহল থেকে এ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি ১৪৪, আওয়ামী লীগ ৮৮, জাতীয় পার্টি ৩৫ এবং জামায়াতে ইসলাম ১৮টি আসনে জয় লাভ করে। এ ছাড়া বাকশাল ও সিপিবি ৪টি করে, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, এনডিপি, জাসদ (সিরাজ), ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ২টি আসন পায়। ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মধ্যে বিএনপি ২৮ এবং জামায়াতে ইসলাম ২টি লাভ করে।
খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলাম-এর সমর্থনে খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেন। সংসদে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একত্রে সংবিধান সংশোধনীতে (দ্বাদশ সংশোধনী) অংশ নেয় এবং দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।
এ সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ প্রদান, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ এ সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন।
প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। মিউনিসিপ্যাল এবং সংসদের উপ-নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মতবিরোধ চরমে পৌঁছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ মাগুরার উপ-নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে সরকারের পদত্যাগ দাবি এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। নির্বাচনকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব মুক্ত করার যুক্তি জনগণের সমর্থন লাভ করে। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে এবং পরবর্তী দু’বছর সংসদের বাইরে নানা ধরনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে অংশ নেয়। সংসদের অপর দু শরিক দল জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামও একই ইস্যুতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করে।
সিভিল সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী দুটি প্রধান দলের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কমনওয়েলথ সচিবালয় থেকে প্রেরিত একটি মিশন, ঢাকাস্থ দূতাবাসগুলির রাষ্ট্রদূত, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি’র দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেগম খালেদা জিয়া সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপি’র অধীনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত বিরোধী দল এ নির্বাচন বয়কট করে।
১৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি’র দীর্ঘ দিনের যুদ্ধংদেহী মুখোমুখি অবস্থানে তীব্র সংকটের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। খালেদা জিয়া সরকার তত্ত্বাবধায়ক সকারের অধীনে নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।
১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নতুন সংসদের একটি মাত্র অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে গৃহীত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার পর সংসদের মেয়াদ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬, বিএনপি ১১৬, জাতীয় পার্টি ৩২ এবং জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসন লাভ করে। এ ছাড়া জাসদ (রব) ১টি এবং নির্দলীয় প্রার্থীগণ ২টি আসনে জয়ী হয়। সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ মনোনীত হন।
শেখ হাসিনা সরকার (১৯৯৬-২০০১) ১৯৯৬ এর ২৩ শে জুন তারিখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন (৯ অক্টোবর, ১৯৯৬)। সকল দলের সহযোগিতায় একটি ঐকমত্য সরকার গঠনের জন্য শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে ঐকমত্য সরকারে যোগদানে বিএনপি রাজি না হলেও জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সরকারে যোগ দেয়।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতিপয় কমিশন গঠন করেন। সরকারি এবং বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে গঠিত এ সকল কমিশন শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন এবং প্রশাসন সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ প্রদান করে। নতুন শিল্প ও স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের হত্যাকারীদের বিচারের জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয় এবং হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার কাজ শুরু হয়। হাসিনা সরকার ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছরের গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি এবং ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিএনপি অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করতে থাকে। বিএনপি সংসদের উপ-নির্বাচনগুলিও বয়কট করে।
২০০১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগ তাদের সরকারের পূর্ণ মেয়াদ শেষ করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ২১৪টি আসনে জয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ ৬২, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ১৪, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ১, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৬টি আসন পায়। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে চার দলীয় ঐক্য জোট খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর সরকার গঠন করে। [আকসাদুল আলম]
খালেদা জিয়া সরকার (২০০১-২০০৬) আমলে একদিকে যেমন আর্থ-সামাজিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তেমনি তা দুর্নীতিরও জন্ম দিয়েছে। ২০০২-০৬ সময়কালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পর পর চার বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে থেকেছে। জনপ্রতি জাতীয় আয় ২০০০-০১’এর ৩৭৪ মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪৮২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমান ২০০১ সালের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬’এর শেষে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপী এমএফএ কোটা প্রথা বিলুপ্তির পরেও অংশত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় ভূমিকার কারণে তৈরি পোশাক খাতের বিকাশও অব্যাহত থাকে এ সময়ে।
বি.এন.পি সরকারের অনুসৃত বিনিয়োগ-বান্ধব অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কৌশলের ফলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান-স্যাক্স’এর দৃষ্টি আকর্ষন করে, যারা বাংলাদেশকে ১১টি দ্রুত প্রাগ্রসরমান দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০২-০৬ মেয়াদকালে দেশে প্রত্যেক বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২.৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে; মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত সাড়ে চার বছরে ৬২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব সম্বলিত ৯ হাজার শিল্প প্রকল্প বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত হয়, যা ছিল পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। এর ফলে জিডিপি’তে শিল্পখাতের অবদান ১৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় এবং এখাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১০ শতাংশ অতিক্রম করে।
জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) সরকার একটি মধ্যম-মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির জন্য প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় এবং ২০০৫-০৬ অর্থ-বছরে এর হিস্যা দাঁড়ায় মোট বরাদ্দের ৫৬ শতাংশ। সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের চরম দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিও সম্প্রসারণ করে।
২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৯ শতাংশ হ্রাস পায়। সরকার পরিবেশ সংরক্ষণেও কিছু উলেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে ছিল ২০-বছরের অধিক পুরোনো বাস ও ট্রাককে ঢাকার রাস্তা থেকে প্রত্যাহার করা এবং ২-স্ট্রোকের ডিজেল-চালিত বেবি-টেক্সির পরিবর্তে সড়কে ৪-স্ট্রোক সিএনজি-চালিত বেবি-টেক্সির প্রবর্তন। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও বিপণনও সারা দেশে নিষিদ্ধ করা হয়।
শিক্ষাখাতেও বি.এন.পি সরকার কিছু সাফল্য অর্জন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তির হার ৯৭ শতাংশে পৌঁছায়, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়, প্রায় ২ কোটি ছাত্রী শিক্ষাবৃত্তি লাভ করে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়নের পাশাপাশি খালেদা সরকার কওমি মাদ্রাসার ‘দাওরা’ সনদকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফাজিল-কামিল ডিগ্রিকে ব্যাচেলরস ও মাস্টারস ডিগ্রির সমমান ঘোষণা করে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি খাতে বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
সাধারন মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বি.এন.পি সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত একটি ইউনিসেফ রিপোর্টে দাবি করা হয় যে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নততর। মানুষের গড় আয়ু এসময় বৃদ্ধি পায় এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.৪৭ শতাংশে নেমে আসে।
বি.এন.পি সরকার টেলিযোগাযোগ খাতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এবং এসময়েই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সাবমেরিন কেবলের সাথে সংযুক্ত হয়। সরকার ১৫টি নতুন উপজেলা সৃষ্টি করে, যার ফলে উপজেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮০। দেশে প্রথমবারের মতো একটি কর-ন্যায়পাল এর পদও সৃষ্টি করা হয়। এসময়েই ঢাকা ও ভারতের আগরতলার মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হয় এবং ঢাকা ও ভারতের কলকাতার মধ্যে রেল চলাচলের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া যমুনা সেতুর উপর দিয়ে দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রেল-সংযোগও এসময়ে স্থাপিত হয়্। এ সময়ে যে কয়টি সড়ক সেতু নির্মিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পদ্মা নদীর উপর ‘ফকির লালন শাহ (পাকশী ) সেত’ু এবং রূপসা নদীর উপর ‘খান জাহান আলী সেতু’।
বি.এন.পি সরকারই জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উত্তরসূরি হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এ সময়ে এর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা কখনোই সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না এবং এর বিরূদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও আনা হয়েছিল। এ সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০০৫ সালে নতুন জাতীয় বেতন-স্কেল প্রবর্তন।
২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জনসভায় ভাষণ দানকালে সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গ্রেনেড হামলায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ঘটনার পর মামলার তদন্তে সরকারের ঢিলেমী ও উদ্দেশ্যমূলক আচরণ নানা সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। বি.এন.পি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে (২০০১-২০০৬) জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) মতো জঙ্গি-গোষ্ঠীর উত্থানও পরিলক্ষিত হয়, যারা ২০০৪ থেকে ২০০৬ সময়ে বিচারক ও আইনজীবীসহ অনেক নিরীহ লোককে হতাহত করে এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টিতে একযোগে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে এ সময়েই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী শায়খ আবদুর রহমান ও বাঙলাভাই সহ জেএমবি’র শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়্। পরবর্তীতে আদালতের রায় অনুযায়ী তাদের অনেককেই ফাঁসি দেওয়া হয়।
বি.এন.পি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, শান্তি বিনির্মাণ কমিশন ও ইকোসক (ECOSOC) সহ জাতিসংঘের ১৩টি সংস্থায় ও আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামেরও সদস্যপদে নির্বাচিত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে বিশ্ব-শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সরকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের যুদ্ধে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করে, আবার এর পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সঙ্গেও পারস্পরিক কল্যাণকর সম্পর্কের উন্নয়নে প্রয়াস চালায়।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮) ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বি.এন.পি সরকার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়। দেশব্যাপী ক্রমাগত রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের অস্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তদানিন্তন নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে আরেকটি অচলাবস্থা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর চাপে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ১১ই জানুয়ারি ২০০৭’এ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করেন। এর পরদিন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।
দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কয়েকটি মৌলিক ও কাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। নিরপেক্ষ সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন ও বিধি সংস্কারের খসড়া প্রস্ত্তত করে, এবং সেগুলো সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত করে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ দ্রুত শুরু করা হয়। ২০০৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৮০ কোটিরও অধিক ভোটারের নাম নিবন্ধিত করে তাদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর তারিখে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের কাজটিও প্রথমবারের মতো সমাধা করে। ম্যাজিস্ট্রেসিকে নির্বাহী ও বিচারিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সকল বিচারিক আদালতকে সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসা হয়।
দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সরকারি কর্ম কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন। সরকারি আইন ও বিধিমালার সরলিকরণ এবং ব্যক্তি-উদ্যোগকে সহজতর করতে ‘রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন’ ও ‘বেটার বিজনেস ফোরাম’এর মতো নতুন সংস্থা গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ট্রুথ কমিশন স্থাপন অনুমোদন করে। একটি তিন-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের আওতায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং একটি স্থানীয় সরকার কমিশনও গঠন করা হয়্। সরকারি সংস্থার সেবাদান কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে ‘নাগরিক সনদ’, ‘সেবা-মান’, ‘মডেল থানা’, ‘হেল্প-ডেস্ক’, ‘হেল্প-লাইন’, এবং ‘ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস’এর মতো ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন করা হয়। সরকারি চাকুরেদের পেনশন ও অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান দ্রম্নততর করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়; কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ছাড়াও ১৭টি জেলা প্রশাসন অফিস থেকে পাসপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি পদক্ষেপের ফলে চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দরের দক্ষতা আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং জাহাজসমূহের ‘টার্ণ-অ্যারাউন্ড’ সময় পূর্বের ১১ দিন থেকে ৩ দিনে নেমে আসে।
ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল স্তরে দুর্নীতির বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে পদ বা অবস্থান নির্বিশেষে সন্দেহভাজন দুর্নীতিগ্রস্থদেরকে বিচারের আওতায় আনার প্রয়াস চালানো হয়। এর ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ অনেক রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন হন। তাদের বিরূদ্ধে প্রচলিত আইনের আওতায় বিচারিক আদালতসমূহে মামলা রজু করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয় এবং দুর্নীতির বিরূদ্ধে নিবারক, নিরাময়মূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মজবুত করা হয়। কমিশনকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদেও স্বাক্ষর করে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বৈরী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৪ শতাংশ ও ৬.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। রপ্তানি আয় ১৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, আবার প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে ৩০ শতাংশ অতিক্রম করে। সরকারের বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের ফলে বিদেশে প্রেরিত বাংলাদেশী কর্মীদের সংখ্যা ২০০৭-২০০৮ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ অব্যাহতভাবে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে থাকে।
২০০৭’এর জুলাই ও আগস্টে দেশ পরপর দুটি ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়। এর ফলে প্রচুর জান-মাল, শস্য ও অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে উৎপাদন ক্ষতি ২৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। আমন ফসলের ক্ষতি হয় প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর আঘাত হানে ১৯৭০ সালের পর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন, আশ্রয়, সঞ্চয় ও জীবিকা হারায়। ‘সিডর’এর ফলে অবকাঠামো ও শস্যের যে ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১৪০ বিলিয়ন টাকায়।
বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে যথাক্রমে প্রায় ৯ মিলিয়ন ও ৮ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার খাদ্য-নিরাপত্তা বাজেটের ২১ বিলিয়ন টাকা এখাতে পুনর্বন্টন করে। ঘূর্ণিঝড়ের শিকার জনগণকে ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে ৬ মাসের জন্য খাদ্য সহায়তা দিতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ২.৬ মিলিয়ন ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করা হয়।
২০০৭ ও ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। জ্বালানি তেলের মূল্য ২০০৬ সালের ব্যারেলপ্রতি ৫৬ মার্কিন ডলার থেকে তিন গুণ বেড়ে ২০০৮ সালে ১৪৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। অন্যান্য জ্বালানি ও প্রাথমিক পণ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। জৈব জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজাত পণ্যের মূল্যও দ্রম্নত বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী খাদ্রদব্যের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, যা বাংলাদেশের মতো আমদানিকারক দেশের ভোক্তাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে দারুণভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। এসকল বহিঃস্থ আঘাত মোকাবেলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু বৈশ্বিক সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলোর সাফল্য ছিল সীমিত।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলেরর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রায় ১ বছর কারান্তরীণ রাখার পর ২০০৮ সালের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে প্যারোলে মুক্তি প্রদান করে। এরপর নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর দেশ থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। তত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে, যাতে সকল প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট অংশ নেয়। এতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৬৩ আসন পেয়ে এক অসাধারণ বিজয় অর্জন করে। বিএনপি পায় মাত্র ২৯টি আসন; তবে পরবর্তীতে বাকী ১ আসনে বিজয়ী হয়ে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ। আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩০টি আসন পায়, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) পায় ২৭টি আসন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু) ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ২, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১ এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা পায় ৪টি আসন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে শপথ গ্রহণ করে।
শেখ হাসিনা সরকার (২০০৯ -চলতি) নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়ের ভিত্তি ছিল একটি আকর্ষণীয় নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, যাকে শেখ হাসিনা রূপকল্প-২০২১ সম্বলিত ‘পরিবর্তনের সনদ’ আখ্যা দিয়েছিলেন। এতে ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিভিন্ন খাতে অগ্রগতির একটি রূপকল্প সন্নিবেশিত ছিল। এর অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলো ছিল; দ্রব্যমূল্যকে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ; দুর্নীতি দমনে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন এবং ক্ষমতাশালীদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী জমাদানের বিধান প্রচলন; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ; কৃষিখাতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মূল কৌশল হিসেবে চরম দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ; সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উগ্রবাদ নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা; সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি অব্যাহত রাখা, মানবাধিকার কমিশন শক্তিশালী করা, ন্যায়পাল নিয়োগ এবং প্রশাসনকে রাজনীতিকরণ থেকে মুক্ত করা।
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে হাসিনা সরকারের সাফল্য ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মিশ্র থেকেছে। সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই ২২ জানুয়ারি তারিখে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের প্রার্থী ও কর্মীদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এর পরের মাসেই ঢাকাস্থ বাংলাদেশ রাইফেলস সদর দপ্তরে সাধারণ সৈন্যদের বিদ্রোহে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ ব্যক্তি নিহত হয়।
আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের প্রথম বছরে বহুল প্রশংসিত একটি সাফল্য ছিল সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী খুনীদের ফাঁসি জেলখানায় কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে ছিল: জাতীয় সংসদে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) বিল ২০০৯ পাশের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করা; সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা; দেশের শেয়ার বাজার শক্তিশালীকরণের জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ৫০টি মার্চেন্ট ব্যাংককে ব্যবসা চালানোর অনুমতি প্রদান; দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো অনুমোদন; শাসনকার্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রণীত বিভিন্ন আইন জাতীয় সংসদে পাস করা; দুঃস্থ, আশ্রয়হীন ও চরম দরিদ্রদের আবাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ৩ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে আশ্রায়ন প্রকল্প পুনঃপ্রবর্তন; দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ‘দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র’ অনুমোদন; এবং ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ।
খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে হাসিনা সরকার ‘একটি বাড়ী একটি খামার’ প্রকল্প পুনরায় চালু করেছে; ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে, যার নির্মাণ ২০১৩ সালের মধ্যে শেষ করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে; বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্মিত ১০ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় সচল করা হয়েছে এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; দেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের জন্য একটি ৫-বছর মেয়াদী স্বকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে; দেশে তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
পাট ও পাটজাত দ্রব্যকে একটি পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সামগ্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে; সংসদে পাস হওয়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে একটি তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে; চাকরিরত মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের বয়স দুই বছর বাড়ানো হয়েছে; ২০১০-২০১৫ সাল মেয়াদের জন্য সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে; একটি নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তিখাতের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনার বিকাশ ও বিশেষত জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের সুচারু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ২০০৯-১০ সালে ৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। একই ভাবে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স ২০০৯-১০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৪ বিলিয়ন ও ১০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।
দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ‘শিক্ষা কমিশন’ গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশমালা সরকার ‘জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০’ হিসেবে অনুমোদন করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাকে কর্মমুখী ও প্রযুক্তি-নির্ভর করা এবং জাতির মৌলিক মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা। এর সাথে সঙ্গতি রেখে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ‘জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা’ প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা শৃঙ্খলাবদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ‘প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯’ পাস হয়েছে, যা সকল মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট আইন পাস, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত ট্রাইবুনাল গঠন এবং আইনজীবী ও তদন্তকারী প্যানেল নিয়োগের পর ২০১০ সালে দেশে সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজও শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ কয়েকজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে এবং একটি উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ইমেজ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে শেখ হাসিনা কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছেন। চীন ও মিয়ানমারকে অন্তর্ভুক্ত করে এই সহযোগিতা সম্প্রসারণেও তিনি প্রয়াস চালাচ্ছেন।
হাসিনা সরকার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে নিরাপত্তা সহযোগিতা শক্তিশালীকরণেরও প্রয়াস চালিয়েছে। তিনি বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশি সন্ত্রাসীদের বিরম্নদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া দেশে ডান ও বাম উভয় প্রান্তের চরমপন্থীদের বিরম্নদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন।
পূববর্তী বি.এন.পি সরকারের ন্যায় বর্তমান সরকারের বিরূদ্ধেও কখনো কখনো প্রশাসনকে রাজনীতিকরণ ও দলীয় স্বার্থে পুলিশ ও বিচার বিভাগকে ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। [হেলাল উদ্দিন আহমেদ]
