মৎস্য উৎপাদন
মৎস্য উৎপাদন বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এ দেশ বিশাল জলসম্পদে সমৃদ্ধ। সারাদেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর। তার দক্ষিণে অন্তহীন সমুদ্র। মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে এ দেশের সর্বত্র। তাতে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ। এ সব মাছ সুস্বাদু ও সহজপাচ্য। মাছ তাই বাঙালিদের কাছে অতি প্রিয়। মাছ আর ভাত ছাড়া বাঙালির খাবার মনঃপূত হয় না। তার তৃপ্তি মেটে না। বাঙালির খাদ্যে মাছ এবং ভাতেরই প্রাধান্য। অনাদিকাল থেকে মাছ এবং ভাতের উপর বাঙালিদের নির্ভরতার কারণে এ দেশের মানুষের পরিচয় হয়েছে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’।
জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্থুল জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৪ ভাগ এবং কৃষির উৎপাদনে শতকরা ২১ ভাগ। জাতীয় রফতানি আয়ে মৎস্য খাতের শরিকানা শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৫৮ ভাগ সরবরাহ আসে মাছ থেকে। এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে প্রায় ১৩ লাখ শ্রমিক সার্বক্ষণিকভাবে এবং ১ কোটি ২৫ লাখ শ্রমিক খন্ডকালীনভাবে নিয়োজিত আছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য মোচনে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে মৎস্য খাতের উন্নয়ন নিতান্ত অপরিহার্য।
মৎস্য উৎপাদন বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে প্রধানত অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রয়েছে মুক্ত জলাশয় ও বদ্ধ জলাশয়। মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে আছে প্লাবন ভূমি, নদী, বিল, কাপ্তাই হ্রদ ও সুন্দরবন। এর আয়তন ৪০.৪৭ লাখ হেক্টর, যা মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা ৮৮.৪৬ ভাগ। বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে আছে পুকুর, মরা নদীর অংশ বা বাঁওড় ও উপকূলীয় চিংড়ি খামার। এর আয়তন ৫.২৮ লাখ হেক্টর, যা মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ১১.৫৪ শতাংশ। আমাদের সমুদ্র তটরেখা ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ। অর্থনৈতিক এলাকা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট সামুদ্রিক জলসম্পদের আয়তন ১৬৬ লাখ হেক্টর, যা দেশের মোট জলসম্পদের ৭৮.৩৯ শতাংশ।
জলাশয়গুলো ঋতু, আবহাওয়া, জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে অহরহই আকৃতি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের শিকার হচ্ছে। কিন্তু বছর ভিত্তিক প্রদত্ত পরিসংখ্যানে তার তেমন প্রতিফলন ঘটছে না। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে জলাশয়ের পরিমাণ হালনাগাদ করা উচিত।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি এবং ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছ রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের সামুদ্রিক এলাকায় রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, যার মধ্যে কেবল ৬৫ প্রজাতির মাছ আহরণযোগ্য। তাছাড়া আছে ৩৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, ৩ প্রজাতির লবস্টার, ২৫ প্রজাতির কাছিম ও ১১ প্রজাতির কাঁকড়া। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এর জীব-বৈচিত্র্য অত্যন্ত বিস্তৃত। তবে এর উৎপাদন ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।
এ দেশে মাছের বার্ষিক উৎপাদন ২৫.৬৩ লাখ মেট্রিক টন (২০০৭-২০০৮ সালের তথ্য অনুসারে)। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ ৮০.৫৯ শতাংশ এবং সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে প্রাপ্ত মাছের হিস্যা ১৯.৪১ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত মাছের শতকরা ৪১.৩৬ ভাগ সরবরাহ আসে মুক্ত জলাশয় থেকে এবং ৩৯.২৩ ভাগ আসে বদ্ধ জলাশয় থেকে। সামুদ্রিক মৎস্যের শতকরা ৯৩.১৩ ভাগ যোগান আসে আর্টিশনাল বা চিরায়ত আহরণ পদ্ধতির মাধ্যমে, আর বাকি ৬.৮৭ শতাংশ আসে ট্রলার কেন্দ্রিক শিল্পায়িত আহরণের মাধ্যমে। বছরের পর বছর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের হিস্যা হ্রাস পেয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ আহরণের হিস্যা বেড়েছে। এর কারণ সামুদ্রিক আহরণের প্রবৃদ্ধির হার কম, অভ্যন্তরীণ আহরণের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে বদ্ধ জলাশয় তথা চাষাধীন জলাশয় থেকে আহরণের প্রবৃদ্ধির হার বেশি বিধায় মোট মৎস্য উৎপাদনে এ হিসস্যা দ্রুত বেড়েছে। গত দশকে (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৭-০৮) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে মৎস্য আহরণের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.৪৪, ৫.৮৬ এবং ৫.২৬ ভাগ। এ সময় মাছের মোট উৎপাদন বেড়েছে বার্ষিক শতকরা ৫.৫৭ শতাংশ হারে (সারণি ১)।
অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মৎস্য আহরণ
অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্যে। এর পেছনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশের বদ্ধ জলাশয়ে হেক্টর প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ২.৬ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এই উৎপাদন সহজেই ৪.০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের ধীর গতির পেছনে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ। তদুপরি বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও জীবনচক্রের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অধিকন্ত প্লাবন ভূমি হ্রাস পাওয়ার কারণে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। ফলে মাছের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হচ্ছে না। এ উৎস্য থেকে মাছের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা মজুদ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হচ্ছে। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার। মাছের প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃ খনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন করা দরকার। তাছাড়া মুক্ত জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট জলমহালগুলো মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা উচিত।
অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো উন্নত পদ্ধতিতে মাছের চাষ। এর জন্য কাঙ্ক্ষিত জাতের গুণগত মান সম্পন্ন পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় শতাধিক হ্যাচারী স্থাপিত হয়েছে ব্যক্তি মালিকানায়। এদের মান নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত দরকার। তাছাড়া বিদেশ থেকে যেন থাই মাগুর ও পিরানহা ধরনের রাক্ষুসে মাছ এদেশে প্রবেশ করতে না পারে এবং আমাদের জলাশয়ে ছড়াতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
ইলিশ মাছ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ অংশ দখল করে আছে। কিন্তু নির্বিচারে মা মাছ এবং জাটকা আহরণ ও নিধনের ফলে এর উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সে কারণে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ইলিশের অভয়াশ্রম নির্ধারণ ও তা কার্যকরকরণ, প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখা ও জাটকা নিধন বন্ধকরণ কর্মসূচিকে জোরদার করতে হবে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মা মাছ নিধন ও জাটকা মাছ আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও একান্ত দরকার।
সামুদ্রিক উৎস থেকে মৎস্য আহরণ
মাছের মজুদ কমে আসা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হ্রাস পাবার প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেন। তবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রকৃত পরিসংখ্যান নিয়েও অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের মতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। চিরায়ত ও শিল্পায়িত আহরণ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া না গেলে এতদসংক্রান্ত দ্বিমতের অবসান হবে না। এ লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তাছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য মজুদের পরিমাণ এবং বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের গতিবিধি জানার জন্যে নিয়মিত জরিপ চালানো প্রয়োজন। তাতে সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলো উপকূলের কাছাকাছি থেকে বেশিরভাগ মাছ আহরণে নিয়োজিত। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা জোরদার করা হলে মাছের মোট আহরণ বৃদ্ধি পাবে। উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির পোনা ধরার সময় বহু সংখ্যক অন্যান্য প্রজাতির মাছের পোনা ও জলজ প্রাণী ধ্বংস করা হয়। তাতে সামুদ্রিক মাছের মজুদ হ্রাস পায়। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির পোনা আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কাজে নিয়োজিত লোকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব।
১৯৯২-৯৩ সালে মোট রফতানি বাণিজ্যে মাছের শরিকানা ৭.৫৭ শতাংশ থেকে ২০০৭-০৮ সালে হ্রাস পেয়েছে ৪.৪ শতাংশে। কিন্তু মাছ রফতানির পরিমাণ বেড়েছে ২৬,৬০৭ মেট্রিক টন থেকে ৭৫,২৯৯ মেট্রিক টনে। আয় বেড়েছে ৭০০.২৯ কোটি থেকে ৩৩৯৬.২৮ কোটি টাকায়। এ সময় মাছের মোট রফতানি আয়ে চিংড়ির শরিকানা কমেছে শতকরা ৮৬.২৫ ভাগ থেকে ৮৪.৩২ ভাগে। অপরদিকে হিমায়িত মাছের হিস্স্যা বেড়েছে। আমাদের রফতানি বাণিজ্যে চিংড়ি একটি বড় এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে। বর্তমানে রফতানিকৃত চিংড়ির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বাগদা এবং ২০ ভাগ গলদা চিংড়ি। জানা যায়, চিংড়ি রফতানিকারক কোন কোন ব্যবসায়ী চিংড়িতে পেরেক ঢুকিয়ে দেয় ওজন বৃদ্ধির জন্য। তাছাড়া ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে চিংড়ি খামারে। তাতে আমাদের রফতানি বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।
সারণি ১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ের আয়তন ও মৎস্য উৎপাদন (২০০৭-০৮)।
| জলায়তন (হেক্টর) | উপাৎন (মে টন) | শতকরা অংশ | উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর) | |
| ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয় | ||||
| (১) মুক্ত জলাশয় | ||||
| ১. নদী ও মোহনা | ৮৫৩, ৮৬৩ | ১৩৬, ৮১২ | ১৬০ | |
| ২. সুন্দরবন | ১৭৭, ৭০০ | ১৮,১৫১ | ১০২ | |
| ৩. বিল | ১১৪, ১৬১ | ৭৭,৫২৪ | ৬৭৯ | |
| ৪. কাপ্তাই লেক | ৬৮,৮০০ | ৮,২৪৮ | ১২০ | |
| ৫. প্রাবনভূমি | ২,৮৩২,৭৯২ | ৮১৯,৪৪৬ | ২৮৯ | |
| মোট | ৪,০৪৭,৩১৬ | ১,০৬০,১৮১ | ৪১.৩৬% | |
| (২) বদ্ধ জলাশয় | ||||
| ১. পুকুর | ৩০৫,০২৫ | ৮৬৬,০৪৯ | ২,৮৩৯ | |
| ২. বাঁওড় | ৫,৪৮৮ | ৪,৭৭৮ | ৮৭১ | |
| ৩. চিংড়ি খামার | ২১৭,৮৭৭ | ১৩৪,৭১৫ | ৬১৮ | |
| মোট | ৫২৮,৩৯০ | ১,০০৫,৫৪২ | ৩৯.২৩% | |
| অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট) | ৪,৫৭৫,৭০৬ | ২,০৬৫,৭২৩ | ৮০.৫৯% | |
| খ. সামুদ্রিক জলাশয় | ||||
| ১. ট্রলার | ৩৪,১৫৯ | |||
| ২. আর্টিসেনাল | ৪৬৩,৪১৪ | |||
| সামুদ্রিক জলাশয় (মোট) | ৪৯৭,৫৭৩ | ১৯.৪১% | ||
| সর্বমোট | ২,৫৬৩,২৯৬ | ১০০% |
বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি চিংড়ির চাহিদা ও রফতানি বৃদ্ধির সঙ্গে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সাতক্ষীরায় গড়ে উঠেছে শতাধিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এ শিল্পগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতার শতকরা মাত্র প্রায় ৪০ ভাগ ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে ব্যবহূত হচ্ছে। কাঁচামালের অভাবে শিল্পগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে চিংড়ির প্রতি একক উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বাড়ানো গেলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সম্প্রসারিত চিংড়ির চাষ লাভজনক প্রতীয়মান হলেও উপকূলীয় এলাকায় এ কারণে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ এলাকা বৃদ্ধির জন্য এখন বেশি করে উদ্যোগ নেয়া উচিত।
মাছ একটি পচনশীল পণ্য। আহরণের পরই এর বাজারজাত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু দেশের অনুন্নত অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থার কারণে মাছের বাজার দক্ষ নয়। তাছাড়া বরফ দেয়া, প্রক্রিয়াজাত করা, ক্রমানুসারে সাজানো, হিমায়িত করা ইত্যাদি কাজগুলো সঠিকভাবে করা হয় না বলে ভোক্তার নিকট অনেক সময় গ্রহণযোগ্য অবয়বে মাছ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আহরণ থেকে ভোক্তার নিকট পেঁছে দেয়া পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মাছ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাছের বিপণন খরচ বেড়ে যায়। এক হিসেব মতে মাছের বিপণন খরচ ও মুনাফা ভোক্তা প্রদত্ত মূল্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। এটি বিপণন অদক্ষতারই পরিচায়ক। তাছাড়া মাছ আহরণের কাজটি এলাকা ও মৌসুম নির্ভর বিধায় স্থান ও কালভেদে মাছের মূল্যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। সময় ভেদে এ ব্যবধান শতকরা ৫৪ থেকে ৪৪৯ ভাগ এবং স্থান ভেদে ১৫ থেকে ৫৪ ভাগ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। মাছ হিমায়িতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহন ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে এ অসুবিধাগুলো ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব।
মাছের বড় বাজারগুলো সাধারণত মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বৃহৎ ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের হাতে জব্দ থাকে। তারা দাদন দিয়ে করায়ত্ত করে রাখে ছোট ব্যবসায়ী ও জেলেদের। ওদের মাধ্যমেই মাছের সরবরাহ নিশ্চিত রাখে বড় ব্যবসায়ীরা। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব থাকে। সে কারণে মাছের ব্যবসা বরাবরই বিক্রেতা শাসিত হয়, ক্রেতা শাসিত নয়। একই কারণে মাছের ব্যবসায়ীরা বিপণনের মান উন্নয়নকল্পে তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা অনুভব করে না। মাছের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যেও তারা কোনো বিনিয়োগে তেমন আগ্রহী হয় না। সমবায়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা এরূপ একচেটিয়া আধিপত্য থেকে উৎপাদক ও ভোক্তাদের রেহাই দিতে পারে। স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমেও মৎস্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা যায়।
মাছ একটি অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। বাংলাদেশে এর ঘাটতি প্রচুর। এর উৎপাদন ব্যবস্থাও তেমন দক্ষ নয়। সে কারণে এ দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বিস্তর। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ধারণ ত্বরান্বিত করে মাছের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচিকে জোরদার করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মৎস্য খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। [জাহাঙ্গীর আলম]
ইতিহাস মানব ইতিহাসের একেবারে আদিকালেও মাছ মানুষের খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। মাছের পেশীকলায় বা আমিষে ৬০-৮২% পানি, ১৩-২০% প্রোটিন এবং কম বেশি চর্বি থাকে। এগুলির জন্যই মাছ উপাদেয় খাদ্য এবং কেবল বাংলাদেশের মানুষেরই নয়, পৃথিবীর বহু জাতির কাছেও।
স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলার মানুষ খাদ্যের জন্য প্রকৃতির এই দান আহরণ করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরা যেন এক ধরনের শিকার। বাস্তবিকই, মাছ ধরা কৃষি কাজের চেয়েও পুরানো এবং মাছ সর্বদাই মানুষকে সুস্বাদু ও উচ্চমানের প্রোটিন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতি প্রদত্ত ও প্রধান আহার্য বিধায় ঐতিহ্যগতভাবে এই দেশের মানুষকে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’ বলে অভিহিত করা হয়।
ফ্রান্সিস হ্যামিলটনের (Hamilton, ১৮২২) গবেষণা থেকেই বাংলাদেশের স্বাদুপানির মৎস্যকুল সম্পর্কে জানার সূত্রপাত ঘটে। ফ্রান্সিস ডে ১৮৭৮ সালে উপমহাদেশের সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির মাছ সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বহু গবেষণাকর্ম পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যচাষ বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।
সাবেক বাংলার রাজস্ব বোর্ডের সদস্য কে.জি গুপ্ত কর্তৃক ১৯০৮ সালে প্রদেশের মৎস্য খাতের সম্ভাবনা বিষয়ে প্রথম অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার ফলেই মৎস্য অধিদপ্তর গঠিত হয় এবং পরে ১৯১০ সালে তা কৃষি বিভাগের অঙ্গীভূত হয়। ১৯১৭ সালে মৎস্য বিভাগ আলাদা করা হলেও যোগ্য লোকবলের অভাবে বাংলার ব্যয়সঙ্কোচন কমিটির (Bengal Retrenchment Committee) সুপারিশক্রমে ১৯২৩ সালে এটি বিলুপ্ত করা হয়। অবশ্য, মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) এম. আর নাইডুর সুপারিশে ১৯৪১ সালে বাংলার মৎস্যসম্পদের উন্নয়নকল্পে মৎস্য বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৪০ সাল থেকেই চিংড়িচাষ চলছে। চাষকৃত চিংড়ির প্রধান ক্রেতা ছিল কলকাতার বাজার। ভারত বিভক্তির পর বাংলাদেশের চিংড়ি চাষীরা কলকাতার বাজার হারায় এবং চিংড়িচাষ ক্রমে লোপ পেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার প্রভৃতি এলাকায় আবার চিংড়িচাষ শুরু হয়। ধানক্ষেতে মাছচাষ বাংলার পুরানো প্রথা। অবশ্য, ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার সম্প্রতি মাছচাষে বড় বাধা সৃষ্টি করছে।
মৎস্য আবাসস্থল (Fish habitats) নির্দিষ্ট আবাসস্থলে অভিযোজিত হওয়ার কারণে মাছকে স্বাদুপানির, স্বল্প লোনাপানির, সামুদ্রিক ও পরিযায়ী ইত্যাদি বাস্ত্তসংস্থানিক দলে ভাগ করা হয়েছে। স্বাদুপানির মাছ সর্বদাই স্বাদু পানিতে বাস করে। স্বল্পলোনাপানির মাছ সমুদ্রের স্বল্পলবণাক্ত অঞ্চল ও নদীর মোহনার বাসিন্দা। সামুদ্রিক মাছ সমুদ্রের পানিতে থাকে এবং মহাসাগরের উন্মুক্ত জলরাশির পৃষ্ঠভাগে বা উপকূলীয় লোনাপানিতে বসবাস করতে পারে। পরিযায়ী মাছ প্রজননের জন্য সমুদ্রের লোনাপানি থেকে স্বাদুপানিতে (ইলিশ, Tenualosa ilisha) অথবা স্বাদুপানি থেকে সমুদ্রের লোনা পানিতে যায়। (বাইম, Anguilla bengalensis)।
প্রধান নদীগুলি (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র) বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। বহু নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা সারাদেশে জালের ন্যায় বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রায় ৫৪টির পানি ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবহার করতে হয়। বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯১ সালে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, মাছের ফলন ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশে পানিসম্পদসহ (নদী, প্লাবনভূমি, পুকুর, বিল, বাওড় ও সুদীর্ঘ উপকূল) উপযুক্ত জলবায়ু ও পরিবেশ রয়েছে। বর্ষাকালে নদীর কূল উপচানো পানিতে প্রাকৃতিক খাদ ও সমভূমি, নিচু জমি, বদ্বীপ ও চরাঞ্চল ডুবে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক অভ্যন্তরীণ সমুদ্র গড়ে তোলে। আবার শুকনো মৌসুমে অধিকাংশ নদী শুকিয়ে খুবই ছোট হয়ে যায় এবং অধিকাংশ পুকুর ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে পড়ে।
সবগুলি নদীর গতিপথেই রয়েছে বিস্তৃত প্লাবনভূমি। খাল দ্বারা যুক্ত নদী, প্লাবনভূমি ও প্রাকৃতিক নিম্নভূমিতে (বিল ও হাওরসহ) বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। প্লাবনভূমিগুলি মাছের বিপুল সংখ্যক পোনা উৎপাদনে পুষ্টিসমৃদ্ধ নার্সারির ভূমিকা পালন করে।
বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাল খনন ও সেচ প্রকল্পের জন্য ব্যাপক পানি ও ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দেশের জলাধার ও ভূদৃশ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বন্যার বিপুল পরিমাণ পানির ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রশমন আবশ্যক ছিল। কিন্তু এটি বাংলাদেশের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও বাস্ত্তসংস্থানের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটিয়েছে। এসব কর্মকান্ড ইতোমধ্যেই মাছ ও অন্যান্য জীবসম্পদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ষাটের দশকে মোট প্লাবনভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৩ লক্ষ হেক্টর, ১৯৮৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টরে এবং ২০০৮ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৮ লক্ষ হেক্টরে। জলজ আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাছের উৎপাদনও কমে আসে। মাছের ওপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রভাব নিম্নরূপ: মাছের আবাসস্থলের ক্ষতির দরুন মাছের আহরণে ঘাটতি, প্রতি একক স্থানে মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস, মাছের ঘনত্ব/প্রাচুর্য হ্রাস, বেশি মাছ আহরণের চেষ্টা, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, পরিযায়ী মাছের সংখ্যা ও মাছের বিচরণের সংখ্যা হ্রাস, জেলেদের সম্প্রদায়গত পরিকাঠামোয় ভাঙন, রেগুলেটরসমূহে অধিক মাছ আহরণের কারণে মাছের অভিপ্রয়াণের সুযোগ হ্রাস, মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ হ্রাস ইত্যাদি।
নদী, প্লাবনভূমি, বিল এবং হাওর ছাড়াও বাওড় নামের অনেকগুলি জলাশয় রয়েছে বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যশোর ও খুলনা জেলায়। মূল নদী থেকে নদীর বাঁক বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্ট পৃথক জলাশয় বাওড়ে পরিণত হয়।
এক বিশাল জলাশয় কাপ্তাই হ্রদের আয়তন প্রায় ৬৮,৮০০ হেক্টর। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলি নদীর উপর বাঁধ দিয়ে এ হ্রদ তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে মানুষের তৈরি এটিই স্বাদুপানির বৃহত্তম জলাধার, যা মুক্ত পানিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে এই হ্রদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
এছাড়া রয়েছে প্রায় অসংখ্য পুকুর, যার মোট জলভাগের আয়তন প্রায় ৩,০৫,০২৫ হেক্টর। পুকুরগুলি ছোট (০.০১ হেক্টরের কম), মাঝারি (০.১-০.৬ হেক্টর) ও বড় (০.৬ হেক্টরের অধিক) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পুকুরগুলির অন্য শ্রেণীবিভাজন হলো: ১. মাছচাষকৃত পুকুর: যেসব পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া হয়; ২. চাষযোগ্য: যেসব পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া হয় না; এবং ৩. পরিত্যক্ত পুকুর: যেসব পুকুর মাছচাষের উপযুক্ত নয়। বিভিন্ন জেলায় শ্রেণি অনুসারে পুকুরের বিন্যাসও বিভিন্ন। জাতীয় পর্যায়ে প্রায় ৪৬% পুকুরে (পুকুরের মোট আয়তনের ৫২%) মাছচাষ হয়। বাদবাকি পুকুর মাছচাষের অনুপযুক্ত, পরিত্যক্ত বা নিম্ন উৎপাদনক্ষম। সব পুকুরই নানাভাবে ব্যবহূত হয়; ৬৩% ধোওয়া-গোসল, ২৫% মূলত মাছ ধরা, ৭% প্রধানত সেচ এবং ৫% পুকুর অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহূত হয়।
বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানা জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। দেশের উপকূল রেখা প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ। দেশের অর্থনৈতিক জলসীমা এলাকা (Exclusive Economic Zone) হিসেবে সমুদ্রসীমার আয়তন প্রায় ১,২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এদিক থেকে এলাকা বেশ বড়, তবে সীমিত সম্পদ দিয়ে এর টেকসই উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন যথার্থ অনুসন্ধান, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। বঙ্গোপসাগরে তিনটি বৃহৎ মৎস্য আহরণ অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গেছে: ১. দক্ষিণাঞ্চল (৬২০০ বর্গ কিমি) ২০৫০ উত্তর-২১৪০ উত্তর এবং ৯১ পূর্ব-৯১-এর মধ্যবর্তী; ২. মধ্যাঞ্চল (৪,৬০০ বর্গ কিমি) ২০৫০ উত্তর-২১২০ উত্তর এবং ৯০ পূর্ব-৯১-এর মধ্যবর্তী; এবং ৩. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (৩,৮০০ বর্গ কিমি) ২১ উত্তর-২১৪০ উত্তর এবং ৮৯ পূর্ব- ৯০ এর মধ্যবর্তী। এই তিনটি মৎস্য আহরণ অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল অধিক উৎপাদনশীল, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ১১.৪-১৬ মে টন, তারপরই সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড যেখানে মজুদ ১০.২-১৪.৪ মে টন এবং মধ্যাঞ্চলে মজুদ ৮.৪-১২ মে টন। দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড কক্সবাজার থেকে যথাক্রমে ১১২ কিমি ও ১৯-২৪ কিমি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে। গোটা মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলের অর্ধেক ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড-এর দুই-তৃতীয়াংশ গলাচিপার ১২৯ কিমি ব্যাসার্ধ ঘিরে রয়েছে। এতে দেখা যায় তিনটি মৎস্য অঞ্চল, অন্তত অংশত, ছোট পুঁজির জেলেদের আওতাভুক্ত, যাদের রয়েছে সাধারণত ১৫-৩৩ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন লাগানো ৯-১৫ মিটার দীর্ঘ নৌকা। বঙ্গোপসাগরে বছরে প্রায় ১,৫৭,০০০ মে টনের বেশি মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব বলে ধারণা করা যায়। [মোহাম্মদ শফি]
মাছের জীববৈচিত্র্য (Fish biodiversity) উন্মুক্ত জলাশয়ে (নদী, প্লাবনভূমি, হাওর, বিল, হ্রদ, নদীর মোহনা ও সমুদ্র) বাস করে বিভিন্ন জাতের মাছ ও চিংড়ি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানিতে প্রায় ২৬৬ প্রজাতির পাখনাযুক্ত মাছ রয়েছে। শফি ও কুদ্দুস (১৯৮২) বাংলাদেশের স্বাদুপানির ৩৬টি গোত্রের ১৪৮ প্রজাতির মাছ ও ১০ প্রজাতির Palaemonidae গোত্রের চিংড়ি শনাক্ত করেছেন, যাদের প্রায় সবগুলিই খাবারযোগ্য ও জনপ্রিয়। অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির উল্লেখযোগ্য মাছের মধ্যে রয়েছে বড় কার্প (রুই, কাতলা ও মৃগেলসহ ৬ প্রজাতি) এবং ছোট কার্প ও স্বাদুপানির ছোট মাছ (পুঁটি, চেলা, মলা ও বার্বেলযুক্ত মাছসহ ৪১ প্রজাতি), Perch (মেনি, বেলা, চেওয়া ও চান্দাসহ ৩১ প্রজাতি), Catfish (পাঙ্গাশ, বোয়াল, মাগুর, শিং, আইড়, রিটা, পাবদা ও বাচাসহ ২৯ প্রজাতি), Shad (অভ্যন্তরীণ মাছের ৪০% সরবরাহকারী ইলিশ, চাপিলা, কাঁচকি ও ফ্যাসাসহ ১০ প্রজাতি), টাকিজাতীয় (গজার, টাকি ও শোলসহ ৫ প্রজাতি), Loach (৭ প্রজাতি) ও Featherback (চিতলসহ ২ প্রজাতি)। রহমান (১৯৮৯) বাংলাদেশের স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছ তালিকাভুক্ত করেছেন। Bernascek ও তাঁর সঙ্গীরা (১৯৯২) বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩১ গোত্রভুক্ত ১৩৭ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছ শনাক্ত করেছেন। স্বাদুপানির চিংড়ির Macrobrachium গণভুক্ত অন্তত ৯টি প্রজাতি রয়েছে।
কয়েকটি বড় নদী (হালদা, পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র) বড় কার্পের ডিম, রেণু ও পোনা উৎপাদনের স্থান। পুকুরে মৎস্যচাষের চাহিদা মিটানোর জন্য এগুলি সংগ্রহ করা হয়। মৎস্যচাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের পুকুর ও হ্রদে কতকগুলি বিদেশী মাছ তেলাপিয়া (২টি প্রজাতি), চীনা সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড কার্প, ব্ল্যাক কার্প, সাধারণ কার্প (৪টি প্রজাতি), থাই পুঁটি, থাই পাঙ্গাশ, আফ্রিকার মাগুর ইত্যাদিরও চাষ প্রবর্তন করা হয়েছে।
হুসেইন (১৯৬৯) বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদীমোহনার পানিতে ১৩৩ গোত্রের ৪৭৫ প্রজাতির মাছ তালিকাভুক্ত করেছেন। কুদ্দুস ও শফি (১৯৮৩) কর্তৃক সমুদ্র ও স্বল্পলোনাপানি থেকে শনাক্তকৃত ১৬৯ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৫৯ গোত্রভুক্ত ১৪৮ প্রজাতির মাছ অস্থিময় ও ১০ গোত্রভুক্ত ২১ প্রজাতির মাছ কোমলাস্থিবিশিষ্ট। এদের মধ্যে বেশির ভাগই সামুদ্রিক Perch-জাতীয় (৩০ গোত্রের ৬৩ প্রজাতি) মাছ। এরপর রয়েছে Herring ও Shad (৩ গোত্রভুক্ত ২১ প্রজাতি), Catfish (৩ গোত্রভুক্ত ১৯ প্রজাতি) ও Flatfish (৫ গোত্রভুক্ত ১৬ প্রজাতি)। সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের শতকরা ৬০ ভাগ হলো ইলিশ। বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় রয়েছে ১০ প্রজাতির হাঙ্গর। সামুদ্রিক মাছের প্রায় ৬৫% বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
সামুদ্রিক চিংড়ির ১৭ প্রজাতির মধ্যে Penaeus গণের ৬, Metapenaeus-এর ৫, Parapenaeopsis-এর ৪ এবং Solenocera-এর ২টি প্রজাতি রয়েছে। অবশ্য, মাত্র ৫ প্রজাতির চিংড়ি যেমন, Penaeus monodon, Penaeus semisulcatus, Penaeus indicus, Metapenaeus monoceros এবং Metapenaeus brevicornis বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে ৫ প্রজাতির লবস্টারের (crustacean) মধ্যে সাধারণত কেবল ২ প্রজাতিই ('Panulirus polyphagus, Scyllarus nearctus) সহজলভ্য। [মোহাম্মদ শফি]
মৎস্য সমবায় (Fisheries co-operatives) কর্মরত মৎস্যজীবীদের একটি সংগঠন, যেখানে তারা অধিকতর কার্যকর মৎস্য আহরণ ও অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা লাভের জন্য সম্পদ লগ্নি করে। মৎস্যজীবীদের জন্য মাছ ক্রয় ও বিক্রয় বা মাছ ধরার সরঞ্জাম বীমাকরণ ইত্যাদি সমবায়ের কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। জাপান, নরওয়ে ও অন্যান্য দেশের মৎস্যজীবীরা হাজার হাজার সফল সমবায়ের আওতাভুক্ত, আর সেসব দেশে ঋণ-সুবিধা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সমবায়ের দায়িত্ব। বাংলাদেশে এই ব্যবসায় অধিকাংশ মৎস্যজীবী মধ্যগদের দ্বারা শোষিত হয়। মধ্যগরা মৎস্যজীবীদের নগদ টাকা দাদন দেয় বলে কখনও মাছ না ধরলে, অমৌসুমে অথবা মাছ কম ধরা পড়লে তারা দালালদের কবল থেকে রেহাই পায় না। এসব ক্ষেত্রে মৎস্য সমবায় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষা করতে পারে, দালালদের শোষণ থেকে তাদের বাঁচাতে পারে ও মাছের ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা দিতে পারে।
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলায় মৎস্যজীবীদের ১২০টি সমবায় ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজীবীদের সমবায়ের সূচনা হয় ১৯৬০ সালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। সাবেক প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি’ রাখা হয়। সমিতির লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে: ১. মাছ ধরার সরঞ্জাম সংগ্রহ ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে সেগুলি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা; ২. সদস্যদের অর্থযোগানের জন্য অধিভুক্ত সমিতিগুলিকে ঋণদান; ৩. মাছ ধরার আধুনিক কলাকৌশল প্রবর্তন; ৪. বরফ কারখানা স্থাপন, হিমাগার নির্মাণ, জাল তৈরির যন্ত্রপাতি বসানো ইত্যাদি; ৫. মাছ বাজারজাত করার ব্যবস্থা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন এবং ৬. মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
বাংলাদেশে জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রথাগত পিরামিডের মতো প্রাথমিক (নিচে), মধ্য ও শীর্ষ (উপরে) এই তিন স্তরবিশিষ্ট। জাতীয় সমিতি একটি (শীর্ষ), মাধ্যমিক সমিতির সংখ্যা প্রায় ৮০ ও প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। সরকার কর্তৃক ১৯৮৬ সালে নতুন উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের পর অভ্যন্তরীণ খাতে ‘বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি’ গঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রথম নাইলন সুতার জালসহ মাছ ধরার যন্ত্রচালিত নৌকা প্রবর্তন করে। অতঃপর ‘বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন’ ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির প্রসার ঘটে।
বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের মৎস্য ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, কারিতাস, প্রশিকা ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থা জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সরাসরি জড়িত রয়েছে। মহিলারা চিরাচরিত জালবোনা, জাল মেরামত, জাল শুকানো ও মাছ শুকানো ছাড়াও বর্তমানে অধিক সংখ্যায় মৎস্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছে। [মোহাম্মদ শফি]
মৎস্যখামার ব্যবস্থাপনা (Fish-farm management) মৎস্যচাষে জলাশয়গুলিতে অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য গৃহীত সামগ্রিক ব্যবস্থাদি। এই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো যথাযথ ব্যবস্থাপনা দক্ষতায় সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে জলাশয়ের সীমিত পরিসরে মৎস্য খাদ্য ও যত্নের জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক পরিমাণ মৎস্যখাদ্যের রূপান্তর হার (feed conversion ratio/FCR) ও মুনাফা অর্জন। ব্যবস্থাপনার অন্যান্য দিকের মধ্যে রয়েছে পানির সবচেয়ে অনুকূল ভৌত রাসায়নিক ও পরিবেশগত অবস্থা অব্যাহত রাখা, পর্যাপ্ত আলো, বায়ু চলাচল ও রোগমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং পানির তলদেশের মাটির উর্বরতা সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক প্লাবন প্রতিরোধ।
বাংলাদেশে মৎস্যখামারের মধ্যে রয়েছে প্রধানত নার্সারি, পোনাবর্ধন ও মাছ মজুদে ব্যবহার্য নানা আকার আয়তনের পুকুর। নার্সারি পুকুরগুলি সাধারণত ০.১ একরের কম আয়তনের, আয়তাকার ও ০.৭৫-১ মিটার গভীর। পোনাবর্ধন পুকুরগুলি ০.১১-০.৬৬ একর, আয়তাকার ও ১-১.৫ মিটার গভীর। মজুদের পুকুরগুলিও আয়তাকার, ০.৬৭- ১.৫ একর ও ১.৫-২ মিটার গভীর।
পোনা মজুদ স্থানান্তরিত মাছের পোনাগুলিকে ১০-২০ মিনিট নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত করে এক-পর্যায় ব্যবস্থাপনায় ৬-৮ গ্রাম/ডেসিমাল, আর দুই-পর্যায় ব্যবস্থাপনায় ১৫-২০ গ্রাম/ডেসিমাল হিসেবে পুকুরে ছাড়া যেতে পারে। ব্যবস্থাপনার চাহিদানুযায়ী মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার পরীক্ষা, ব্যায়াম, খাদ্যের মূল্যায়ন, পুকুরের তলা রেকিং ও অন্যান্য পরিবর্তনের জন্য প্রতি দুই সপ্তাহে একবার পোনা জালে ধরা যেতে পারে।
মাছের স্বাভাবিক খাদ্য হিসেবে প্লাঙ্কটনের অবিরাম বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন সামান্য মাত্রায় সার (১৫ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম টিএসপি/ডেসিমাল) প্রয়োগসহ পানি নাড়াচাড়া করা দরকার। সকাল ও দুপুরের খাবারের জন্য সমপরিমাণ ভিজা খৈল ও গম বা চালের ভুসি পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি ছড়ানো প্রয়োজন। মাছ না তোলা পর্যন্ত মেঘলা ও বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রত্যহ এভাবে খাবার দিতে হবে।
মৎস আহরণ আগাম (মার্চ-জুন) মৎস্যচাষের জন্য এক-পর্যায় চাষে ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে এবং দুই-পর্যায় চাষে পোনা ছাড়ার ২ সপ্তাহ পরে মাছের সংখ্যা কমাতে হয়। ব্যতিক্রম ঘটে বিলম্ব (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে।
পালনের পুকুর এ ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়, তবে মাছের ঘনত্ব রাখা হয় ১০০০ পোনা/ডেসিমাল এবং হ্রাসকৃত খাদ্যহার (দেহের ওজনের ৫%) দিনে একবার।
মজুদের পুকুর মজুদের আগে ৩০০ ppm KMnO4 দ্রবণে ২-৩ মিনিট মাছের পোনার নির্বীজন আবশ্যক।
পুকুরের আয়তন, ভূসংস্থান, পুকুর পাড়ের গাছগাছড়া, তলার মাটির ধরন ও পুকুরের সর্বমোট উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুদের পরিমাণ লাগসই হওয়া উচিত। স্বাভাবিক খাদ্য বা সম্পূরক খাদ্য সাপেক্ষে বাংলাদেশের পুকুরে প্রতিপালনের জন্য মৎস্যবিজ্ঞানীরা মৎস্য মজুদের নিম্নোক্ত সংমিশ্রণ অনুমোদন করেন। [মোঃ সানাউল্লাহ]
মাছের পরজীবী ও রোগবালাই (Fish parasites and diseases) মাছের পরজীবী মাছের শরীরের উপরে বা ভিতরে বসবাসকারী এবং পোষক মাছ থেকে খাদ্যগ্রহণকারী জলজ জীব। এগুলি বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ এবং রোগ সৃষ্টিকারী (pathogenic) বা রোগ সৃষ্টি করে না এমন (non-pathogenic) হতে পারে। পুকুর, জলা ও অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো কৃত্রিম জলাশয়ে মাছচাষ করলে মাছের পরজীবিজনিত রোগের অধিক প্রকোপ ঘটে। কোন কৃত্রিম পরিবেশে এক বা একাধিক প্রজাতির মাছের অত্যধিক ঘনত্বের চাপই পরজীবীদের অধিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ, যা প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে ততটা দেখা যায় না। সেজন্য পরজীবিঘটিত রোগের প্রকোপ প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মাছের তুলনায় কৃত্রিমভাবে চাষকৃত মাছে অধিক।
পরজীবী সংক্রমণ থেকে পোনামাছের মৃত্যু ও বাড়ন্ত মাছের পুষ্টিঘাটতির ফলে মাছ উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পায়। পরজীবীরা বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রতঙ্গসহ মাছের প্রায় সবগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আক্রমণ করতে পারে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মাছের ১৩০ প্রজাতির পরজীবী শনাক্ত করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় ও গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি নিম্নরূপ:
প্রটোজোয়া পরজীবী Ichthyobodo necatrix, Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella cyprini, Trichodina species, Epistylis species, Zoothamnium species, Myxobolus cyprini, M. mrigala, Mitraspora cyprini ইত্যাদি।
বহুকোষী (Metazoan) পরজীবী ১. Trematodes: Dactylogyrus glossogobii, D. vastator, Gyrodactylus species, Neobucephalopsis species, Phyllodistomum species, Posthodiplostamum cuticola, P. minimum, Clinostomum complanatum, Opegaster species, Neopecoelina species, Genarchopsis species, Pleurogenes species, Isoparorchis hypselobergi; ২. Cestodes: Ligula intestinalis, Bothriocephalus opsarichthydis এবং Caryophyllids (Lytocestus species, Bovienia serialis, Djombangia penetrans, Pseudocaryophyllaeus species); ৩. নিমাটোড: অ্যাসকারিডীয় লার্ভা, Camallanus species, Zeylanema species, Spirocamallanus species, Procamallanus species, Gnathostoma spinigerum; ৪. Acanthocephalans: Neoechinorhynchus species, Acanthogyrus acanthogyrus, Acanthosentis species, Pallisentis species, Heterosentis species; ৫. ক্রাসটেসিয়ান (Crustacean) পরজীবী: Ergasilus species, Lernaea cyprinacea, Argulus species, Bopyrus species ইত্যাদি; ৬. জোঁক: Piscicola geometra।
বাংলাদেশে প্রবর্তিত বিদেশী মাছের নিম্নে উল্লিখিত ১৪টি পরজীবীর কথা জানা যায়: Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina reticulata, Chilodonella cyprini, Balantidium ctenopharynogdonis, Eimeria sinensis, Myxobolus pavlovoski, Trichophrya sinensis, Dactylogyrus extensus, D. vastator, Gyrodactylus cyprini, Bothriocephalus opsarichthydis, Camallanus cotti, Argulus foliaceus, এবং Lernaea cyprinacea।
মাছের রোগ সাধারণ প্রটোজোয়াঘটিত রোগের মধ্যে রয়েছে ১. Ichthyobodiasis ফ্লাজেলাযুক্ত Ichthyobodo (=Costia) necatrix পোনা ও অল্পবয়সী মাছের ত্বক ও ফুলকা আক্রমণ করে; পুকুর নির্বীজন (disinfection), যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সমবয়সী মাছ চাষের মাধ্যমে রোগনিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ২. Ichthyophthiriasis– ‘Ich’ বা সাদা দাগ রোগ দেখা দেয় Ichthyophthirius multifiliis সংক্রমণে। এটি অ্যাকুয়ারিয়াম ও চাষ করা মাছেই বেশি; সাদা দাগ দেখা দেয় ত্বক, পাখনা ও ফুলকায়। ৩. Chilodonelliasis এতে Chilodonella cyprini জীবাণু ত্বক, পাখনা ও ফুলকা আক্রমণ করে, ফলে অত্যধিক মিউকাস ক্ষরণের ফলে মাছের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

৪. Trichodiniasis– Trichodina species ত্বক, পাখনা ও ফুলকা আক্রমণ করে এবং ফুলকার মারাত্মক ক্ষতির জন্য ব্যাপক হারে পোনা ও অল্পবয়সী মাছ মারা যায়। ৫. Myxosporidiasis– Myxosporidia-র বিভিন্ন গণের (Myxobolus, Henneguya, Myxosoma, ইত্যাদি) প্রজাতি ফুলকা, ত্বক, বৃক্ক, মাংসপেশী ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে। পলিস্পোরোব্লাস্ট সাদা সাদা সিস্ট গড়ে তোলে।
সাধারণ বহুকোষী পরজীবীয় রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Dactylogyriasis ফুলকার কৃমি (Dactylogyrus species) কর্তৃক ফুলকার মারাত্মক ক্ষতির কারণে ব্যাপক সংখ্যায় পোনা ও কমবয়সী মাছ মারা যায়। Gyrodactyliasis/‘Gyros’– Gyrodactylus প্রজাতির ফিতাকৃমি ত্বক ও ফুলকায় ক্ষত সৃষ্টি করে। চিকিৎসা ফুলকার কৃমির অনুরূপ। Diplostomiasis/কালোদাগ রোগ- Posthodiplostomum cuticola ঘটিত ত্বকের কালো দাগ। শামুক (Limnea) ও বক যথাক্রমে মাধ্যমিক ও শেষ বাহক। Clinostomiasis/হলুদ কীড়ারোগ- Clinostomum complanatum- জীবাণুর লার্ভাঘটিত; ত্বক, পাখনা ও ফুলকা থেকে হূৎপিন্ড ও মাংসপেশীতে ছড়ায় এবং হলুদ বা ঘি রঙের সিস্ট তৈরি করে। Ligulosis– Ligula inestinalis নামের ফিতাকৃমি (১০-১০০ সেমি লম্বা ও ০.৬-১.২ সেমি চওড়া) অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উদরের প্রদাহ ঘটায়। Caryophyllidiasis– ক্যাটফিসের অন্ত্রে অবস্থানকারী Lytocestus indicus, L. parvulus, Bovienia serialis, Djombangia penetrans ঘটিত রোগ। Piscicolasis– Piscicola geometra জোঁকের আক্রমণঘটিত রোগ; সাধারণত প্রাকৃতিক জলাশয়ের মাছে থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই চাষকৃত মাছেও দেখা যায়; ত্বক, পাখনা, ফুলকা, মুখ ও চোখ আক্রমণ করে। Ergasiliasis– Ergasilus species ঘটিত কার্প ও ক্যাটফিসের ফুলকার রোগ, ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে পুকুরে Neguvon বা Dipterex (০.২৫-০.৫ ppm) প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা যায়। Lernaeasis/অ্যাঙ্করওয়ার্ম সংক্রমণ- Lernaea cyprinacea ঘটিত রোগ। স্ত্রী লার্ভা মাছের শরীরে গর্ত করে ঢোকে এবং বাইরে কাঁটা বা কুর্চের মতো বেরিয়ে থাকে, প্রায়শ দেহের গভীরে পৌঁছে অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করে। Argulosis/মাছের উকুনরোগ- পরজীবী Argulus species শুঁড় দিয়ে চামড়া ফুটো করে মাছের রক্ত চুষে খায়; ত্বক, পাখনা ও ফুলকা আক্রমণ করে এবং বিষ ঢুকিয়ে মাছের মৃত্যু ঘটায়।
অ-পরজীবী মৎস্যরোগ মাছ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বিধায় সহজেই, বিশেষত জটিল কৃত্রিম পরিবেশগত পরিস্থিতিতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাছ ও রোগজীবাণুর মধ্যেকার ভারসাম্যগত অবস্থা ভেঙে গিয়ে রোগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলে, প্রধানত পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে রোগ দেখা দেয়।
মৎস্যরোগের বাহ্যিক ও আচরণগত লক্ষণ হলো: দেহবর্ণের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস ও রঞ্জককণার পরিবর্তন, নিশ্চল বা অস্থির সাঁতার, ভারসাম্যহীনতা, দলবদ্ধতা ও পানির উপর ভেসে ওঠা, অস্বাভাবিক ঢোক গেলা; দেহের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা কৃশতা, রক্তশূন্যতা, অক্ষিস্ফীতি, হূৎপিন্ডস্ফীতি, ত্বকে ক্ষত, পাখনা ও ত্বক ক্ষয়, স্ফীত অাঁশ, অত্যধিক মিউকাস নিঃসরণ, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ লক্ষণের মধ্যে আছে দেহগহবরে ঈষৎস্বচ্ছ তরল জমা হওয়া, দেহগহবরের স্ফীতি বা সঙ্কোচন, গভীর ক্ষত, অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্তক্ষরণের চিহ্ন বা সিস্ট।
মৎস্যরোগের মূলে রয়েছে পানির গুণমানের অবনতি, অধিক মাছ মজুদ ও অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি। পানিদূষণ, পুকুর ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ইত্যাদিও মাছে রোগ উৎপাদনের সহায়ক।
পরজীবী ছাড়াও মৎস্যরোগের অন্যান্য কারণ রোগজীবাণু, পরিবেশের অবক্ষয়, পুষ্টির অভাব ও বংশানুসৃত ত্রুটি। বাংলাদেশে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ অ-পরজীবী মৎস্যরোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১. ভাইরাসঘটিত রোগ- বাংলাদেশে এই ধরনের কোন রোগ এখনও নেই। ২. ব্যাক্টেরিয়াঘটিত রোগ- Columnaris রোগ- রোগের জীবাণু Flexibacter columnaris; স্বাদুপানির প্রায় সকল প্রজাতির মাছের ত্বক, পাখনা ও ফুলকাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করে, ফলে ক্ষত ও রক্তক্ষরণ ঘটে। অক্সিজেনের ঘাটতি ও জমাকৃত বিপাকীয় বর্জ্যই এ রোগের প্রধান কারণ। রক্তক্ষরাজনিত সেপ্টিসেমিয়া (শোথ)- Aeromonas hydrophila ও Pseudomonas florsescence আক্রমণে শরীরে ক্ষত, রক্তক্ষরণ এবং অন্ত্র, লিভার, প্লীহা ও বৃক্কে অস্বচ্ছ তরল সঞ্চয়সহ উদরস্ফীতি দেখা দেয়। অাঁশ ফেঁপে ওঠা (scale protrusion) রোগের মূলে রয়েছে Pseudomonas ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ। এই রোগে অাঁশগুলি ফুলে উঠে ফাঁক ফাঁক হয়ে যায় এবং অাঁশের মাঝখানে নির্গত তরল জমা হয়। ব্যাক্টেরিয়াঘটিত ফুলকাপচা রোগ Myxobacteria জীবাণুর দ্বারা ঘটে এবং সাধারণত অল্পবয়সী কার্প মাছের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। ফুলকার পচন এবং শ্বাসকষ্ট থেকে মাছ মারা যায়। পুকুরে চুন প্রয়োগে এ রোগের প্রকোপ কমে। ৩. ছত্রাকরোগ- Saprolegniasis রোগ দেখা দেয় Saprolegnia প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে। এতে স্বাদুপানির মাছ, ডিম ও পোনা ব্যাপক হারে আক্রান্ত হয়। এ রোগে ত্বকের প্রদাহ থেকে মাংসপেশীর পচন ঘটে; Branchiomycosis রোগ দেখা দেয় Branchiomyces-এর কয়েক প্রজাতির আক্রমণে। এতে ছত্রাকের অণুসূত্রে রক্তনালীগুলি আবদ্ধ হয়ে ফুলকায় ক্ষত দেখা দিলে রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, ফলে মাছের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
অপুষ্টিজনিত রোগ মাছের অপুষ্টিজনিত রোগের মধ্যে ভিটামিন ‘সি’-র অভাবজনিত রোগ পুকুরের কার্প ও ক্যাটফিশের মধ্যে সাধারণত দেখা যায়। মাছ প্রধানত মূল খাদ্যের সঙ্গে জলজ আগাছা ও শৈবাল থেকে ভিটামিন সি পেয়ে থাকে, কিন্তু নিবিড় চাষে তাদের মধ্যে মেরুদন্ডবক্রতা (Lordosis/Scoliosis) দেখা দেয়। এ রোগে কার্প ও ক্যাটফিশ বেশি আক্রান্ত হয় এবং তাদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, দেহবিকৃতি ঘটে। অধিকন্তু করোটির অস্থিগঠন ব্যাহত হওয়ার দরুন ‘মাথাভাঙ্গা’ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। রোগের সংক্রমণে মাছের থুতনির নিচ থেকে রক্তক্ষরণ হয়, যা আফ্রিকান মাগুরে বেশি দেখা যায়।
পরিবেশগত রোগ পরিবেশগত অবক্ষয়ের দরুন ব্যাপক হারে মাছ মারা যেতে পারে এবং মাছের বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। তন্মধ্যে অত্যধিক অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন সম্পৃক্ততার কারণে সৃষ্ট গ্যাস-বুদ্বুদ রোগ অনেক মাছে লক্ষ্য করা যায়। এ রোগে পোনার কুসুমথলি, চোখের অধঃত্বক, ফুলকা ও পটকায় এবং পূর্ণবয়স্ক মাছের দেহগহবরে গ্যাস-বুদ্বুদ দেখা যায়। আক্রান্ত মাছে রং গাঢ়, চলাচলে ভারসাম্যহীনতা এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা যায়।
ত্বকের ক্ষতজনিত সিনড্রোম (Epizootic Ulcerative Syndrome/EUS) প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাশয়ের বিভিন্ন ধরনের মাছের একটি সংক্রামক রোগ। এতে শরীরে গভীর ক্ষত দেখা দেয় ও মাছ মারা যায়। এ রোগ স্বাদুপানি ও মোহনার মাছের মৌসুমি পরজীবী Aphanomyces-এর সংক্রমণ থেকে দেখা দেয়। প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যায় পানির ক্ষারত্ব, ক্লোরাইড ও লবণাক্ততা হঠাৎ হ্রাস পেলে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কমে গেলে এ রোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশে রোগটি ১৯৮৮ সালে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রথম দেখা দেয়। এটি এখনও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে মাছের ব্যাপক মৃত্যুজনিত কারণে মৎস্য সম্পদের অবনতি ঘটে। রোগাক্রান্ত মাছ বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়ে।
সর্বাধিক রোগপ্রবণ হলো নিম্নস্তরে বসবাসকারী মাংসাশী বিভিন্ন মাছ। এর পরে রোগপ্রবণ হচ্ছে মধ্যস্তরের প্রজাতিগুলি। বাতাস থেকে শ্বাসগ্রহণকারী অনেক জাতের মাছ যেমন, টাকি (Channa punctatus), শোল (C. striatus), কই (Anabas testudineus), মাগুর (Clarias batrachus) এবং শিঙ্গি (Heteropneustes fossilis) কমবেশি সমভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়। সর্বাধিক আক্রমণ ঘটতে দেখা গেছে শোল-টাকি প্রজাতিতে (৩০%), তারপর যথাক্রমে পুঁটি প্রজাতিগুলি (Puntius species), মেনি (Nandus nandus), ও কুচিয়া (Monopterus cuchia)- যারা নিচুস্তরের কদমাক্ত পরিবেশে বাস করে। টাকি-শোল মারাত্মক ক্ষত নিয়েও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে। তবে অন্য প্রজাতিগুলি দ্রুত মারা যায়। [আবু তৈয়ব আবু আহমেদ এবং মোঃ সানাউল্লাহ]
মৎস্য বিপণন (Fish marketing) মৎস্য অথবা মৎস্যজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড। উৎপাদক, মধ্যম, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা এবং ভোক্তার সমন্বয়ে মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিপণন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাইকারিভাবে ভোক্তাদের গ্রহণযোগ্য মূল্যে সরবরাহ করা গেলেই মৎস্য আহরণ ও বিপণন লাভজনক হয়।
মৎস্য বিপণন প্রায় পুরোটাই সম্পন্ন হয় ব্যক্তিগত খাতে। গ্রামীণ বাজার (হাট), শহরের মার্কেট (বাজার), জনসমাগমস্থল, শহুরে পাইকারি ও খুচরা বাজারগুলির এক জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে এ বিপণন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে মাছ নামানোর ঘাটগুলিতে ক্রেতাদের প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার যোগান দেওয়া। অনেক সময় মৎস্যজীবীরা ব্যবসায়ী/দালালদের (আড়তদার/পাইকার) নির্ধারিত দামেই তাদের কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মধ্যগ কেবল মাছ ব্যবসায়ী নয়, সে নিজেও মৎস্যজীবী হতে পারে এবং হতে পারে নৌকা, জাল ইত্যাদির মতো পুঁজির মালিক, যা সে মৎস্যজীবীদের ইজারা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সে এগুলি চালাতে নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে জেলেদের মাছ ধরার শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগায় এবং ন্যায্য পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করে।
বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাছ বিপণন ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর এবং গুণগত মানের খুব বেশি অবনতি না ঘটিয়েই প্রয়োজনমতো বাজারকেন্দ্রগুলিতে যথাসময়ে মাছের চালান পৌঁছায়। মৎস্যজীবীদের নিকট থেকে মাছ সংগ্রহে নৌকা ব্যবহূত হয়। বরফসহ মোড়কবদ্ধ মাছ ট্রাক ও বাসে করে বড় বড় শহরে পৌঁছায়।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন চট্টগ্রামে আধুনিক মৎস্য পোতাশ্রয় এবং কক্সবাজার, বরিশাল, খেপুপাড়া, পাথরঘাটা ও খুলনায় সামুদ্রিক মাছের, আর রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, রাজশাহী ও ডাবরে স্বাদুপানির মাছের অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। পোতাশ্রয় ও সকল অবতরণ কেন্দ্রে নোঙর বাঁধা, নিলাম ডাকা, বরফকল, হিমাগার, ফ্রিজার ও মৎস্যবাহী ভ্যান ইত্যাদির ব্যবস্থাসহ আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রয়েছে। তবে অনেক সময় মাছ ব্যবসায়ীরা অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার কারণে এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে কম আগ্রহী। [মোহাম্মদ শফি]
মৎস্য প্রশাসন (Fisheries administration) বাংলাদেশে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বলতে সরকারের রাজস্ব (কর) অর্জনের উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন নদ-নদী বা তাদের অংশবিশেষ, বিল, বাওড় ও অন্যান্য জলাশয় ইজারা প্রদান বোঝায়। ১৭৯৩ সালে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন-১ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই এ ধরনের ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয়। এই আইনের অধীনে বিশাল এলাকা ভূস্বামীদের (জমিদার) স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। শুধু জমিই নয়, বড় বড় নদ-নদীর অংশ, তাদের শাখা-প্রশাখা এবং প্লাবনভূমিও এই ধরনের জমিদারি বা ভূসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্লাবনভূমির মধ্যে ছিল গভীর খাদ, যেগুলি ‘বিল’, ‘বাওড়’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্র মৎস্য ব্যবস্থাপনা বলতে জলভাগের জীবন্ত সম্পদের এমন ব্যবস্থাপনা বোঝায়, যাতে বছরের পর বছর একটি পূর্বনির্ধারিত মাত্রায় আহরণের পরও তা স্থায়িভাবে টিকে থাকে।
কোন জমিদারির সীমানাভুক্ত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ইত্যাদি বড় নদ-নদীর অংশ বা অংশসমূহ অথবা তাদের শাখা-প্রশাখার অংশ এবং বিল বা হাওর সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এধরনের নদ-নদীর অংশবিশেষ, বিল বা হাওরকে জলমহাল বা জলকর (জল তালুক) বলা হতো। ভূস্বামীরা সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্য এসব জলমহাল ইজারা দিত। নদীর জলমহাল এক বছর এবং বিল ও হাওর তিন বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হতো। বর্তমানে জলমহালের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০, যার মধ্যে রয়েছে সাবেক জমিদারদের বাড়ির দিঘি ও পুকুর।
সরকারের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পূর্ব বাংলার (পরে পূর্ব পাকিস্তান) সাবেক সরকার ১৯৫০ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের (East Bengal Act, III of 1951) মাধ্যমে জমিদারদের দেয় খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। এভাবে সাবেক প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ জমিদারদের বসতবাড়ির দিঘি ও পুকুরসহ সকল জলমহালের মালিক হয়। সাবেক প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ (ভূমি মন্ত্রণালয়) জমিদারদের অনুসৃত জলমহাল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বজায় রাখে। পরিবর্তন শুধু একটিই, রাজস্ব বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বোর্ড জেলা কালেক্টরদের (বর্তমান পদবি ডেপুটি কমিশনার) মাধ্যমে জেলার জলমহাল ইজারা দেওয়া হতো। প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাকদাতা জলমহাল ইজারা পেতো। নদ-নদী জলমহাল এক বছর (এক বাংলা সন) আর বিল, বাওড়, বড় পুকুর/জলাশয় সচরাচর তিন বছরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। ইজারাদার জলমহালকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত এবং মৎস্যসম্পদ আহরণ করত। বর্তমানে ভূমিমন্ত্রণালয় (ভূতপূর্ব ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়) জলমহাল (জল-তালুক) ইজারা দিয়ে থাকে। উপজেলা পরিষদকে ২০ একর পর্যন্ত আয়তনের বদ্ধপুকুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই শর্তে যে, উপজেলা পরিষদ এই ধরনের জলমহাল থেকে অর্জিত আয়ের ১% ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করবে। বিশ একরের বড় বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৯৫ সালে নদ-নদী জলমহালের ইজারা ব্যবস্থা বিলোপ করে।
নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় ১৯৮৬ সালের গোড়ার দিকে ‘মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি’ (Fishing Management Policy) নামে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন ধারণার সূচনা করেছে। এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. জলমহাল থেকে আহরিত মাছের সর্বোচ্চ লাভ মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের পরিবর্তে প্রকৃত জেলে ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন এবং ২. মৎস্যসম্পদ অটুট রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে কিছু নির্বাচিত জলমহালের দখল নিতে চায় এ শর্তে যে, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রত্যেক মেয়াদে প্রচলিত ১০% বাড়তি হারে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জলমহালের কর পরিশোধ করবে। নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হয়: ১. জলমহাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জামের (মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য উপকরণ) আকার ও ক্ষমতা এবং মাছ ধরার ইউনিটে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে লাইসেন্স ফি’র বিনিময়ে জলমহালে মাছ ধরার নবায়নযোগ্য লাইসেন্স দেওয়া হবে। ২. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও জাতীয় মৎস্যজীবী সংস্থার প্রতিনিধি কর্তৃক একত্রে মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরি করা হবে। জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তালিকাভুক্ত মৎস্যজীবী ও মাছ ধরার ইউনিটকে নবায়নযোগ্য লাইসেন্স প্রদান করবেন। প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করবে।
কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সূচিত প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের বাস্ত্তসংস্থানিকভাবে পরিপোষণমূলক (ecologically sustainable) ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলির মাছ ধরা থেকে সংগৃহীত লাভের আরও ন্যায়সঙ্গত বিতরণে মদদ যোগানো। সাধারণত মৎস্য অধিদপ্তর বড় বড় এনজিও-র সঙ্গে একযোগে কাজ করে। অংশীদার এনজিওসমূহের দায়িত্ব: ১. মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা ও জোরদার করা এবং সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া এবং ২. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য উপার্জনের বিকল্প উৎসসহ তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। বর্তমানে কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার অধীনে ২০টি জলাশয় রয়েছে।
অন্যান্য মালিক কর্তৃক মৎস্য ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কয়েকটি সরকারি সংস্থার নিজস্ব জলাশয় রয়েছে। এসব সংস্থার মধ্যে বন বিভাগ সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরের বড় ও ছোট নদী, খাল ও ফাঁড়ির মালিকানায় রয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে চলাচলকারী মাছ ধরার নৌকা ও মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে টোল, খাজনা ও কর আদায়ের মধ্যে বন অধিদপ্তরের মৎস্য ব্যবস্থাপনা সীমিত। মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের নৌকার লাইসেন্স, সার্টিফিকেট ফি, শুষ্ক জ্বালানি ব্যয় ও তাদের নৌকার নানা ধরনের মাছ, চিংড়ি ও শুঁটকির জন্য বিভিন্ন হারে কর দিতে হয়। এভাবে বন অধিদপ্তর মাছ ধরা ও মাছ পরিবহণ বাবদ বেশ ভাল অঙ্কের রাজস্ব আয় করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর খাল ও খাদের মতো জলাশয় খনন করে। এসব সংস্থা এই জলাশয়গুলিকে প্রধানত মাছ চাষের জন্য প্রকাশ্য নিলামে ইজারা দেয়। প্রচলিত মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বাংলাদেশে এখনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করা হয়নি। [এম ইউসুফ আলী]
মৎস্য আইন (Fish laws) ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন মৎস্য অধিদপ্তর শুধু মাছ বাজারজাতকরণ ও মৎস্যজীবীদের কল্যাণ সাধনের বিষয়গুলি তদারক করত। এরপর থেকে অধিদপ্তর অন্যান্য বিষয়, যেমন মৎস্য সংরক্ষণ, মাছ ধরার সময়কাল নিয়ন্ত্রণ, জালের ফাঁসের আকার নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে শুরু করে এবং বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে, যা মৎস্যখাতের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।
বিশেষ বিশেষ মৎস্যপ্রজাতির পোনা ও রেণু সংরক্ষণ এবং কতিপয় মাছ শিকার কার্যক্রম সীমিত করার জন্য ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক আইন সভায় পূর্ব বাংলা মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন (East Bengal Protection and Conservation of Fish Act) পাস করা হয়। আজ পর্যন্ত বলবৎ এই আইনে মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করণে আইন ও প্রবিধান প্রণয়নে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৩, ১৯৭০, ১৯৮২ ও ১৯৮৫-১৯৮৮ সালে এ আইনের বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। এই আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: মাছ বলতে কোমলাস্থি ও অস্থিবিশিষ্ট মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য খাবার উপযোগী ক্রাসটেসিয়ান, উভচর, কচ্ছপ ও কাউঠা/কাছিম, শামুক-ঝিনুক, কন্টকত্বকী (echinoderms) ইত্যাদি বোঝাবে; নদী, খাল ও বিলের বহির্মুখী নালা বরাবর মাছ ধরার সরঞ্জাম (জাল, খাঁচা, ফাঁদ ইত্যাদি) বসিয়ে মাছ শিকার নিষিদ্ধ। এই ধরনের পেতে রাখা সরঞ্জাম অপসারণ বা বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে; বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যতীত পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী অন্য যে কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী ঘের, জলাধার, বাঁধ, বেড়িবাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ; অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় জলভাগে বিস্ফোরক, বন্দুক, ধনুক ও তীর দিয়ে মাছ শিকার নিষিদ্ধ; কারখানার বর্জ্যে বা অন্যভাবে পানি বিষাক্ত বা দূষিত করে মাছ মারা নিষিদ্ধ; মাছ চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নদী, খাল ও বিলের শোল, গজার ও টাকি মাছ বা সেগুলির পোনা ধরা নিষিদ্ধ; জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্ধারিত মাসুল দিয়ে লাইসেন্স পাওয়ার পর নির্বাচিত ২৭টি নদী ও খাল থেকে মাছ চাষের উদ্দেশ্যে যে কোন আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ ও ঘনিয়া ধরা যেতে পারে; মাছ চাষের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ প্রতিবছর জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ সেমির কম দৈর্ঘ্যের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ ও ঘনিয়া, নভেম্বর-এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা (ছোট ইলিশ) ও পাঙ্গাশ এবং ফেব্রুয়ারি-জুন পর্যন্ত ৩০ সেমি’র কম দৈর্ঘ্যের শিলং ও আইড় ধরা নিষিদ্ধ; ৪.৫ সেমির কম ফাঁসবিশিষ্ট কারেন্ট জাল/মশারি দিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ; প্রথমবার আইনভঙ্গকারী ৬ মাসের জেল বা ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা একই সঙ্গে উভয় দন্ড ভোগ করবে; দ্বিতীয়বার আইন ভঙ্গকারী এক বছরের জেল বা ১,০০০ টাকা জরিমানা বা একই সঙ্গে উভয় দন্ড ভোগ করবে; গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই আইন ভঙ্গকারীকে গ্রেফতার করা যাবে; বিধিটি প্রয়োগের জন্য সরকার সকল ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা পর্যায়ের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, সুন্দরবনের বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জার ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদান করছে; বিধির অধীনে গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দেওয়া হয় না।
সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (The Marine Fisheries Ordinance 1983) অধ্যাদেশটি সাধারণত সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৩ নামে পরিচিত, যা ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়েছে। আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এরূপ– চট্টগ্রামে কর্মরত একজন পরিচালক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রয়োগ ও লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন; প্রতিটি মাছ ধরার ট্রলার ও যন্ত্রচালিত নৌকার জন্য প্রতিবছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) মাছ ধরার লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক, যা নির্দিষ্ট মাসুল (টাকা ২০০-১৮০০) দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে। যন্ত্রচালিত নয় এমন নৌকাগুলিও ১৯৯৫ সাল থেকে লাইসেন্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে; প্রত্যেক লাইসেন্সধারীকে মাছ ধরা ও বিক্রির তথ্যাদি অবশ্যই চট্টগ্রামের পরিচালককে জানাতে হবে; বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশী ট্রলারের প্রবেশ নিষিদ্ধ; সরকার বাংলাদেশের জলসীমায় কোন ট্রলার বা ব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে; অবৈধ ট্রলারকে নাবিক ও অন্যান্য লোকজনসহ আটক করা হবে।
জলাধার উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ (The Tank Improvement Act, 1939) সাধারণভাবে পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ নামে পরিচিত এই আইনটি ১৯৮৬ সালে সংশোধন করা হয়। এই আইনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যে কোন পতিত পুকুরের মালিককে যথাযথভাবে নোটিশ ও সময় দিয়ে পুকুরটিকে মাছচাষের আওতায় আনতে পারবেন।
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সাধারণভাবে মাছের মাননিয়ন্ত্রণ বিধি, ১৯৮৩ নামে পরিচিত এ আইনটি ১৯৮৯ সালে সংশোধিত হয়। অধ্যাদেশের প্রধান প্রধান দিক– নির্ধারিত মাসুল প্রদান করে ২৫টি শর্তপূরণকারী প্রসেসিং কারখানায় সদ্যধরা মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে; প্রসেসিং-এর সময় মানবিনষ্টকারী উপাদান ব্যবহার নিষিদ্ধ; সরকারের নিকট থেকে পণ্যের গুণগত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষেই কেবল সেগুলি রপ্তানি করা যাবে।
চিংড়িচাষ কর আইন, ১৯৯২ সরকার এই আইনের ক্ষমতাবলে চিংড়িচাষের এলাকায় বেড়িবাঁধ ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ এবং খালকাটার সুবিধা ভোগকারীদের ওপর করারোপ করতে পারে। [মোহাম্মদ শফি]
মৎস্যচাষ
খাঁচায় মাছচাষ (Cage culture) খাঁচার মধ্যে মৎস্যজাতীয় প্রাণী প্রতিপালন। সাধারণত কার্প ও পাঙ্গাশ এবং শোল ও গজার জাতীয় মাছ খাঁচায় চাষ করা হয়। বিভিন্ন মোলাস্ক (molluscs) যেমন বিভিন্ন জাতের ঝিনুক (oyster, clam) এবং বিভিন্ন জাতের চিংড়িও (prawn, shrimp) খাঁচায় চাষ করা যায়। উপসাগর, নদী, খাল, হাওর, প্লাবনভূমি ইত্যাদি উন্মুক্ত জলাশয়েই খাঁচা-চাষ চলে। এটি জাল দিয়ে উল্টানো মশারির মতো করে তৈরি করা হয়। নাইলন সুতার তৈরি এই জাল ২-৩ বছর টেকে। লোহার তারের জালের খাঁচাও আছে যা টেকে ৪-৫ বছর। বাঁশের ফালির খাঁচাও দেখা যায়। বসানোর জায়গা অনুসারে এগুলি আয়তাকার বা বর্গাকার হতে পারে। সাধারণত খাঁচা ১-২ মিটার লম্বা, ১-২ মিটার চওড়া ও গভীরতায় এক মিটার হয়ে থাকে। অন্তত ৩-৬ মাস পানি থাকে এমন জায়গায় খাঁচা বসানো হয়।

বাংলাদেশে খাঁচায় তেলাপিয়া (Tilapia nilotica), রুই (Labeio rohita), কাতলা (Catla catla) ও মৃগেল (Cirrhina mrigala) যৌথভাবে চাষ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রজাতিও অনেক সময় আলাদা আলাদাভাবে চাষ করা যায় যেমন, পুঁটি (Puntins chola), কই (Anabas testudineus), মাগুর (Clarias batrachus, C. gariepinus), শোল (Channa striatus), গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি। কেয়ার বাংলাদেশ CAGES (Cage Aquaculture for Greater Economic Security) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটি সরকারের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের একটি উন্নয়ন প্রকল্প। মুন্সিগঞ্জ জেলার বাউশিয়াঘাট ও গজারিয়া উপজেলায় মেঘনা গোমতি নদীতে CAGES পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচা চাষ শুরু করেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, সিলেট ও বরিশাল জেলার কোন কোন এলাকায়ও খাঁচায় চাষ চলছে। [আবদুস সালাম ভূঁইয়া]
মিশ্র মাছচাষ (Mixed fish culture) দ্রুতবর্ধনশীল, সহঅবস্থানক্ষম এবং পৃথক পৃথক খাদ্যাভাস ও জলাশয়ের বিভিন্ন গভীরতার খাদ্যবস্ত্ততে অভ্যস্ত কয়েক প্রজাতির মাছের একত্র চাষ। মিশ্র মাছচাষ বহুচাষ বা যৌথচাষ (polyculture, composite culture) নামেও পরিচিত। এ ধরনের চাষের মূলনীতি হলো পুকুর, বিল, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়ে কয়েক প্রজাতির মাছ পালন, যাতে তাদের পক্ষে সেখানকার বিভিন্ন বাস্ত্তসংস্থানিক অবস্থান দখল এবং এসব জলাশয়ে লভ্য জীবনধারণের সবগুলি উপকরণ ব্যবহার সম্ভব হয়। বাংলাদেশে মিশ্র মাছচাষের সাধারণ দৃষ্টান্ত হলো বড় কার্প, যেমন কাতলা, রুই ও মৃগেলের চাষ; এবং দেশী ছোট, মাছ যেমন মলা (Amblypharyngodon mola), পুঁটি ও খলিসার (Colisa fasciatus) চাষ। মিশ্রচাষের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে পুকুরে এখন বিভিন্ন বিদেশী কার্প যেমন সিলভার কার্প, সাধারণ কার্প, গ্রাসকার্প, কয়েক ধরনের ক্যাটফিশ এবং তেলাপিয়া ও চিংড়ির চাষ চলছে।
মিশ্রচাষে সিলভার কার্প বাড়তি শেওলা খেয়ে পুকুরে অক্সিজেন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায়। কারণ পুকুরে অধিক শেওলা থাকলে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। পুকুরের তলার বর্জ্যভুক মাছেরা সেখানকার জৈববর্জ্য খেয়েও অক্সিজেন পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়তা করে। গ্রাসকার্প জলজ উদ্ভিদ খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে। এছাড়া কিছু মাছ অন্য মাছের মল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন সাধারণ কার্প সিলভার কার্পের মল খায়। তাই জলজ বাস্ত্ততন্ত্রের (ecosystem) উন্নতি সাধনে মিশ্র মাছচাষ যথেষ্ট সহায়ক।
মিশ্র মাছচাষের আগে একত্রে চাষযোগ্য মাছের খাদ্যাভ্যাস ও চাষের পুকুরে লভ্য খাদ্যবস্ত্তর মজুদ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অনুপাত ও ঘনত্ব জানা আবশ্যক। ময়মনসিংহের মৎস্যচাষ গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত সাত প্রজাতির মাছের মিশ্রচাষ সফল প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলি হলো সিলভার কার্প, কাতলা, রুই, মৃগেল, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প ও সরপুঁটি এবং মজুদের হার প্রতি একরে ৫-৭ সেমি লম্বা পোনা যথাক্রমে ১২০০, ৩০০, ৩০০, ৩০০, ৩০০, ৪০০ ও ১২০০।
সফল মিশ্র মাছচাষের কয়েকটি পূর্বশর্ত হলো উপযুক্ত ও সহবাসী প্রজাতি নির্বাচন, পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়, পোনার উপযুক্ত সংখ্যা ও আকার, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য, সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ, রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ, মাছ ধরা ও বিপণন প্রভৃতি। বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন মাছই চাষ করা প্রয়োজন। দেশী বড় জাতের কার্প (রুই/কাতলা) ও চীনা কার্পের মিশ্রচাষের জন্য কমপক্ষে ০.২ একর আয়তনের পুকুর দরকার। পক্ষান্তরে ০.২ একরের চেয়ে ছোট পুকুরে মলা, পুঁটি, চাপিলা, ঢেলা, খলিসার মিশ্রচাষ লাভজনক। [মো. গোলাম মোস্তফা]
মাছের একক চাষ (Monoculture of fish) বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় কোন জলাশয়ে এক প্রজাতির মাছচাষ। সাধারণত উদ্ভিদভোজী অথবা মাংসাশী মাছ যেমন ক্যাটফিশ, কার্প বা তেলাপিয়া একক চাষের জন্য নির্বাচিত হয়। এতে জলাশয়ের স্বাভাবিক খাদ্যবস্ত্ত ও প্রদত্ত সম্পূরক খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে।
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছোট পুকুর, ডোবা, খাল, নিচু খাদের মতো অসংখ্য জলাশয় রয়েছে, যেগুলি বড় আকারের নানা জাতের মাছের মিশ্রচাষের অনুপোযোগী এবং ৫-৬ মাস পানি থাকার দরুন এগুলি সংক্ষিপ্ত জীবনচক্রের ছোট ছোট মাছ মলা, ঢেলা, চাপিলা, খলিসা, পুঁটি, টেংরা, পাবদা ইত্যাদির একক চাষে ব্যবহার করার উপযোগী। [মো. গোলাম মোস্তফা]
একত্রে ধান ও মাছচাষ (paddy-cum fish culture) পানিতে নিমজ্জিত ধানের ক্ষেতকে মাছ চাষের জন্য দুভাবে ব্যবহার করা যায় ক্ষেতকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা; এক্ষেত্রে পোনা ছাড়া হয় না, এটি কেবল ক্ষেতে প্রবেশ করা মাছ ধরার একটি পদ্ধতি অন্য পদ্ধতিতে ক্ষেতকে পুকুরের মতো ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে পোনা ছেড়ে মাছের খামার গড়ে তোলা হয়। অন্যদিকে, ধান চাষের ক্ষেতে মাছ চাষ হতে পারে প্রতি বছর একবার ধান ও একবার মাছ আহরণ করে; ধানের চারা রোপণ ও পাকা ধান তোলার মধ্যবর্তী সময়ে একবার মাছ আহরণ করা; এবং ধান ও মাছ একত্রে চাষ করা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে মাছকে গৌণ ফসল হিসেবে গণ্য করা হয়। ধান ক্ষেতে চিংড়ি (penaeid shrimp) চাষ বাংলাদেশের সনাতন পুরনো পদ্ধতি। এক্ষেত্রে ‘ঘের’ অর্থাৎ বেড় দিয়ে একটি এলাকা প্রথম ঘিরে ফেলা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরা ও তদসংলগ্ন এলাকায় জোয়ার-ভাটার নদীর তীর বরাবর লোনা পানি প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য মাটির তৈরি নিচু ঐতিহ্যবাহী বাঁধ বা বেড়ি নির্মাণ করার প্রচলন আছে। এখানে কাঠ নির্মিত ছোট স্লুইস গেটের সাহায্যে ঘেরে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত স্লুইস গেট উন্মুক্ত রাখা হয় যাতে নদী থেকে বাগদা চিংড়ি ও মাছ পোনাসহ ঈষৎলোনা পানির ঘেরে ঢুকতে পারে। এভাবে আটকা পড়া চিংড়ি ও মাছ আহরণ উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ঘেরের ভিতরে বাড়তে থাকে।

মৌসুমের সময় (জুন-সেপ্টেম্বর) বৃষ্টির পানি ঘেরের লোনাপানির ঘনত্ব হ্রাস করে। নির্দিষ্ট সময় পর পর স্লুইস গেট খুলে ঘের থেকে পানি বের করে দেওয়া হয়। মৌসুমি বৃষ্টি ও বার বার স্লুইস গেট খুলে পানি বের করে দেওয়াতে ঘেরের পানির লবণাক্ততা হ্রাস পায় এবং ভিতরের জমি ধান চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। কৃষকরা তখন জুলাইয়ের শেষ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ধানের সঙ্গে মাছ উৎপাদন করে। ঘেরের ভিতরে অপেক্ষাকৃত গভীর খাদে পানি জমা থাকে, যেখানে বিভিন্ন মাছ ও চিংড়ির পোনা আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে ঘেরে বৃষ্টির পানি জমানো হয় এবং ক্ষেতের লবণাক্ততা হ্রাসের লক্ষ্যে তা অপসারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাগদা চিংড়ি ও মাছের বাড়ন্ত পোনার আশ্রয়স্থল গভীর খাদের পানিও ক্রমে লবণাক্ততা হারায়।
একই সঙ্গে রোপা আমন ধানের চারা লাগানোর জন্য জমি তৈরি করা হয়। লোনাপানির চিংড়ির খামারে ব্যবহূত জমি সাধারণত লাঙল দিয়ে চাষ করা হয় না। রোপা আমনের চারা লাগানোর পর ঘেরের ভিতরে ৬০-১০০ সেমি বৃষ্টির পানি জমানো হয়। এ সময় চিংড়ি ও মাছ খাদের পানিতে বাড়তে থাকে। সেসঙ্গে প্লাবিত জমিতে স্বাদুপানির চিংড়ির লার্ভা, রুই-কাতলাজাতীয় মাছ ও তেলাপিয়ার পোনা ছাড়া হয়। এভাবে মৌসুমের ধান ও মাছ একত্রে চাষ করা হয়। মাছ ধরার সময় সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে, চিংড়ি ধরা হয় অক্টোবর-নভেম্বরের কাছাকাছি সময়ে। মাছ ও চিংড়ি ধরা এবং ধান কাটা সম্পন্ন হওয়ার পর ডিসেম্বরে লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য পুনরায় ঘের নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ঘেরে প্রাকৃতিক উপায়ে বাগদা চিংড়ি সংগ্রহের যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, তার বদলে এখন ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট জাতের বাগদা চিংড়ির পোনা কৃত্রিম উপায়ে সংগ্রহের প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে। [নূরুদ্দিন মাহমুদ]
ঘেরে মাছ চাষ (Pen culture) ছোট ঘেরে মাছ চাষ করার পদ্ধতি। মাছ চাষের ঘেরের বৈশিষ্ট্য হলো, এর চতুষ্পার্শ্বে কাঠের খুঁটিতে জাল বেঁধে বেড়ার সৃষ্টি করা হয় এবং এর তলায় থাকে মাটি। ১৯২০ সালের দিকে জাপানের অভ্যন্তরীণ সামুদ্রিক এলাকায় ঘেরে মাছ চাষ প্রবর্তিত হয়। চীন ১৯৫০ সালের দিকে স্বাদুপানির হ্রদে কার্প বা রুই-কাতলাজাতীয় মাছ পালনের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং পরে ১৯৬৮ ও ১৯৭০-এর মধ্যে ফিলিপাইনে মিল্ক ফিশ (Milk fish, Chanos chanos) পালনের জন্য ঘেরে মাছ চাষ প্রবর্তিত হয়। ঘেরে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ একটি নতুন প্রযুক্তি।
বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের জন্য ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষের ধারণা ১৯৭৭ সালে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮১-১৯৮৪ সালের মধ্যে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে, যেমন বাহাদুরপুর বাওড়, নবগঙ্গা নদী, ঝিনাইদহের সাগন্না বাঁওড় এবং ঢাকা মহানগরের ধানমন্ডি ও গুলশান হ্রদে পরীক্ষামূলকভাবে ঘেরে মাছ চাষের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সাগন্না বাওড়ে ০.৫ হেক্টর আয়তনের ঘেরে সম্পূরক খাদ্য যোগান দিয়ে কার্প জাতীয় মাছগুলিকে একত্রে চাষ করে আট মাসে ১,৮৯০ কিলোগ্রাম মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সিলভার কাপের্র ওজন হয় প্রায় ৩৫০ গ্রাম, যা কাতলা, রুই ও মৃগেলের ওজনের চেয়ে বেশি।

১৯৮১ সালে ধানমন্ডি হ্রদে ০.২৫ হেক্টর এলাকায় ১০০ ২৫ মিটার আয়তনের ঘেরে হেক্টর প্রতি ৩৮,৬০০টি ৪.০-৫.৬ গ্রাম আকারের মাছের ঘনত্বে পাঁচ প্রজাতির কার্প, যথা সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কাতলা, রুই ও মৃগেল ছাড়া হয়। সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করে ৬ মাসের মধ্যে মাছের গড় ওজন দাঁড়ায় ১৮৬ গ্রাম এবং সর্বমোট ১৫,১৯৫ কিলোগ্রাম মাছ আহরিত হয়। দেখা গেছে যে, পলিইথাইলিনের গিঁটহীন জাল, বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি, নাইলন রশি ইত্যাদি সামগ্রী ঘের নির্মাণের জন্য উপযোগী। প্রতি একরে ২০,০০০ মাছের ঘনত্বে রুই-কাতলাজাতীয় মাছ এবং চীনা কার্পের পোনা একত্রে চাষ উপযোগী ও লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঘেরে কার্পের সঙ্গে Macrobrachium rosenbergii, Oreochromis species, Pangasius sutchi ও Pangasius pangasius মাছের সম্মিলিত চাষও যথার্থ দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ৩ মাস বয়সের ১০ সেন্টিমিটার আকারের পোনা ব্যবহার উত্তম। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সেচ সুবিধা সম্পন্ন ০.৫০ হেক্টরের একটি ঘেরে একবার মাছ চাষে মোট ৭০,০০০ টাকা (প্রায় ১৩০০ মার্কিন ডলার) মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। [খান কামাল উদ্দিন আহমেদ]
আর্টেমিয়ার চাষ (Artemia culture) চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য আর্টেমিয়ার (Artemia) সিস্ট গবেষণাগারের পরিবেশে উৎপাদন প্রক্রিয়া। আর্টেমিয়া হচ্ছে প্রায় ১২মিমি দীর্ঘ প্লাঙ্কটনিক ক্রাসটেসিয়ান (planktonic crustacean), যা অতি লবণাক্ত পানির জীব। পৃথিবীব্যাপী শেলফিশ ও ফিনফিশের হ্যাচারিতে এর সিস্ট আহার্য হিসেবে ব্যবহূত হয়, কেননা এতে পালন পুকুরের পানি দূষিত হয় না। আর্টেমিয়ার সিস্ট কয়েক বছর অবাত অবস্থায় মজুদ রাখা যায় এবং প্রয়োজনের সময় সমুদ্রের পানিতে ছেড়ে দিলে অতি সহজে নপ্লিয়াস-এ পরিণত হয়। কয়েকটি দেশ বাণিজ্যিকভাবে এই সিস্ট উৎপাদন করে এবং আবদ্ধ পাত্রে বিপণন করে।
সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের অতি লবণাক্ত আবাসস্থলে যেমন উপকূলীয় নুন-কুয়া ও অভ্যন্তরীণ লবণহ্রদে আর্টেমিয়া দেখা যায়। কিন্তু আর্টেমিয়া সর্বত্র পাওয়া যায় না, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাকৃতিকভাবে আর্টেমিয়া জন্মায় না। এজন্য প্রয়োজন পানির পর্যাপ্ত লবণাক্ততা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০ পিপিটি-র বেশি), যা বিভিন্ন শিকারি জীবকে দূরে রাখে এবং পানির অনুকূল তাপমাত্রা (আর্টেমিয়ার প্রজনন ও বিকাশের জন্য), যা বাংলাদেশে নেই। প্রকৃতপক্ষে আর্টেমিয়ার সিস্ট বিস্তারের জন্য বাতাস, জলচর পাখি ও মানুষের মতো সক্রিয় বাহক দরকার। অনুকূল পরিবেশে অত্যন্ত ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে আবাসস্থল এদের অজস্র কলোনিতে ভরে ওঠে। ডিম্ব-জরায়ুজ (ovoviviparously) পদ্ধতিতে প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-আর্টেমিয়া ৪ দিন পর পর ২০০-৩০০ অবাধ সন্তরণশীল নপ্লিয়াস উৎপন্ন করে। দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে নপ্লিয়াস প্রাপ্তবয়স্ক আর্টেমিয়ায় পরিণত হয়।
বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে যেহেতু আর্টেমিয়া জন্মায় না, সেহেতু বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম চাষই একমাত্র বিকল্প। বাংলাদেশের ৫-৬ মাস (নভেম্বর-এপ্রিল) শুষ্ক মৌসুম। এছাড়া এদেশে রয়েছে ১৭,০০০ হেক্টরের অস্থায়ী নুন-কুয়া (saltpan), যার একাংশে লবণ ও আর্টেমিয়া সমন্বিতভাবে উৎপাদন করা সম্ভব। মাটির পাত্রের অত্যধিক লোনাপানিতেও এরা বাঁচতে পারে; উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন, জৈব বর্জ্য এবং চালের কুড়ার মতো কম দামি খাবার খেয়ে থাকে। যথাযথ জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে লবণ উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে পুকুরে আর্টেমিয়া সন্তোষজনকভাবে চাষ করা সম্ভব।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ১৯৭৬ সাল থেকে আর্টেমিয়া চাষের ওপর গবেষণা চলছে এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় একটি নুন-কুয়ায় প্রথমবারের মতো আর্টেমিয়ার সিস্ট উৎপাদন সফল হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন ভৌগোলিক স্ট্রেইন নিয়ে পরীক্ষাতেও উৎসাহজনক ফল পাওয়া গেছে। [নূরউদ্দিন মাহমুদ]
স্বল্পলোনাপানিতে মৎস্যচাষ (Brackish-water aquaculture) স্বল্পলোনাপানিতে মৎস্যচাষ (ঝিনুক ও কাঁকড়াজাতীয় প্রাণিসহ)। খামারগুলির কর্মকান্ড বাড়ছে এবং বাংলাদেশের সার্বিক মৎস্য উন্নয়ন প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব খামারে সামুদ্রিক ও মোহনার চিংড়ি, মাছ ও কাঁকড়া উৎপন্ন হয়। বাগদা চিংড়িই প্রধান লক্ষ্য, আনুষঙ্গিক হিসেবে রয়েছে কতিপয় প্রজাতির মাছ, নানা জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া। উপকূলীয় জেলাগুলির মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজারে স্বল্পলোনাপানিতে মৎস্যচাষ হয়। অবশ্য উপকূলীয় বিস্তৃত অঞ্চল স্বল্পলোনাপানির মৎস্যচাষের আওতাধীন, যা প্রধানত চিংড়িচাষভিত্তিক। সত্তরের দশকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে স্বল্পলোনাপানিতে মৎস্যচাষ শুরু হলেও চাষপদ্ধতি ছিল একেবারে সেকেলে। আশির দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশ সরকার সনাতন মাছচাষ পদ্ধতির উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে আসছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ভিতরের নিচু জমির জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রধানত স্বল্পলোনাপানির মৎস্যচাষ চলে। মূলত লোনাপানির কবল থেকে কৃষিজমি রক্ষার জন্য এসব বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। অনেক জায়গায় কৃষকেরা নিজেরাই কৃষি ও মৎস্যচাষ উভয় উদ্দেশ্যে নদীর পাড় বরাবর মাটির বাঁধ নির্মাণ করেছে। মৎস্যচাষের আওতাধীন মোট ২,৯২,৩৭৮ হেক্টর জমির প্রায় ৪৮% স্বল্পলোনাপানির জমি।
১৯৯৩-৯৪ সালে মৎস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ মে টনের কিছু বেশি। যার ২৪% ছিল কৃত্রিম মৎস্যচাষ থেকে। স্বল্পলোনাপানির খামারগুলি একত্রে চিংড়ি ও মাছ উৎপাদন করে প্রায় ৩৯,৪৭৭ মে টন, যার মধ্যে চিংড়ি প্রায় ২৫,০০০ মে টন (হেক্টরপ্রতি ২০৪ কেজি)। মোট মৎস্য উৎপাদনে স্বল্পলোনাপানির মৎস্যচাষের অবদান ছিল ওজনে প্রায় ১৫% এবং মূল্যে ৩৮.৫%। স্বল্পলোনাপানির চিংড়ি হিসেবে চাষকৃত মোট চিংড়ির পরিমাণ ছিল ওজনে প্রায় ৮০% এবং মূল্যে প্রায় ৮৪%। উৎপন্ন সর্বমোট চিংড়ির (১,০০,৫৩৮ মে টন) মধ্যে স্বল্পলোনাপানির চিংড়ি ছিল ওজনে প্রায় ২৫% এবং মূল্যে প্রায় ৫০%। তৈরি পোশাক ও পাটের পরই চিংড়ি বাংলাদেশের তৃতীয় বেশি বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য। ধারণা করা হয় জোয়ার-ভাটাবিধৌত ২,২০০,০০০ হেক্টর জমি স্বল্প-লোনাপানির চিংড়িচাষের উপযোগী।
বাংলাদেশে স্বল্পলোনাপানিতে নিবিড় চিংড়িচাষ না হলেও দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাপক চিংড়িচাষ চলছে। চাষীরা উপকূলীয় নিচু জমিতে বাঁধ দিয়ে মাছ ও চিংড়ি সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে। কোথাও কোথাও ধানচাষ ও লবণ উৎপাদনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে, আবার কোথাও এককভাবে চিংড়িচাষ হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে লবণাক্ততার পরিমাণ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। ফলে দুই অঞ্চলের চিংড়িখামারের চিংড়ি ও চিংড়ির আহরণপদ্ধতি ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে চিংড়ি/মাছের এককচাষ বা চিংড়ি/মাছ ও লবণের যৌথচাষ দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতিতে চাষ হয়, যেমন যৌথ চিংড়ি/মাছ ও ধান চাষ এবং চিংড়ি/মাছের এককচাষ। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রধানত গলদা ও বাগদা উভয় চিংড়িরই চাষ হয়ে থাকে। [ইউসুফ শরীফ আহমদ খান]
অয়েস্টার চাষ (Oyster fishery) অগভীর উষ্ণ-পানির তলদেশে অয়েস্টার ও খাবারযোগ্য ঝিনুকের চাষ। অয়েস্টার ছাড়া এই চাষের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ঝিনুকজাতীয় প্রাণী হলো মাসেল (Mussel), ক্ল্যাম (Clam) ও স্ক্যালোপ (Scallop)।

ছাঁকন পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহকারী (filter feeder) এসব প্রাণীর জীবনচক্র প্রায় একই ধরনের এবং জীবনচক্রের প্রথম দিকের পর্যায়সমূহ প্লাঙ্কটনিক।ডিমের নিষেক হয় দেহের বাইরে এবং প্লাঙ্কটনিক লার্ভা আটকে থাকার জন্য মাধ্যম প্রয়োজন হয়। চাষের জন্য ব্যবহূত খুঁটিগুলি উপকূলের অগভীর পানির স্বল্পঢালু তলদেশে স্থাপন করা হয়। প্রাকৃতিক প্রজননভূমি থেকে অয়েস্টারের ডিম সংগ্রহ করে চাষের জায়গায় স্থানান্তরিত করলে সেগুলি সেখানকার আশ্রয় অাঁকড়ে থাকে এবং ৭-৮ মাস পর অয়েস্টার ৪-৭ সেমি হলে বাজারজাত করা যায়।
বাংলাদেশে Ostrea ও Crassostrea-এর কতিপয় প্রজাতি রয়েছে এবং এগুলির চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল উপাদানই এখানে বিদ্যমান। উঁচু জোয়ারের ব্যাপ্তি, জোয়ার-ভাটার পর্যাপ্ত জলস্রোত, দোঅাঁশ কাদামাটির নিচু সমতল, ম্যানগ্রোভ বনের উপকূল ভাগ, দূষণমুক্ত অঞ্চল, লবণাক্ততার সহনক্ষম মাত্রা ও বিদ্যমান পর্যাপ্ত প্ল্যাঙ্কটনসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার অগভীর পানিতে গোঁজ, খুঁটি, তাক ফেলে বা অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে ভাসন্ত ভেলা ও লম্বা রশি ব্যবহার করে স্বল্পপুঁজি খাটিয়ে অয়েস্টার চাষ সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ না হলেও বাংলাদেশের কোন কোন এলাকার স্বাদুপানির ঝিনুকজাত মুক্তা নিয়মিতভাবে আহরণ করা হয়ে থাকে। [ননীগোপাল দাস]
মৎস্য আহরণ
স্বল্পলোনাপানির আহরণ স্বল্পলোনাপানির মৎস্যসম্পদকে মোহনার মৎস্যসম্পদও বলা হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপে অবস্থিত বিধায় বাংলাদেশের স্বল্পলোনাপানির অঞ্চলও বেশ ব্যাপক। স্বল্পলোনাপানির মৎস্যসম্পদ দু’ধরনের; উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মৎস্যসম্পদ। মাছ আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, খাদ্য সরবরাহ ও উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুস্থিত রাখার নিরিখে জাতীয় উন্নয়নে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বল্পলোনাপানির অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৎস্যসম্পদের একটা বড় অংশ হিমায়িত করে রপ্তানি হয়।
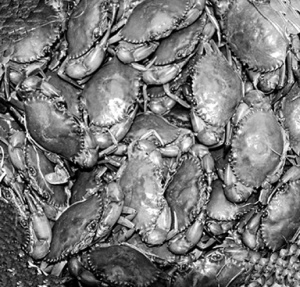
বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্বল্পলোনাপানি থেকে আহরিত মাছকে সাধারণত সামুদ্রিক মাছের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বল্পলোনাপানিতেই বাগদা চিংড়ির চাষ হয়। এটি বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য হিসেবে প্রধান রপ্তানি পণ্য। এদেশে স্বল্পলোনাপানির মাছ সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের একাংশ হলেও বহু সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ও লালনভূমি হিসেবে এ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত গলদা নামে পরিচিত স্বাদুপানির গলদা চিংড়ি প্রজননের জন্য স্বাদুপানির আবাস থেকে স্বল্পলোনাপানিতে নেমে আসে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক চিংড়ি সেখানে লার্ভা পর্যায়ে পৌঁছায়। এ আবাসে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলি অতিক্রম করে গলদা চিংড়ি স্বাদুপানিতে ফিরে আসে। একইভাবে অনেক সামুদ্রিক প্রজাতি স্বল্পলোনাপানির অঞ্চলে জীবনের একটি অংশ কাটায় এবং বাড়ন্ত বয়সে উন্মুক্ত সমুদ্রে ফেরে।
উপকূলীয় নদীসমূহ ও প্রাকৃতিক নিম্নভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের প্রায় ২৫,০০০ বর্গ কিমি এলাকা স্বল্পলোনাপানির আওতাভুক্ত। বর্তমানে ম্যানগ্রোভ বনে রয়েছে প্রায় ৭,০০,০০০ হেক্টর জমি এবং বাকিটা সাধারণত বাঁধ, বেড়িবাঁধ দিয়ে ঘিরে কৃষি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। উন্মুক্ত স্বল্পলোনাপানি এলাকা থেকে মৎস্যসম্পদ আহরণ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, কিন্তু উপকূলীয় স্বল্পলোনাপানির এলাকা ব্যক্তিমালিকানাধীন। স্বল্পলোনাপানির মোহনা, নদীমুখ ও খালগুলি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বাধীন। হিসাব মতে, বাংলাদেশে উৎপন্ন মোট মাছের ১৯% সমুদ্র থেকে আসে। স্বল্পলোনাপানি থেকে আসে মোট সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের ১০-১৫%। উপরন্তু, স্বল্পলোনাপানির অঞ্চল থেকে বছরে মোটামুটি ৩০০-৩৫০ কোটি লার্ভা পর্যায়ের বাগদা চিংড়ির (Peneus monodon) সরবরাহ আসে। এক হিসেব অনুযায়ী ১,৫০,০০০ হেক্টর উপকূলীয় এলাকা থেকে বছরে লক্ষ্যমাত্রার বাইরে প্রায় ৭০,০০০ মে টন বিভিন্ন ধরনের মাছ, কাঁকড়া ও ছোট চিংড়ি উৎপন্ন হয়।
স্বল্পলোনাপানির মৎস্যসম্পদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত স্থানীয় ও পরিযায়ী। স্থানীয় প্রজাতির মধ্যে রয়েছে খল্লা, Threadfins, Saienidaes, Perches, ফিতামাছ, Clupeids, Catfish, Bombay Duck, Camila ইত্যাদি। এছাড়া Penaeidae গোত্রভুক্ত অনেক চিংড়িও স্থানীয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো ও বিদেশে রপ্তানির জন্য ফিনফিশ ও শেলফিশ উৎপাদন এবং বাস্ত্তসংস্থানিক ভারসাম্য রক্ষার নিরিখে বাংলাদেশের স্বল্পলোনাপানিতে মৎস্যচাষ একটি গোটা পদ্ধতি হিসেবে এখনও বিকশিত হয়নি। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে অধিক উৎপাদনের জন্য জমি ও জলাশয় ব্যবহারের রেওয়াজ অত্যন্ত প্রাচীন। [মো. আবুল হোসেন]
সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সমুদ্রের মাছ ও সমুদ্রজাত অন্যান্য বস্ত্ত আহরণ ও এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। পৃথিবীর মৎস্যসম্পদ মূলত সামুদ্রিক। সর্বমোট মৎস্য আহরণের ৯৭ শতাংশের বেশি সামুদ্রিক মাছ, স্বাদুপানির মাছ মাত্র ২.৫%। অবশ্য, বাংলাদেশে প্রায় ৮০% স্বাদুপানির এবং অবশিষ্ট অংশ সামুদ্রিক ও স্বল্পলোনাপানির মাছ। বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বিগত ৪০ বছরে সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প অনেক পরিবর্তিত হলেও বাংলাদেশে এখনও তা সনাতন মৎস্যশিল্প হিসেবেই রয়ে গেছে। এখানে বিগত চার দশকে কেবল মাছ ধরার সনাতন নৌকাকে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন করার জন্য ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছশিকার উপকূলীয় মাছ ধরার অবস্থাতেই রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে গুটিকয়েক প্রজাতির মাছ ধরাই লক্ষ্য, ফলে প্রায়শই তা অতিসংগ্রহে পর্যবসিত হয়।
বাংলাদেশের জলসীমা উপকূল থেকে প্রায় ২০ নটিক্যাল কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, আবার রাষ্ট্রীয় জলভাগ থেকে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ৩২০ নটিক্যাল কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ উপযোগী অঞ্চলের আয়তন মোটামুটি প্রায় ২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যা দেশের সর্বমোট আয়তনের অধিক। সামুদ্রিক মৎস্য দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য, পানির উপরিভাগের (pelagic) ও তলদেশীয় (demersal)। বাংলাদেশের পেলাজিক মাছের মধ্যে রয়েছে পানির উপরের স্তরে সর্বক্ষণ সাঁতার কেটে বেড়ানো প্লাঙ্কটনভুক মাছ। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইলিশ, রূপচান্দা, ছুরিমাছ, ম্যাকারেল, লইট্টা, খল্লা, লাখুয়া, Sardine, pelagic shark, sword fish, কালিমা, Bonito, Skipjack, Threadfin, Smelt, ফাঁস্যা, Indian anchovy, করাতি চেলা, Dorab Herring, Indian Scad, Bone Fish ইত্যাদি এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাছ। হাঙ্গরের ছোট একটি জাত ডগফিশও পাওয়া যায়।

সমুদ্রের তলদেশে বা তলদেশের কাছাকাছি বসবাসকারী মাছকে তলদেশীয় মাছ বলা হয়। তলদেশীয় অধিকাংশ মাছ মাংসাশী বা আবর্জনাভুক। বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৪৪২ প্রজাতির মাছ থাকলেও মাত্র ২০ প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আহরিত হয়। তলদেশীয় মাছের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ Jaw fish, Croaker, Catfish, Flatfish, কালিমা, লাল দাতিনা, Snapper, Goat Fish, Crab eater, Rabbit Fish, Rock Fish, Seabass, Grouper, Silver Bream, ছুরিমাছ ও তলদেশীয় হাঙ্গর। অন্যদিকে, তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের মধ্যে কয়েক প্রজাতির কাঁকড়া ও প্রায় ১০ প্রজাতির চিংড়িও রয়েছে। Gastropoda শ্রেণীভুক্ত শামুকজাতীয় প্রাণী অন্যত্র খাদ্য হিসেবে সমাদৃত হলেও বাংলাদেশে ভোজ্য নয় বলে বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয় না। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫ লক্ষ মে টন সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়। সাধারণ বা যন্ত্রচালিত নৌকায় স্থায়ী ভাসমান ফাঁসজাল, স্থায়ী থলেজাল ও লম্বা সুতার বড়শিতেই অধিকাংশ মাছ ধরা পড়ে।
বঙ্গোপসাগর উপ-উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই উপসাগরে সমুদ্রস্রোত প্রবেশ না করার ফলে এতে পানির ভরণ-নিষ্কাশনের (upwelling) মাধ্যমে পুষ্টি পুনরাবর্তন (nutrient recycling) তেমন সম্পাদিত হয় না। অবশ্য গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সম্মিলিত স্রোতবাহিত বিশাল পরিমাণ স্বাদুপানি বঙ্গোপসাগরে এসে মেশে। এই নদীগুলি ভূ-পৃষ্ঠ বিধৌত জৈব ও অজৈব পুষ্টি উপাদান বয়ে আনে এবং স্বাদুপানি ও লোনাপানি মিশিয়ে পৃথিবীর অন্যতম বিপুল একটি স্বল্পলোনাপানির মাছের আবাসস্থল সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু, বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমাণ স্বাদুপানি মেশার ফলে মাছের জন্য এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্রের গভীর পানির মাছ এখানকার অগভীর পানিতে ছুটে আসে। ইলিশ সামুদ্রিক মাছ, জীবনের বেশির ভাগ বঙ্গোপসাগরেই কাটায়, কিন্তু ডিম ছাড়ার জন্য নদীতে আসে এবং অল্পবয়সী ইলিশ আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। [মোঃ আবুল হোসেন]
সামুদ্রিক চিংড়ি আহরণ বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টর এলাকায় চিংড়ির চাষ হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের ১০-১০০০ মিটার গভীর অর্থনৈতিক জলসীমা এলাকার (৭৬,৮০০ বর্গ কিলোমিটার) চারটি মৎস্য অঞ্চল- দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল, Swatch of No Ground ও দক্ষিণ অঞ্চলের দক্ষিণ এলাকার মৎস্যসম্পদ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে ১৯ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি রয়েছে, তন্মধ্যে কোলা বা বাঘা চিংড়ি (Penaeus merguiensis), বাগদা চিংড়ি (P. monodon), চাপড়া বা চাপদা চিংড়ি (P. indicus), বাঘতারা চিংড়ি (P. semisulcatus), হরিণা চিংড়ি (Metapenaeus monoceros) এবং হন্নি চিংড়ি (M. brevicornis) বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গলদা চিংড়ি স্বাদুপানির চিংড়ি হলেও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ডিম ছাড়ে এবং পোনাগুলি সেখানেই বড় হয়। উষ্ণমন্ডলীয় উষ্ণ জলবায়ু, ১২-৩৯ ppt লবণাক্ততা ও ৪.০-৪.৮ ppm অক্সিজেনসহ খাদ্যসমৃদ্ধ পানি চিংড়ির দ্রুতবৃদ্ধির উপযোগী। সাধারণ নৌকা (প্রায় ২০,০০০) ও মোটরচালিত নৌকা (প্রায় ১২,৭০০) থলেজাল, ট্রামেল জাল, বেলাভূমির বেড়জাল, ফাঁসজাল, দীর্ঘ লাইন বড়শি ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশের মহীসোপানে (৬৬,৪৪০ বর্গ কিমি) মাছ ধরে। জাল দিয়ে ১০-৫০ মিটার গভীরে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ ধরা হয়। উপকূল থেকে দূরে ১০-১০০ মিটার গভীর পানিতে পূর্বে উল্লিখিত চারটি এলাকা থেকে অন্তত ৫০টি চিংড়ি ট্রলারের একটি বহর চিংড়ি সংগ্রহ করে। চারটি অঞ্চলের দক্ষিণ খন্ডের দক্ষিণ ভাগ (সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে) বাগদা চিংড়ির জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। দেশে বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের ছয়টি হ্যাচারি রয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার ও খুলনার উপকূলে সূক্ষ্ম বুনটের কুনিজাল, থলেজাল ও টানাজাল দিয়ে বাগদা চিংড়ির প্রচুর লার্ভা ধরা হয়। এই পোনা সংগ্রহে অবশ্য অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের অজস্র পোনা ধ্বংস হয়। সামুদ্রিক চিংড়ি আহরণ করে হাজার হাজার লোক জীবিকা নির্বাহ করে। [মো. আব্দুল কাদের]
উপকূল দূরবর্তী মৎস্য আহরণ (Offshore trawler fishery) সমুদ্রতট থেকে দূরে যান্ত্রিক জলযান (trawler) ব্যবহার করে টানা জালের (trawl net) সাহায্যে মাছ শিকার বা অন্যান্য সম্পদ আহরণ করা হয়। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের গভীর পানিতে, বিশেষ করে উপকূলের চারটি মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্রে মাছ শিকারে ট্রলারের ব্যবহার বেশ ব্যাপক। ১৯৭৮-৭৯ সালে ট্রলারের সাহায্যে (২১-৪১ মিটার দীর্ঘ) মাছ ধরার কাজ শুরু হয়। সূচনালগ্নে ট্রলারের সংখ্যা ছিল মাত্র চারটি, কিন্তু ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৩০টিতে।
বর্তমানে, সমুদ্র উপকূলবর্তী জলসীমায় মাছ ধরার জন্য অন্তত ৭০টি ট্রলার ব্যবহার করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে টানা জাল দিয়ে ধরা ৫০টি প্রজাতির মাছ ও ১৫টি প্রজাতির চিংড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধান প্রজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে চিংড়ির দুটি প্রজাতি, বাদামি ও বাগদা চিংড়ি এবং ফিন ফিশের মধ্যে রূপালি ও কালো রূপচাঁদা, গ্র্যান্টস, ভারতীয় স্যামন, স্ন্যাপার, গোটফিশ, ক্রোকার, ম্যাকেরেল, লিজার্ড ফিশ ও ছুরি মাছ। বঙ্গোপসাগরে চিংড়ি ও ফিন ফিশ ধরার জন্য পৃথক ধরনের টানা জাল ব্যবহূত হয়। চিংড়ির জন্য ব্যবহূত জালে বাদামি চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, ভারতীয় সাদা চিংড়ি ও কলা চিংড়ি এবং ফিন ফিশের জন্য ব্যবহূত জালে ক্রোকার, ব্লচ ক্রোকার, লইট্টা, লিজার্ড ফিশ, গোটফিশ ও ইলিশ ধরা পড়ে। ফিন ফিশের জালে ধৃত মাছগুলির মধ্যে রয়েছে ২০টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। সেগুলির মধ্যে ভারতীয় স্যামন, গ্রাউপার, গ্র্যান্ট, রূপচাঁদা, ছুরিমাছ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে আহরণ করা হয়। ফিন ফিশের জালে ৩০-৮০ মিটার গভীর সমুদ্রে কিছু চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ধরা পড়ে। ত্রিশ মিটারের কম গভীর পানি থেকে ছোট আকারের দুটি প্রজাতির চিংড়ি (Metapenaeus species ও Parapenaeopis species) অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ১৯৯০ সালে চিংড়ি আহরণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০০ মে টন। ১৯৮৬-৮৭ সালে ফিন ফিশ ধরা পড়েছিল প্রায় ৭,৪০০ মে টন। অবশ্য, ধৃত শতকরা ৫০-৬৫ ভাগ ফিন ফিশকে ‘বর্জ্যমাছ’ হিসেবে গণ্য করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীদের এক হিসাব অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে বর্তমানে মজুদ মৎস্যসম্পদের পরিমাণ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:
| মাছের ধরন | মজুদ মাছের পরিমাণ(০০০ মে টন) | বছরে সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য মাছের মজুদ (০০০ মে টন) |
| গভীর সমুদ্রের মাছ | ২০০-২৫০ | ১০০-১২৫ |
| উন্মুক্ত অগভীর পানির মাছ | ১৬০-২০০ | ৩০-৬০ |
| চিংড়ি | ৩০-৬০ | ২-৬ |
[মোহাম্মদ জাফর]
হাঙ্গর আহরণ (Shark fishery) মৎস্য আহরণের অংশ হিসেবে সমুদ্র থেকে Chondrichthyes শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গের কোমলাস্থিময় মৎস্য অনেক সময় ধরা পড়ে। বাংলাদেশে অবশ্য সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে হাঙ্গর টার্গেট প্রজাতি নয়। সাধারণত অন্যান্য মাছ ধরার সময় এরা জালে আটকা পড়ে। এখানকার উপজাতিরা হাঙ্গরের মাংস ও পাখনা খায়।

সম্প্রতি রপ্তানির জন্য হাঙ্গরের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। জেলেরা সংগ্রহ করে হাঙ্গরের শক্তিশালী চোয়াল যা অলঙ্কার হিসেবে বিক্রি হয়। গিল-নেট, ট্রামেল-নেট, সেটব্যাগ নেট, টানা বড়শি এবং টানা জালে হাঙ্গর ধরা পড়ে। আটকে পড়া হাঙ্গরের মোট হিসাব জানা কঠিন, কারণ জেলেরা হাঙ্গরের পাখনা রেখে দেহ সমুদ্রে ফেলে দেয়। হাঙ্গরের পাখনার শুঁটকি রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এদেশের সমুদ্রে ১৬ প্রজাতির হাঙ্গর রয়েছে। ‘কামট’ নামে পরিচিত এক ধরনের হাঙ্গর দক্ষিণ বাংলার নদীমোহনায় প্রবেশ করে। স্বাদুপানিতে কোন হাঙ্গর বাস করে না। [মোঃ আবুল হোসেন]
মৎস্য শিক্ষা ও গবেষণা (Fisheries education and research) দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি সম্প্রসারণ, পলি জমা হয়ে জলাভূমি হ্রাস ও অন্যান্য কারণে মৎস্যসম্পদে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় এ অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য শিক্ষা ও গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশের মৎস্য চাষের বিপুল সম্ভাবনাকে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগাতে এবং মৎস্যচাষ শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের অন্যতম মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চারটি বিভাগ, একটি মৎস্যখামার ও একটি মাঠ গবেষণাগার নিয়ে গঠিত এ অনুষদ মৎস্য চাষের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে দেশের মৎস্যখাত উন্নয়ন এবং মাৎস্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন উচ্চমানের দক্ষ জনশক্তি তৈরি এই অনুষদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। অনুষদ বি.এসসি মাৎস্যবিজ্ঞান (সম্মান) ডিগ্রি প্রদান করে। অনুষদের পঠিতব্য বিষয় হচ্ছে: Fisheries Biology and Genetics, Aquaculture, Fisheries Management, Limnology এবং Fisheries Technology। এসবের রয়েছে তত্ত্বীয় ও ফলিত উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তারিত পাঠ্যক্রম।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে মৎস্যবিদ্যার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি (১৯৯৮) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে Aquaculture and Fisheries নামে পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে Institute of Marine Sciences, যেখানে সামুদ্রিক মাৎস্যসম্পদের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে Fisheries and Marine Resources Technology Discipline নামে একটি পৃথক বিভাগ।
গবেষণা মৎস্যচাষের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিতেই পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ নিজস্ব চারটি বিভাগের মাধ্যমে বিবিধ গবেষণা পরিচালনা করে। মৎস্য জীববিদ্যা ও বংশগতিবিদ্যা বিভাগ, মৎস্যকুল প্রজনন জীববিদ্যা, পোনা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য প্রজনন এবং ক্রোমোজোম ও জিন ম্যানিপুলেশনের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি ও বিপণন, জীবপরিসংখ্যান এবং মৎস্যস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মৎস্যবিদ্যায় এম.এসসি, এম.ফিল, পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা কর্মসূচি।
মৎস্যচাষ সম্পর্কিত ফলিত গবেষণা চলে কয়েকটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে। সেগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হলো মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটের রয়েছে কয়েকটি স্টেশন ও ইউনিট: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বাদুপানি স্টেশন; চাঁদপুরে নদী স্টেশন (Riverine station); কক্সবাজারে সামুদ্রিক মৎস্য প্রযুক্তি স্টেশন; খুলনায় স্বল্পলোনা পানির স্টেশন; এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে দুটি পৃথক সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট।
বিভিন্ন স্টেশনে গৃহীত গবেষণা প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে দেশের মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের সহায়তা প্রদানই মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য। দেশের সকল নীতিনির্ধারক সংস্থা, সম্প্রসারণ বিভাগ, এনজিও এবং প্রসেসিং ও রপ্তানি শিল্পকে গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহের জন্য ইনস্টিটিউট একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। [গুলরু বেগম সূফি]
গ্রন্থপঞ্জি MM Hussain, Marine and estuarine fishes of north-east part of Bay of Bengal. J. Sci. Res. Vol. 7(1), PCSIC, Dhaka, 1969. F Day, The Fisheries of India, William Dowson and Sons, London, 1878; M Shafi & MMA Quddus, Bangladesher Matsya Sampad (in Bangla), Bangla Academy, Dhaka, 1982; BFRSS (Bangladesh Fisheries Resources Survey System), Department of Fisheries, Dhaka, 1986; M Lamboeuf, Demersal fish resources of the continental shelf of Bangladesh, FAO, Rome, 1986; AKA Rahman, Freshwater Fishes of Bangladesh, Zoological Society of Bangladesh, Dhaka, 1989; WB (World Bank), Bangladesh Fisheries Sector Review, Report No 8830-BD, Dhaka, 1991; BERNASCEK et al Fisheries in the northern region of Bangladesh FAP 6, Draft Thematic Study, Dhaka, 1992; MMA Quddus & M Shafi, Bangopasagarer Matsya Sampad (in Bangla), Bangla Academy, Dhaka, 1993; FAP (Flood Action Plan), Fisheries Study and Pilot Projects, Interim Report, Dhaka, 1995; জাহাঙ্গীর আলম, কৃষি ও কৃষক, পালক পরলিশার্স, ঢাকা ২০১০।
আরও দেখুন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; মৎস্যজীবী।








