শিক্ষা
শিক্ষা ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। উপাদানের স্বল্পতার কারণে প্রাচীনকালে বাংলায় কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তার বর্ণনা দেওয়া, এমনকি সে সস্পর্কে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা খুবই কঠিন। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায় মাত্র। অবশ্য উপনিবেশিক আমলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বা এ সময়ের শিক্ষার উন্নয়নের ধারা সস্পর্কে অধিকতর সুসঙ্গত বিবরণ বিদ্যমান।
প্রাচীন যুগ প্রাচীনযুগে বাংলার শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রকৃতি যথার্থভাবে নিরূপণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সেযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে প্রাপ্ত সূত্রাদিতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।
বৈদিক আর্যরা প্রাচীন বাংলার জনগণকে দস্যু ও ম্লেচ্ছ বলে মনে করত। কিন্তু কালের স্রোতধারায় আর্যভাষা ও সংস্কৃতিই (সম্ভবত মৌর্য আমল থেকে) বাংলায় প্রবেশ করে।
সম্ভবত খ্রিস্টীয় ছয় শতকের পূর্বে বাংলার পন্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি। তবে চেষ্টাটা বোধ হয় কয়েক শতক আগেই শুরু হয়েছিল ও বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ছোট-বড় শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায়, ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুবছর অবস্থান করে অধ্যয়ন ও পুথি নকল করেছিলেন। সাত শতকে যখন হিউয়েন-সাং কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জনগণের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় কজঙ্গলে ৬/৭টি বৌদ্ধ বিহারে তিনশর উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুন্ড্রবর্ধনের ২০টি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ; সমতটের ৩০টি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুহাজারের উপর; কর্ণসুবর্ণের ১০টি বিহারে দুহাজারের উপর এবং তাম্রলিপ্তির ১০টি বিহারে একই সংখ্যক শ্রমণ ছিল। পুন্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, হিউয়েন-সাং-এর সাক্ষ্যই তার প্রমাণ।
নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে ছয়-সাত শতকের বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ মহাবিহারের মহাচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাঙালি। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান এবং হিউয়েন সাং-এর গুরু। তিনি সমস্ত শাস্ত্রে ও সূত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমণসংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাম্রলিপ্তির শিক্ষাদীক্ষার কথা আরও একাধিক চৈনিক শ্রমণের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। তা-চেঙ-টেঙ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বছর তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি পড়াশোনা করে বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাও-লিন্ তিন বছর তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে-সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং সর্বাস্তিবাদ-নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ই-ৎসিঙ্ ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন। পো-লো-হো বিহারে তা-চেঙ-টেঙ-এর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।
বাংলার বৌদ্ধ বিহার সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। হিউয়েন-সাং অনেক দেবমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এখানে বাস করতেন বেশ সংখ্যক ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় এবং অগণিত দেবপূজক। দেবপূজকগণ যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করতেন তা নয়, তারা নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও করতেন। এভাবে দেখা যায় যে, ছয়-সাত শতকের মধ্যে বাংলায় সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করে আর্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার বীজ বপন করা হয় এবং এক শত বছরের মধ্যেই তা সুফল বয়ে আনে। সাত শতকের লিপিগুলির অলঙ্কারময় কাব্যরীতিই তার প্রমাণ।
ব্যাকরণ চর্চায় বাংলার অতিপ্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সাত শতকে ই-ৎসিঙ যেসব বিদ্যা অনুশীলন করার জন্য তাম্রলিপ্তি এসেছিলেন তার মধ্যে শব্দবিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী চান্দ্রব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা। তিনি সাত শতক বা তার আগে কোন এক সময়ের লোক। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন ও তার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে। তিনি যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন তা নয়, তিনি তর্কবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির নিকট অধ্যয়ন করেন এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।
প্রাচীনকালে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায়ও বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আগম-শাস্ত্রগ্রন্থ গৌড়পাদকারিকা এ যুগেরই লেখা। কৌটিল্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকবর্গ হতে শুরু করে হিউয়েন-সাং পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হাতির লীলাভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। তাই হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলাদা একটি শাস্ত্রই গড়ে উঠেছিল এতদঞ্চলে। খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতকে রচিত হস্ত্যায়ুর্বেদ (গজ চিকিৎসা) খ্যাতি লাভ করেছিল।
সাত শতকে যে অলঙ্কৃত কাব্যরীতির সূচনা হয়েছিল, তার পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় পাল আমলের গোড়ার দিকেই। সমসাময়িক লিপিমালা ও চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্যে দেখা যায় যে, বাংলায় অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুরই চর্চা হতো। এসব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও বিদ্বজ্জন সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এসব শাস্ত্র অনুশীলন করতেন। কিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চা হতো সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করে ছোট-বড় চতুষ্পাঠী গড়ে তুলতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী গ্রহণ করতেন। বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্র একজনের নিকট শিক্ষা শেষ করে অন্য শাস্ত্র পাঠ করার জন্য অন্য আচার্যের কাছে যেতেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শী হতে চাইলে তার জন্য বিশেষজ্ঞ আচার্য পাওয়া যেত। বাঙালি ছাত্ররা অনেক সময় পড়াশোনার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেতো। ধর্মপ্রচার কিংবা বিদ্যাদানের জন্য বাঙালি আচার্যগণ অনেক সময় বাংলার বাইরে যেতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যারা করতেন, রাজা মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামন্তগণ তাদেরকে অর্থদান, ভূমিদান করতেন। পন্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদেরকে মাঝে মাঝে তারা পুরস্কৃত করতেন।
এ সময়ে পন্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই তাদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। কিন্তু এ ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা ছিল না বলে পাল যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার শিক্ষিত উচ্চ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্যে দেখা যায় যে, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যে বিচক্ষণ ছিলেন। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেব দর্শন, মীমাংসা, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিতে পারদর্শী ছিলেন।
সেনযুগ তো সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা, কাব্যচর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সুবর্ণ যুগ। তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ না করলেও শিক্ষার প্রসারই বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার পথ সুগম করেছিল। মধ্যযুগের টোল/পাঠশালারই কোন কোন আদি সংস্করণ প্রাচীনযুগে বিদ্যমান ছিল। তবে গুরুগৃহে, আশ্রমে বা বৌদ্ধ বিহারেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে শিক্ষা যে সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজপৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সহায়ক ভূমিকা অবশ্যই পালন করত। ধর্ম চর্চার পাশাপাশি পার্থিব বিষয়াদির যে চর্চা হতো, তা প্রাচীন যুগের প্রাপ্ত গ্রন্থরাজি থেকেই প্রমাণিত হয়। তবে এসব গ্রন্থাদিতে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য নেই বললেই চলে।
মধ্যযুগ বাংলার মুসলমান সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক বা উচ্চতর সবরকম শিক্ষা বিস্তারেই উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শাসক, সুফি, উলামা, অভিজাতবর্গ, গোষ্ঠীপ্রধান এবং জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ সকলেরই অবদান রয়েছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহূত হতো। সে সময় ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন কাজে নির্দেশনা দিতেন। শাসকগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এসব ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ভূমিদান করতেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা এঁদেরকে গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের এলাকায় অভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন।
তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় রীতি-নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সে কারণে দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়- হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন এবং জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে দুই সম্প্রদায়ের শাসক ও অভিজাতগণ সারা মধ্যযুগে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।
মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মকতব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল। মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেকগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আরবি ভাষাকে উৎসাহিত করা হতো। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যকরণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও আইন শিক্ষা প্রদান করা হতো। হিন্দুদের স্থানীয় পাঠশালাগুলিতে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। তাই, স্বদেশী ভাষার এ বিদ্যালয়গুলিতে কদাচিৎ মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। তাই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ফারসি ভাষা শিখতেন।
গৌড়, পান্ডুয়া, সোনারগাঁও, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে দেশ-বিদেশের পন্ডিত ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলমান শাসকগণ স্থানীয় প্রতিভাবানদের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকেও প্রথিতযশা ব্যক্তিদেরকে তাদের দরবারে আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না। পাঠশালার অনুকরণে মকতবসমূহ গড়ে উঠত যেখানে মুসলিম ছাত্রদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতো।
মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। এখানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটত। নবদ্বীপ ব্যতীত সপ্তগ্রাম, সিলেট এবং চট্টগ্রামেও সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য এসব স্থানে সমবেত হতেন।
এভাবে মধ্যযুগীয় বাংলায় যে সনাতনি শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল, তা মুসলিম শাসনের পর থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। ক্ষমতা দখলের পর উপনিবেশিক শাসকগণ বেশ কিছু সময়ের জন্য প্রাচ্যদেশীয় ভাষা শিক্ষা চালু রেখেছিলেন। কারণ, প্রশাসনিক কার্য নির্বাহের জন্য ফারসি, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় পারদর্শী লোকের তাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সনাতনি শিক্ষা ক্রমশই বিলুপ্ত হচ্ছিল এবং একটি ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে উক্ত সনাতনি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
উপনিবেশিক যুগ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকে তাদের দায়িত্ব বা আইনগত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে মনে করত না। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নবায়নকালে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলে এ ধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুদান বিতরণের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮২৩ সালে কলকাতায় একটি ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন’ গঠিত হয়। এ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে মতামত প্রদান করে এবং সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য এর তহবিল ব্যয় করে। ইংরেজি গ্রন্থসমূহ প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য এ তহবিলের একটি অংশ ব্যয় হয় এবং ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়।
এসময় খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে শিক্ষা এক নতুন অনুপ্রেরণা লাভ করে। প্রাথমিক মিশনারিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদেরকে শীঘ্রই দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে যে, ধর্মান্তরিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে অবশ্যই স্কুল চালু করতে হবে। ড্যানিশ মিশনারিগণ (১৭০৬-৯২) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদয় তত্ত্বাবধান ও সহানুভূতিপূর্ণ সহায়তা লাভ করেছিলেন। বাংলায় শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল এবং তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন, যদি শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ তাদেরকে রক্ষা না করতেন। এদের কার্যকলাপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে পাঠদান, একটি বিস্তারিত পাঠক্রম এবং সুস্পষ্ট শ্রেণি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বই-পুস্তক ছাপিয়ে মিশনারিগণ ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নয়নে প্রেরণা যোগায়। দেশীয় ভাষাসমূহ চর্চার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিষয়সমূহের শিক্ষাদান চলতে থাকে। এভাবেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম হয়।
মিশনারিগণ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়ের মতো কিছু জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় ছিলেন যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয়দেরকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেই হবে। গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক স্মারকলিপিতে তিনি জোরালো সুপারিশ করেন যে, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল করতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের উচিত গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং অন্যান্য উপকারী বিজ্ঞান বিষয়সমূহ নিয়ে অধিকতর উদার ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
জেনারেল কমিটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের উত্তপ্ত বিতর্কই বিষয়টির প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। অধিকতর সংস্কার মনোভাবাপন্ন তরুণ সদস্যগণ প্রাচ্য-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার নীতি সম্পর্কে আপত্তি জানান এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত মেকলের বিবরণী দ্বারা ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে এ বিতর্ক সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর সুপারিশমালা বেন্টিঙ্কের অনুমোদন লাভ করে।
ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পেছনে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণ বেশ সহায়ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ The Freedom of Press Act, ১৮৩৫ ইংরেজি ভাষায় বইয়ের মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রাপ্যতাকে উৎসাহিত করে এবং এভাবে পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কয়েক বছর পরে সরকারি দলিল-পত্রের ভাষা হিসেবে ফারসির বিলুপ্তি এবং এর পরিবর্তে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার প্রবর্তনও উক্ত প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। চূড়ান্তভাবে, সকল সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদাকে জোরদার করে তোলে।
১৮৫৪ সালের চার্লস উড-এর ‘education despatch’ প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি, ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ‘Grants-in-Aid’ প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং এ প্রতিবেদন সরকারের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নীতির মূল উপাদান উপস্থাপন করে। নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের শিক্ষা দানের ভূমিকা পালন করা হতে দূরে ছিল। এ সময়ে তাদের কার্যক্রম পরীক্ষা পরিচালনা, অধিভুক্তির জন্য অনুমোদন এবং ডিগ্রি ও সনদপত্র প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা কলেজ শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণে তেমন সুফল বয়ে না আনলেও নতুন শিক্ষায় শিক্ষিতগণ বিশেষ পান্ডিত্য প্রদর্শন করেন।
১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশকালে বিদ্রুপাত্মকভাবে অভিমত প্রকাশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি উচ্চাশার গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্যে পরিণত এবং সরকারি চাকুরিতে সম্মানজনক অবস্থান ও শিক্ষিত পেশার একটি পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ করত। এখন স্বল্প অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ শিক্ষার মাধ্যম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করলে এর ফলাফল যথার্থভাবেই হবে দুর্ভাগ্যজনক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি, তাদের দিক থেকে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে যথেষ্ট আগ্রহী হলেও সে প্রতিষ্ঠানগুলি জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী তাদের ছাত্রদেরকে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে নতুন ব্যবস্থা মাথাভারী হয়ে ওঠে। জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাগ্রহণ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত- এ মর্মে কমিশন সুপারিশ করে। কমিশন কেতাবি মর্যাদার জন্য উগ্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্ক এবং ভীষণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের একাংশকে অধিকতর বাস্তবধর্মী বিষয়ের দিকে মনোযোগী করার প্রস্তাব করে। কমিশন বাণিজ্য, কৃষি ও প্রায়োগিক বিদ্যা সম্বলিত বিকল্প পাঠ্যক্রম বিবেচনার জন্য পেশ করে। কিন্তু তা খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্রদের আকর্ষণ করে। যদিও প্রায়োগিক শিক্ষা সাধারণ জনগণের জনপ্রিয়তা লাভ করে, তবু সরকার এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে।
ঊনিশ শতকের শেষ দশকসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা ও অযত্নের শিকার হয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারি উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতায় অপরিকল্পিতভাবে বহু উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার কেন্দ্র না হয়ে শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে (Coaching Institutions) পরিণত হয়েছে। সরকার অবাধ নীতি (Laissez-faire) গ্রহণ করায় এসকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সামান্য।
ঊনিশ শতকের শেষার্ধে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কতিপয় মুসলিম সংস্থা এবং অন্যান্য উপদলসমূহ ব্রিটিশদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তারা এর পরিবর্তে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক আন্তরিক প্রচেষ্টার দাবি জানায়। ১৮৯৯ সালে ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লর্ড কার্জন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি অনতিবিলম্বে জনগণের অনুভূতি উপলব্ধি করেন এবং দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রতি পাঁচটি গ্রামের চারটিতেই কোন স্কুল ছিল না। প্রতি চারজন বালকের মধ্যে তিনজনই কোনরূপ শিক্ষা ছাড়া বেড়ে ওঠে এবং প্রতি চল্লিশজন বালিকার মধ্যে কেবল একজন কোন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে উল্লম্বভাবে, সমান্তরাল ভাবে নয়। সুতরাং কার্জন দুর্বল দিকগুলি সুদৃঢ় করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলির প্রতি প্রদেশসমূহের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, এগুলি বেসরকারি উদ্যোগের আদর্শ হিসেবে কাজ করবে। তিনি পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের সতর্ক নীতির মাধ্যমে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরূপ নীতি অবশ্যম্ভাবীরূপে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনকে উত্তেজিত করে তোলে, যারা মনে করেন যে সরকার সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তুমল বিতর্ক হয়। দেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্জন ১৯০২ সালে ‘Indian Universities Commission’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আকার ছোট করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে নয়, শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করবে। উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিভুক্ত কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য চাপ প্রদান করবে। শিক্ষা পাঠক্রম উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান, দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজসমূহের বিলোপ সাধন এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহে ন্যূনতম হারে ফি নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করে। তীব্র সমালোচনার কারণে শেষের দুটি সুপারিশ বাতিল করা হয় এবং অন্যান্যগুলির আইন পরিষদ ও সংবাদপত্রের বিরোধিতার মুখেও বাস্তবায়িত করা হয়।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলায় এক প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বভাবতই এই সময় শিক্ষা ক্ষেত্রেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কার্জনের শিক্ষা সংস্কার এমন এক সময়ে শুরু হয় যখন একে অবশ্যম্ভাবীরূপে শিক্ষার আমলাতান্ত্রিকীকরণের সাথে সমার্থক বিবেচনা করা হয়। পাঁচ বছরের অদম্য প্রচেষ্টার পরও কার্জন জনগণকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হন। অপর দিকে, বন্ধন দৃঢ়করণের ফলে কার্জনের নীতি এবং পদক্ষেপ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্ত্তত করে। এ নতুন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের প্রকৃতি পরীক্ষা করার এবং সম্ভব্য সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, এ নতুন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ শিক্ষা বিভাগের দ্রুত ভারতীয়করণ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় ভাষাসমূহ গ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস শিক্ষাদান এবং ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করার দাবি করে। কার্জনের প্রশাসনিক নীতিসমূহ জাতীয় শিক্ষার জন্য প্রথম সংগঠিত আন্দোলন সৃষ্টি করে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কলকাতায় একটি জাতীয় কলেজ এবং একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলায় একান্নটি জাতীয় স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করে। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন (১৯০৬)-এর লক্ষ্য হিসেবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এ আন্দোলন ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। স্বদেশী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়লে অধিকাংশ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি পরিণামে বন্ধ হয়ে যায়। এ আন্দেলনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলায় বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে তাঁর বিখ্যাত বিদ্যালয় শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদীদের দাবি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের এলাহবাদ এবং নাগপুর অধিবেশনে উচ্চারিত হয়।
কার্জন-এর উত্তরাধিকারিগণ মূল উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্ন রেখে শিক্ষানীতি কিছুটা সংশোধন করেন। কার্জনের সংস্কারের প্রতি বিরূপ জনমত সত্ত্বেও তাঁর শাসনামলে শিক্ষার উন্নতি উল্লেখযোগ্যভাবে সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পুনঃস্থাপন ও পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং সেগুলির পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা অব্যাহত রেখে সেগুলিকে শিক্ষা দানকারী সংস্থার রূপ দান করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলেজগুলি পরিদর্শন করতেন। সরকারও সতর্ক ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বিশৃঙ্খল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ হয়।
১৯১৭ সালের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে এক তদন্ত পরিচালনা করে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে কেন্দ্রীভূত থাকলেও এর প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রস্তাবসমূহের গুরুত্ব ছিল সর্ব ভারতীয়। মধ্যবর্তী কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠাসহ কমিশন একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের সুপারিশ করে। এ কলেজগুলি দুবছর মেয়াদী একটি পাঠক্রম অনুসরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং উচ্চ-মাধ্যমিকোত্তর পর্যায় হবে তিন বছর মেয়াদী একটি স্নাতক পাঠক্রম। শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠান এবং একক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতকোত্তর ও অনার্স পাঠক্রমগুলি অগ্রাধিকার লাভ করবে। বিজ্ঞান চর্চা, টিউটোরিয়াল ও গবেষণা কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করে যে, হিন্দু এবং মুসলমান বালিকা, যাদের পিতা-মাতা তাদের ১৫ অথবা ১৬ বছর পর্যন্ত শিক্ষা দান করতে আগ্রহী, তাদের জন্য পর্দাস্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নারী শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করে, যা মহিলা কলেজসমূহে শিক্ষাদানের জন্য সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার আয়োজন করবে। এ পর্ষদ বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা পাঠক্রম প্রস্ত্ততির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঢাকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক, বি.এ এবং এম.এ পরীক্ষায় শিক্ষাকে আলাদা বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।
ভারত সরকার এ প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত আকারে ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে একটি প্রস্তাব আকারে প্রকাশ করে। তখন থেকে উচ্চ-শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে যে, কোন আইনে কম-বেশি এ প্রতিবেদনের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করত।
কার্জনের নীতিসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৃহত্তম অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করায় ১৯০৫ এবং ১৯১২ সালের মধ্যে এর দ্রুত সম্প্রসারণ সাধিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রস্থানের পর সরকার শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের পক্ষে তার অভিমত ব্যক্ত করে। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নীতি বাতিল হয়ে যায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী জনমত অবশ্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষেই ছিল। ১৯১০ এবং ১৯১৩-এর মধ্যে গোখলে সরকারকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করার জন্য সাহসিকতার সাথে জোর প্রচেষ্টা চালান। বোম্বাই আইন পরিষদ পৌর এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বিটলভাই জে. প্যাটেল-এর প্রস্তাবিত বিল গ্রহণ করে, যা পরিণামে ১৯১৮ সালে বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইনে পরিণত হয় এবং তা পরবর্তীসময়ে প্রণীত আইনের আদর্শ হিসেবে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল।
১৯১৯ সালের আইনে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে এর দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর অর্পিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে, শিক্ষানীতি ও প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং চূড়ান্তভাবে জনগণের নিকট দায়ী শিক্ষামন্ত্রীর ওপর অর্পিত হয়। ইউরোপীয় রীতির শিক্ষা সংরক্ষিত বিষয় হিসেবে রাখা হলেও এটি ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে এ অনিয়ম চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয়। এর দ্বারা ‘হস্তান্তরিত’ এবং ‘সংরক্ষিত’ বিষয়সমূহের পার্থক্য চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত করা হয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেশগুলিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়।
১৯১৯ সালের আইনের দ্বারা সূচিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং এ আন্দোলন বিলাতি প্রতিষ্ঠান ও দ্রব্যসমূহ বর্জন করার নির্দেশ দেয়। শিক্ষা বিষয়ক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ খোলা এবং নির্বাচিত কেন্দ্রসমূহে বিদ্যাপীঠসমূহ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এ জাতীয়তাবাদী জোয়ার বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। প্রচন্ড সরকারি বিরোধিতার মুখে এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, অর্থ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অভাবে এ আন্দোলন তার উদ্দ্যম হারিয়ে ফেলে।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীদের অবস্থান আরো জোরদার করে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন, পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং নারী শিক্ষা ও অপরাপর অ-সুবিধাভোগী শ্রেণির শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ - প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ কর্তৃক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ন ছিল ১৯২১ এবং ১৯৪৭-এর মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক বৈশিষ্ট্য। এ আইনসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা প্রদান করে।
এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল গান্ধীর মৌলিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্তন। গান্ধীর কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হয়েছিল ছাত্রদেরকে কতিপয় মৌলিক পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিষয় বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান, যা পরে তাদের অর্থ উপার্জনের উৎস হতে পারে। এটি ছিল জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের একটি সচেতন পদক্ষেপ।
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৪৬-৪৭ সালে তালিকাভুক্ত ২১,৯৯,০০০ ছাত্রসহ উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫২৯৮; অথচ ১৯১৬-১৭ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৭,২০০ জন এবং স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫০৭টি। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে গ্রাম ও উপ-শহরে স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব স্কুলে স্বল্পোন্নত সম্প্রদায়গুলি অংশগ্রহণ করতে পারত। এসময় নারী শিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। ১৯২১-২২ এবং ১৯৪৬-৪৭ সময়কালের মধ্যে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।
বেসরকারি ভোকেশনাল বিদ্যালয়গুলিকে বিপুল আর্থিক অনুদান দিয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহ কারিগরি, বাণিজ্যিক ও কৃষি স্কুলগুলির উন্নতি সাধন করলে পেশাভিত্তিক শিক্ষা যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তহবিল ঘাটতি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব শিক্ষার উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি তখনও কলেজে কলা এবং বিজ্ঞান পাঠক্রমে ছাত্রদেরকে ভর্তির জন্য প্রস্ত্তত করতেই ব্যস্ত ছিল।
এ সময়ে (১৯১৬-১৭ হতে ১৯৪৬-৪৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এবং সমগ্র একক ও অধিভুক্ত ধরনের ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশবিশেষ। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক অঙ্গের গণতন্ত্রায়ণ ঘটে। নতুন নতুন অনুষদ, পাঠ্যক্রম ও গবেষণা প্রকল্পগুলি চালু হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে মহাবিদ্যালয় এবং তালিকাভুক্ত ছাত্রদের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদনকারী কর্মকান্ডের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। আন্তবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ গঠন এবং আন্তবিশ্ববিদ্যালয় কার্যকলাপের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাঙ্গনের জীবনে নতুন গতি সংযোজিত হয়।
ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর (১৯৪৭) উপনিবেশিক শাসনের ক্ষতিকর দিকগুলি দূরীভূত করার জন্য একটি পরিকল্পিত ও ব্যাপক শিক্ষা বিষয়ক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নতুন পরিকল্পনাকারীদের ওপর অর্পিত হয়।
১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায় ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। এই সালটি এক জলবিভাজিকা, যেমন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এরপর বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কার্যক্রম যে পথ ধরে অগ্রসর হয়, তা ভারতীয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে দুদেশের যে সম-ঐতিহ্য, তার প্রভাব মুছে যায়নি, যেহেতু ব্রিটিশ শাসনামলে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে। এর পর যে প্রতিষ্ঠানগুলির পত্তন হয়, সেক্ষেত্রেও পুরানো আদল, অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ, অনুসৃত হয়। যেমন জীবনে তদ্রুপ শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ ছেদের অবকাশ নেই।
ব্রিটিশ শাসন রেখে গিয়েছিল একটি উত্তরাধিকার। সংক্ষেপে, পশ্চিমি ধারায় ১৮৩৫-এর ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে মেকলের প্রস্তাবানুযায়ী (Mecaulay’s Minute, 1835) শিক্ষার মাধ্যম স্থির হয়েছিল ইংরেজি, আর শিক্ষার বিষয়গুলি এসেছিল পশ্চিমের উদারনৈতিক শিক্ষার বিবিধ বিদ্যা থেকে। শিক্ষায় গৃহীত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকারের নীতি। সনাতন প্রাচ্যবিদ্যা ভিত্তিক শিক্ষার জন্য সরকার কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবেনা, এদের দায়িত্ব এরাই পালন করবে। সরকারের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চশিক্ষার উপর; ভাবা হয়েছিল, সুসংগঠিত উচ্চশিক্ষার প্রভাব পড়বে নিম্নতর মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরসমূহে।
১৯৪৭ সালের পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণভাবে সেকালে নির্দেশিত ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটি-কমিশন দ্বারা সমর্থিত ব্রিটিশ নীতির প্রতিফলনই দেখা যায়। সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪৪), যা পুরোপুরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় এক নতুন প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল, ওই সময়ে পাকিস্তানের অংশে পরিণত বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হলো না। একে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছিল ভারত, পাকিস্তান দেয় নি। ইতোমধ্যে শিক্ষা পরিণত হয়েছে প্রাদেশিক বিষয়ে; করাচি, পরে ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার দূর থেকে নজরদারি করেছে। মাঝে-মধ্যে যে হস্তক্ষেপ করেছে তার মধ্যে সদিচ্ছার প্রকাশ যেমন ছিল, আবার অজ্ঞতা-প্রসূত ও কুফল প্রদায়ী হস্তক্ষেপও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে।
স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকার স্কুল পর্যায়ে একটি নতুন পাঠ্যক্রম প্রস্ত্ততির লক্ষ্যে প্রবীণ রাজনীতিক ও ইসলামি শাস্ত্রে সুপন্ডিত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ’র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। কমিটির সুপারিশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ মাতৃভাষা ভিত্তিক। ধর্মশিক্ষা থাকবে, তবে তা হবে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল এক কথায় দুঃখজনক। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ১৯২০-এর আইনে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, তা কেড়ে নেওয়া হলো। সরকারকে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এর মধ্যে উপাচার্যের নিয়োগও ছিল এক নতুন ও ব্যাপক ক্ষমতা, যা আরও দুঃখজনক। বহু-সংখ্যক কলেজ, কিছু সরকারি, অধিকাংশ বেসরকারি, সবই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। এই বিশ্ববিদ্যালয় জন্মাবধি ছিল একটি অধিভুক্তিহীন শুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল দায়িত্ব প্রায় শতবর্ষকাল পালন করে এসেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সকল দায়িত্ব পালনের না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল যোগ্যতা, বা কিছুমাত্র আগ্রহ। নতুন ব্যবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পেল দারুণ আঘাত, আর কলেজসমূহের ভাগ্যে ছিল নামে মাত্র অ্যাকাডেমিক নজরদারি।
১৯৪৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি এ রকম উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিচের স্তরে, কলেজসমূহ ও প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুলসমূহ নিয়ে একটি বেসরকারি সেক্টর। এর ফলে শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সরকারের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার যেভাবে এই চাহিদায় সাড়া দিয়েছে, তা কখনও যদিও বা সঠিক হয়েছে, অন্য সময়ে তা আবার হয়ও নি। কখনও লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ও লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে কিন্তু সকল ব্যর্থতার পরও, এই প্রদেশে, পরবর্তীকালের বাংলাদেশ রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাবাহিক ও রৈখিক অগ্রগতি।
প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ওপরই বর্তমান সরকারের মনোযোগ সর্বাধিক। বিশ শতকের শেষ দশক থেকেই এর সূচনা। গুরুত্বানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে, পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-পরম্পরায় সেটা ধরা পড়ে। এর উৎস রয়েছে সংবিধানের (১৯৭২) ১৫ ও ১৭ নং অনুচ্ছেদে এবং ১৯৭৪-এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুস্পষ্ট সুপারিশের মধ্যে। সংবিধান ও রিপোর্ট, দুটিতেই প্রাথমিক শিক্ষা চিহ্নিত হয়েছে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে। ১৯৭৪-এ, সংবিধানের ব্যবস্থামতে, সরকার কর্তৃক জারিকৃত জাতীয়করণ ডিক্রির আওতায় আসে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক স্কুল। শিক্ষার ইতিহাসে এ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এরপর, একাদিক্রমে প্রত্যেক পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আবর্তক ও উন্নয়ন উভয় খাতেই। বর্তমানে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা সরকারি স্কুলের প্রায় সমান। এর অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। এগুলি বহুলাংশে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত। তবে এদের পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নেয় নি। নগরস্থ যে সকল স্কুলের ইংরেজির প্রতি ঝোঁক, যদিও জাতীয়ভাবে গৃহীত পাঠ্যক্রম এরাও মোটের উপর অনুসরণ করে, প্রায় ক্ষেত্রেই এরা সরকারি সাহায্য-নির্ভর নয়। এর পরও স্কুল-বয়সী ছেলে-মেয়ে যারা স্কুলে যায়না তাদের সংখ্যা বিস্তর। কিছুদিন থেকে কতিপয় বেসরকারি সংস্থা (NGO) পরিচালিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সমান্তরাল ধারার বিকাশ ঘটেছে। এছাড়া কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অংশীদার পরিচয়ে দেখা দিয়েছে। এই তালিকায় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আরও কিছু সংস্থা ও কয়েকটি রাষ্ট্র।
আলোচ্য সেক্টর যে গুরুত্ববিচারে এগিয়ে রয়েছে এবং এর মর্যাদাও যে ক্রমবর্ধমান, তার একটি কারণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। ১৯৯০-এর মার্চে থাইল্যান্ডের জোমটিন (Jomtein)-এ অনুষ্ঠিত হয় সর্বজনীন শিক্ষা বিষয়ে বিশ্বসম্মেলন। এই সম্মেলনে ও সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ নিউ ইয়র্কে শিশু আধিকার বিষয়ে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়, বাংলাদেশ তার প্রতি পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করে। উপরন্তু ডিসেম্বর ১৯৯৩-এ দিল্লির উচ্চ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৯টি উন্নয়নশীল দেশের ‘সবার জন্য শিক্ষা’ বিষয়ে শীর্ষ ঘোষণার প্রতিও বাংলাদেশ দায়বদ্ধ।
১৯৪৭ পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে মন্দগতি এর মূল সমস্যা। ওই বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশিষ্ট একটি গ্রামের বিপরীতে ছিল বিদ্যালয়হীন ৪টি গ্রাম। স্কুল গৃহগুলি ছিল হীনাবস্থায়। বেশির ভাগ শিক্ষক ছিলেন প্রশিক্ষণহীন, তাঁরা বেতনও পেতেন অতি সামান্য। সরকারের উপর ন্যস্ত হলো একটি দুর্বহ কাজের ভার- এই হীনাবস্থা থেকে গোটা সেক্টরকে একটি মানসম্মত স্তরে তুলে আনা। কিন্তু সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার বেলায় বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার বেলায়, চিরকালই ছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২, বাংলাদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন কাল পর্যন্ত, প্রাথমিক শিক্ষা ও দেশের সাক্ষরতার স্তর, দুটিই ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী জড়ত্বের শিকার।
১৯৭২-৭৩-এ ৩৬,০০০-এর অধিক সংখ্যক স্কুলের সরকারিকরণ এক নবপর্যায়ের সূচনা বলে গণ্য হয়। তবে এর ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বজনীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কিন্তু ১৯৭৪-এর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে লক্ষ্য অনেক বেশি স্পষ্ট ভাষায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে নতুন কৌশল প্রস্তাবিত হয়েছিল। ১৯৮১-র প্রাথমিক শিক্ষা আইনে (The Primary Education Act, 1981) মহকুমা পর্যায়ে ‘স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ’ (Local Educational Authority) গঠনের ব্যবস্থা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এ উদ্যোগটি ফলপ্রসূ হয় নি এবং হয় নি মূলত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে। এরপর এলো ১৯৯০-এর ‘বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন’। এতে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় একটি সমন্বিত কর্মোদ্যোগের সূচনা হয়েছে, যার লক্ষ্য নিরক্ষতার উচ্ছেদ। এই উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। এসব প্রকল্পের আওতায় রয়েছে একদিকে আনুষ্ঠানিক অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং এ ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানে বেসরকারি সংস্থাগুলি বড় ভূমিকা পালন করছে। সরকারিভাবে দাবি করা হচ্ছে, বর্তমানে (২০০১-২০০২) সাক্ষরতার হার ৫০% থেকে ৬০%-এর মাঝামাঝি কোন এক অবস্থানে। এ ছাড়া, জেলা পর্যায়ে সাক্ষরতা অভিযানের ফলে কয়েকটি জেলা পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করেছে বলে অন্তত সরকারি দাবি।
মাধ্যমিক শিক্ষা ১৯৪৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিস্থিতি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ। অধিকাংশ স্কুল ছিল বেসরকারি সেক্টরে। প্রতি জেলা সদরে ছিল একটি করে জেলা স্কুল। উপনিবেশিক শাসকদের ধারণা ছিল জেলা স্কুলগুলি কাজ করবে বেসরকারি স্কুলসমূহের আদর্শ বা মডেল হিসেবে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষার বেলায়, তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও জড়িত না হওয়ার নীতি ছিল কার্যকর। প্রসঙ্গত, একই নীতির সম্প্রসারণ দেখা গিয়েছে কলেজ স্তরের শিক্ষার বেলায়।
আট বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ওকালতির শুরু সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪৪) থেকেই বা তারও পূর্ব থেকে। পরবর্তী সময়ে সকল পর্যালোচনায় ধারণাটি জোরালো সমর্থন লাভ করেছে, বিশেষত কুদরাত-এ-খুদা কমিশন নামে সমধিক পরিচিত ১৯৭৪-এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে। ধারণাটি বর্তমানে নীতিগতভাবে সমর্থিত, যদিও এর বাস্তবায়ন শুরু হয় নি। যদি এর বাস্তবায়ন ঘটে, তবে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী জড়িত কাঠামোগত সমস্যাটি জটিলতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
১৯৪৭-এর পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের গতি প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় দ্রুততর ছিল। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের ঝরে পড়ার হার অত্যধিক হওয়া উল্লিখিত তারতম্যের অন্যতম কারণ।
ব্যবস্থাপনার দিকে স্বাধীনতা-উত্তর কালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব হয়েছিল স্যাডলার কমিশন-এর সুপারিশে (১৯১৭-১৯)। তবে অবিভক্ত বাংলায় এ-প্রস্তাব কার্যকর হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাভুক্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যাল এলাকা।
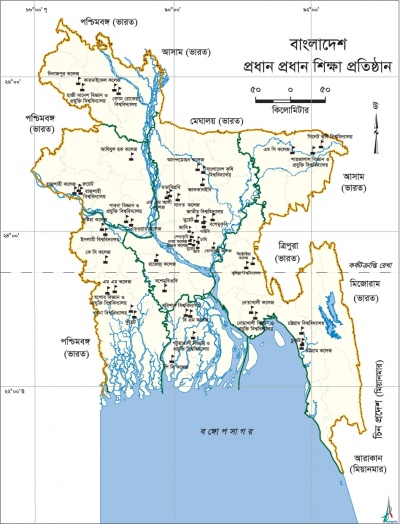
ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড গঠিত হলে (East Bengal Secondary Education Board) বোর্ড মাধ্যমিক স্কুলগুলির অধিভুক্তি ও পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ১৯৫৪ সালে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড গঠন। আরও পরে দেশের ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য বোর্ডটিকে ছয়টি ভাগে বিভাজন করে প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন বিভাগ প্রধান করা হয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনার, নামে মাত্র হলেও, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আজও অব্যাহত আছে। সরকারের অর্থায়ন পদ্ধতির ও নীতির ফলাফল হয়েছে নেতিবাচক; স্থানীয় সমাজ নিজেদের গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নীতিগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ গৃহীত হয়েছে, তবে প্রাথমিক শিক্ষার মতো অতোটা দৃঢ়তার সঙ্গে নয়। উভয় ক্ষেত্রেই এ নীতির অগ্রগতির তালমাত্রা বাঁধা রয়েছে প্রস্তাবিত ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের তালমাত্রার সঙ্গে। স্কুলের অনুমোদন, পাঠ্য পুস্তকের যোগান, পরিদর্শন এবং সর্বোপরি দুটি পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, ১০ম শ্রেণির পর মাধ্যমিক, ১২শ শ্রেণির পর উচ্চমাধ্যমিক, এই দায়িত্ব ভাগ করে নেয় ৬টি বোর্ড।
প্রচলিত ব্যবস্থায়, এই পর্যায়ে দুটি পাবলিক পরীক্ষা, বিশেষত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, ভবিষ্যৎ শিক্ষার গতি নির্ধারণ করছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্বই বেশি। কারণ এটা হলো উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বার।
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও মান, দুটি প্রসঙ্গেই তীব্র সমালোচনা হয়েছে। বিস্তর সংখ্যায় আছে বেসরকারি স্কুল, যেখানে আছে উপযুক্ত শিক্ষক মন্ডলীর অভাব। এগুলির সরকারিকরণের কোন পরিকল্পনা নেই। বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে এই নীতি ফলপ্রসূ না হওয়াও স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারের এই অনীহা বোধগম্য। বেসরকারি স্কুল (ও কলেজ) শিক্ষকদের অব্যাহত দাবি, সরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের সমান বেতন স্কেল, এ দাবি আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের নীতি হলো সাধারণভাবে শিক্ষামানের মানোন্নয়নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ। স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার মূল দুর্বলতাগুলি দিনে দিনে স্পষ্টতর হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিফলতার উচ্চহার থেকে ধরা পড়েছে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ, উভয়ক্ষেত্রেই যোগ্যতার অভাব। স্বভাবতই, বিদ্যমান পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে সকল পর্যায়ে ও সকল মহলে, সরকারি মহলেও, এক গুরুতর দুশ্চিন্তার।
১৯৫৯-এর কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী, ৮ম শ্রেণির পর পৃথক ধারার শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছিল। অভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথাগত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছিল। দৃশ্যত, মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ম্ভরতা উপেক্ষিত হলো, বা সম্ভবত যে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক স্তর প্রস্তাবেই ছিল, বাস্তবে পরিণত হয় নি, সেটাই অধিকাংশ পড়ুয়ার জন্য প্রান্তিক শিক্ষা ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কোন স্পষ্ট ও বিস্তারিত শিক্ষানীতি ঘোষিত হয় নি, বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনে এক খন্ডিত পাঠক্রম থেকে উদ্ভূত হলো এক শ্রেণির শিক্ষিতের, যারা প্রকৃত শিক্ষার অনেক মৌলিক বিষয়ে তেমন কিছুই শেখেনি।
বাংলাদেশ পর্যায়ে ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটি’ (National Carriculaum Committee, 1976-78) এই ত্রুটির সংশোধনের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেছিল। এর বাস্তবায়নে একটা অসুবিধা দেখা দিল গ্রাম ভিত্তিক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করা। বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজির পঠন-পাঠন গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় না। এর ফলে পরবর্তী স্তর, উচ্চশিক্ষার ওপর পড়ে এর ক্ষতিকর প্রভাব। অতীতে অনেক শিক্ষা-সংস্কারমূলক চিন্তা বিফল হয়েছে দুটি কারণে: কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের সংকল্পে দৃঢ়তার অভাব ও সম্পদের অপ্রতুলতা। কিভাবে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর, অভ্যন্তরীণ ও আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধিত হবে, তা এ মুহূর্তে অনুমান সাপেক্ষ। এক্ষণে, কোথাও মাধ্যমিকের শেষ দুবছর স্কুলের কাজ, কোথাও তা ৪ বৎসরের কলেজে নিম্নস্তরের কাজ, অথবা এ দুটি শ্রেণি নিয়েই চালু রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। এই ইন্টারমিডিয়েটকে স্যাডলার কমিশন দেখেছিল একটা মধ্যবর্তী স্যান্ডউইচ কোর্স হিসেবে, যা ম্যাট্রিকুলেশন/এনট্রান্স পর্ব শেষ করার পর ভালো ছাত্রদের জন্য, ডিগ্রি অভিসারীদের জন্য প্রস্ত্ততির কাল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, অধিকাংশ ছাত্রের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন প্রান্তিক পরীক্ষা নয়। পরবর্তী সময়ের চিন্তায় এই মধ্যবর্তী স্তরটি ১১শ-১২শ শ্রেণি মাধ্যমিকেরই অংশ বিবেচিত হয়েছে। নতুন নামে এর পরিচয় উচ্চমাধ্যমিক। এখন যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হলো শিক্ষা-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হলে বর্তমান ডিগ্রি কলেজের নিচের দুটি ক্লাস উঠে যাবে, স্কুলের হবে ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়ন, ১১শ-১২শ শ্রেণির সমন্বয়ে। স্কুলের প্রাথমিক অংশটি উঠে যাবে। আর এই যোগ-বিয়োগ কর্মের সঙ্গেই জড়িত থাকবে আরও একটি মাত্রা শিক্ষকমন্ডলীর পুনর্গঠন।
বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতা, যথাযথ মান ও সচলতা বজায় রাখার জন্য সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে (দাখিল, আলিম পর্যায়) একটি একক পদ্ধতির আওতায় আনয়ন। পাকিস্তান আমলের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে পুনর্বিন্যস্ত করে বর্তমানে সারা দেশে সাতটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ইসলামী শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১০ সালে অনুমোদিত নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পর্যায়ক্রমে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষার স্তর তিনটি। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর, সেকেন্ডারি শিক্ষার মেয়াদ সাত বছর। এ পর্যায়ে রয়েছে তিন বছরের জুনিয়র সেকেন্ডারি, দুই বছরের সেকেন্ডারি এবং দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক বা হাইয়ার সেকেন্ডারি শিক্ষাকোর্স। অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র সেকেন্ডারি পর্যায়ের ছাত্ররা সমাপনি পরীক্ষার মাধ্যমে সেকেন্ডারি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে।
উচ্চ শিক্ষা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব খন্ডে (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) যে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রাশুরু, উনিশ শতকে তার গোড়াপত্তন ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত সকল কলেজে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়েছে, ছাত্ররা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরীক্ষায় বসেছে এবং তার দেওয়া ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় যে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা পৌরসভার সীমানার মধ্যে। এর বাইরে সারা দেশের সম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাই যুক্ত ছিল যে বৃহত্তর ব্যবস্থার সঙ্গে, তার শীর্ষ অবস্থানে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
দেশ বিভাগের কারণে এই অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারীর ব্যাপক ভূমিকা বর্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ঢাকার সমস্যা ছিল অনেক। জন্ম থেকেই ঢাকা একটি এককেন্দ্রিক (Unitary) ও শিক্ষাপ্রদায়ী (Teaching) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় নিয়ে চলেছে। এর দূরবর্তী মডেল ছিল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। এর আবাসিক হলগুলি ছিল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের কলেজের অনুকৃতি। এর ৩ বছরব্যাপী অনার্স কোর্সও ওই দুটি মডেল থেকে ধার করা। এর টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাও ছিল ওদের প্রচলিত টিউটোরিয়ালের ছকে তৈরি। সংক্ষেপে, শিক্ষাগত ও কাঠামোগত, উভয়তেই, অর্ধশতাধিক বছর পূর্বেকার লন্ডনের মডেলে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। এখন ঢাকার সমস্যা হলো দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা। বাস্তব বিবেচনায় কলেজগুলিকে তাদের পূর্ব প্রচলিত কোর্স নিয়ে চলতে দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আর কোন বিকল্পপন্থা ছিল না। কলেজে বজায় রইল ২ বছর মেয়াদী পাস ও অনার্স কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল রইল ৩ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, রাজশাহী শহরে; তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ সালে, চট্টগ্রামে, শহর থেকে কিছুটা দূরে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার দৃষ্টান্তে ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স গ্রহণ করে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কলকাতার ২ বছরের অনার্সকে ৩ বছরে উন্নীত করে অন্তত অনার্স ধারাকে এক জায়গায় মিলাতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে দারুণ চাপ পড়ে সেই কলেজগুলির ওপর, যারা দীর্ঘকাল কলকাতার অধীনে ও পরবর্তী সময়ে কিছুকাল ঢাকার অধীনে ২ বছরের অনার্স কোর্স চালু রেখেছিল। এই চাপের কারণে কোন কোন কলেজ অনার্স কোর্স বন্ধ করে দেয়, যারা চালু রাখে তারা বেসামাল হয়ে পড়ে, তবে হাল ছাড়ে না।
রাজশাহী ও চট্টগ্রামের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সাংগঠনিকভাবে প্রধানত ঢাকার অনুগামী হয়। ঢাকা এতদিনে পূর্ব চরিত্র হারিয়ে পরিণত হয়েছে মিশ্রচরিত্রের প্রতিষ্ঠান, একাধারে শিক্ষাপ্রদায়ী ও অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারী বিশ্বদিল্যালয়ে। একই মিশ্রচরিত্র নিয়ে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়। এ ছাড়াও, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব বিস্তৃত ক্যাম্পাস গঠনের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলে। ক্যাম্পাসে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হল, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক বৃহদংশের জন্য আবাসন ব্যবস্থা। ঢাকাকে এই জন্মযন্ত্রণা সইতে হয় নি, যেহেতু একটা তৈরি ক্যাম্পাস নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সৌভাগ্য অন্যদের হয় নি। তাদের শুরু করতে হয়েছে শূন্য থেকে।
পাকিস্তান পর্বের (১৯৪৭-৭০) শেষ দিকে প্রদেশে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাশুরু করে: ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১) ও ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি (১৯৬২)। দ্বিতীয়টি একেবারে নতুন নয়, পূর্বতন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নীত রূপ।
পাকিস্তান পর্বের এই বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাভিত্তিক কলেজসমূহের সমন্বয়ে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ ছিল যতোটা রৈখিক (Linear) ততোটা উল্লম্ব (Vertical) নয়।
আইয়ুব শাসনের দশকে দুটি কমিশন কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন (১৯৫৯) ও কমিশন অন স্টুডেন্ট প্রবলেম্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার (১৯৬৪-৬৬), বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সচেতনতার সাক্ষর রেখেছিল। প্রথমটা ছিল সামরিক শাসন-সুলভ সংস্কার চিন্তাভাবনা উৎসাহের ফলশ্রুতি। শরীফ কমিশন (CNE-র সমধিক প্রচলিত নাম) রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়টি ছিল দীর্ঘতম, ৪৬ পৃষ্ঠা। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৬ পৃষ্ঠা। আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র ৬ পৃষ্ঠা। এই ভারসাম্যহীনতা অর্থবহ।
পূর্ব পাকিস্তানে বহুলভাবে নিন্দিত হলেও CNE উচ্চ শিক্ষার এই বিষয়গুলির উপর কিছু প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছে ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট পর্যায় পরিচয়ে উচ্চশিক্ষা, যা ইন্টারমিডিয়েটের ঝামেলামুক্ত; ডিগ্রি পাস ও অনার্সের মেয়াদ ৩ বছরে বর্ধিতকরণ; ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও সে উদ্দেশ্যে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজস গঠন; পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন; গবেষণা; শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষক নির্বাচন নিয়োগ ও পদোন্নয়ন; ছাত্র কল্যাণ ও শৃংখলা; বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী এক অজটিল প্রশাসনিক কাঠামো। এরই পরিণতি হিসেবে আসে ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সসমূহ (১৯৬১) ও ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে গঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব পূর্বাভাস।
CNE রিপোর্টটি সুলিখিত। এর একটা ত্রুটি, ঢালাও মন্তব্যের প্রবণতা, মন্তব্যের সমর্থনে তথ্য উপাত্ত পরিবেশনে ব্যর্থতা। এটি প্রকাশের পর এর বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল: (i) ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট অংশ বিচ্ছিন্ন করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সরকারি কলেজ দিয়ে; (ii) ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষা গুরুত্ব পায়; (iii) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় আইন রদ করে সেস্থলে নতুন অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হয় (১৯৬১)।
বেশ কিছু সুপারিশ ছিল ব্যাপক সংস্কারমুখী ও বিতর্কিত। কিন্তু কৌশলে, সরকারি নির্দেশে ও গোপন সার্কুলারে তর্ক-বিতর্কের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। পাবলিক ডিবেট-এর কোন সুযোগ থাকে না।
রিপোর্টের মূল সুর ছিল অতিমাত্রায় নির্দেশনাপূর্ণ। এ ছাড়া ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে, শিক্ষাঙ্গনে ও বাইরে সরকারের প্রতি বিরূপতার দ্রুত বিস্তার ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে ইতোমধ্যেই যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তা অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। ফলে, উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় কমিশন গঠিত হলো। সভাপতি বিচারপতি হামুদুর রহমান, যিনি ইতঃপূর্বে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাভিষিক্ত ছিলেন। অন্য ৩ জন সদস্য সকলেই ছিলেন সাংবিধানিক পদাধিকারী। শিক্ষাবিদ কেউ নন। তবে যখন কাজী আনওয়ারুল হক ভিন্ন দায়িত্বে চলে গেলেন তখন তাঁর শূন্য আসনে যোগ দিলেন ড. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ। ৪ সদস্যের কমিশনে একমাত্র শিক্ষাবিদ।
ছাত্র অসন্তোষ কিছুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করছিল এবং দিনে দিনে ক্যাম্পাসসমূহ প্রচন্ড বিক্ষোভের রূপ গ্রহণ করছিল। এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কমিশন নজর দিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়ক বৃহত্তর প্রসঙ্গের প্রতি। এই কাজ করতে গিয়ে কমিশনের মনে হলো, পূর্ববর্তী কমিশনের কোন কোন সুপারিশ সবিশেষ আদেশাত্মক, যা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ছাত্রদের অভিযোগ ছাড়াও শিক্ষকদের অভিযোগও বিবেচনায় আনে কমিশন। পূর্ববর্তী কমিশন যে সুনির্দিষ্ট কাজের সময় বেঁধে দিয়েছিল, তার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল না। একই সময়ে শৃংখলা বিষয়ক নীতিমালার সমর্থন করা হলো এই বিবেচনায় যে, এর মধ্যেই আছে শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা। এতে অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদারও হানি হয় না।
কমিশনের কার্যকালে, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষটি মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী হলেও এর ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে। তাসখন্দ চুক্তি সাক্ষর ও যুদ্ধবিরতির পর সারা দেশে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই খন্ডেই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা করায়ত্ত হয় জেনারেল ইয়াহিয়ার ও কিছুদিনের জন্য ফিরে আসে রাজনৈতিক সুস্থিরতা। একজন এক ভোট, এই ভিত্তিতে দেশ যখন অপেক্ষা করছে সাধারণ নির্বাচনের, তখনই এয়ার ভাইস-মার্শাল নূর খানকে দেয়া হলো একটি নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব।
নয়া শিক্ষানীতি (The New Educational Policy, 1969) ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট, ইতিবাচক চিন্তায় সমৃদ্ধ ও এর মধ্যেই ছিল একটি সংস্কারমূলক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের রূপরেখা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ, সিনেটের পুনর্বাসন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন (যা NEP কেবল আভাসে চেয়েছিল ও CSPW/হামুদুর রহমান কমিশন পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল)-এ সবই ঠাঁই পেল NEP-র সুপারিশ মালায়। রিপোর্টটি মূল্যবান এ জন্য যে, এর সুর ইতিবাচক এবং এর মধ্যেই ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্বাভাস রয়েছে।
স্পষ্ট দৃষ্টিতে, জাতীয় ইতিহাসের এই পর্বে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ সুষ্ঠু অগ্রগতির সংবাদ মেলেনা। অংশত এজন্য দায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতা। সামরিক শাসনামলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়েছে সামরিক ব্যয়ে, মানব সম্পদ উন্নয়নের বিনিময়ে। গণশিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনকে দারুণভাবে উপেক্ষ করা হয়েছে। ফলে, যখন ১৯৭১-এর শেষে পূর্ব পাকিস্তান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে দেখা দিল, তখন এর যাত্রারম্ভে পেল এক বিধস্ত অর্থনীতি ও এক বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা।
স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার প্রশ্নে সূচনাপর্ব ছিল উৎসাহজনক। ওই সময়ে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত জাতীয়করণ আদেশের উলেখ পূর্বেই করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের জন্য সরকার অপেক্ষা করে নি। বিশ্ববিদ্যালয় মহলের অ্যাকাডেমিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিল সরকার। ১৯৬১-র ঘৃণিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স-এর জায়গায় এলো একগুচ্ছ নতুন আইন, যেগুলি ছিল ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত। একই সময়ে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে ঘোষিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের জন্মের কথা।
এ সময়ে আরও গঠিত হয় ড. কুদরাত-এ-খুদার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট (মে, ১৯৭৪) এ দেশের শিক্ষা ভাবনার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। এই দলিলের কুলক্ষণ হলো আদর্শবাদ ও বাস্তবতাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উচ্চাশা। এর মধ্যে আছে সকল মাত্রায় পুনর্গঠন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে একটি স্বল্পমেয়াদী ও একটি দীর্ঘ মেয়াদী দৃশ্যপট। এর সকল প্রত্যাশা ও সকল ভবিষৎ ভাবনা সত্যে পরিণত হয় নি। কিন্তু সেজন্য এর স্থায়ী মূল্য কমে নি, কারণ এর মধ্যেই এক জায়মান রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক স্বপ্ন সংরক্ষিত রয়েছে।
এই রিপোর্ট এর পুঙ্খানুপুঙ্খতা সত্ত্বেও, উচ্চশিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নে বিস্ময়করভাবে নীরব। অ্যাক্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো অনেকটা সাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অনুসরণে এবং মঞ্জুরী কমিশনের যাত্রারম্ভ হলো, এই স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান করবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে।
১৯৮৬ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ কার্যক্রম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় নি। যদিও এই মধ্যবর্তী বছরগুলি একেবারে নিষ্কর্মা ছিল না। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছিল বাড়বাড়ন্ত। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম- এর সঙ্গে অধিভুক্ত কলেজগুলিও সংখ্যায় ও আকার-আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির ছিল দুটি দিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক, কারণ এর মধ্যেই প্রকাশ পায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ে জাতির আকাঙ্ক্ষা, নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে যা বেগ সঞ্চার করেছিল। এর ফলে আবার বহু সদ্যোজাত কলেজকে স্বীকৃতিদানের জন্য চাপ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর; এগুলি ছিল শিক্ষক ও সরঞ্জাম, উভয় দিক দিয়েই দুর্বল, সেহেতু অ্যাকাডেমিক চাহিদাপূরণে অযোগ্য। এটা নেতিবাচক দিক।
উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শুরুতেই সমস্যাটি শনাক্ত করেছিল শিক্ষাকমিশন। কমিশন শিক্ষাপ্রদায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কলেজ অধিভুক্তির দায়মুক্ত করার কথা ভেবেছিল। কমিশনের প্রস্তাব ছিল ৪টি কেবলমাত্র অধিভুক্তির দায়িত্বপালনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যারা কলেজসমূহের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। এ প্রস্তাব কার্যকর না হতেই ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সত্তর ও আশির দশকে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের তুলনায় দ্রুততর বেগে। এটা হলো প্রকৃত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব। কিন্তু পরিসংখ্যানই এ ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়।
স্বাধীনতার পর সরকারি পর্যায়ে আরও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ১৯৯০; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০; বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২।
প্রথম তিনটি প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি প্রচলিত ধারণা কার্যকর ছিল: বিশ্ববিদ্যালয় একটি জনবহুল দেশের এক বৃহৎ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য পূরণে নিবেদিত এক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান; সেই অঞ্চলের সকল ডিগ্রি কলেজের সমন্বয়কারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এই নীতির উপরে। একই পন্থায় এলো সিলেটের শাহজালাল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য একটি আলাদা ইতিহাস আছে। খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তিমূলক দায়িত্বের ইতি ঘটে।
১৯৭৪-এর কমিশনের রিপোর্টের মূল প্রস্তাব, ৪টি অধিভুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-র রিপোর্টে ২টিতে নামিয়ে আনা হয়। ১৯৯২-এ শেষ পর্যন্ত এটি পরিণত হয় ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় এক কেন্দ্রিক (ইউনিটারী) প্রতিষ্ঠানে, যা ছিল বহু দিনের ও বহুজনের লালিত স্বপ্ন।
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল শিক্ষা প্রশিক্ষণের সীমিত ও করেসপন্ডেন্স কোর্স প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে এই ধরনের ও বৃহত্তর পরিধি নিয়ে কোর্স প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। আগে থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু থাকায় সেগুলি মডেলের কাজ করেছিল এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে বেতনের বিনিময়ে পূর্ণকালীন ছাত্রত্ব গ্রহণ ছাড়াই তা দিতে পারে সকল বয়সের অগণিত নারী-পুরুষকে ডিগ্রি স্তরের শিক্ষা। এর একটি বিশেষ আবেদন আছে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। শুরু করেছিল ডিপ্লোমা/ডিগ্রিস্তরের কার্যক্রম দিয়ে। এর পর সাহসের পরিচয় দেয় মাধ্যমিক (SSC) কার্যক্রম শুরু করে। ছাত্র সংখ্যায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন সবার শীর্ষে। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তুলনামূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের। বিভিন্ন কোর্স ও প্রতিষ্ঠানের আপেক্ষিক মান নির্ণয়ের জন্য। এই প্রয়োজন আরও বেড়েছে, যেহেতু নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও উন্মুক্ত এখন এত বৃহৎ পরিসরে এবং এমন এক পরিস্থিতির কাজ করছে যে, এর ফলে মান সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০-র দশকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। বিবাদমান দলগুলির মধ্যে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সংঘাত ও সংঘর্ষ, ঘন-ঘন অনির্ধারিত বন্ধ ও তজ্জনিত সেশন-জট, এ পরিস্থিতির আশু অবসান হবে, তেমন ভরসা মিলছিল না। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা, যারা পেরেছেন, ছেলেমেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় এরা গিয়েছে ভারতে ও আমেরিকায়।
অবস্থা যখন এ রকম, তখন দেশের মধ্যেই এক বিকল্প ব্যবস্থার কথা অনেকেই ভাবতে থাকেন। উদ্দেশ্য, এমন এক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, যা হবে প্রচলিত উপনিবেশিক সময়ে প্রবর্তিত ব্রিটিশ মডেলের স্থলে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ। মডেল পরিবর্তনেই এর শেষ নয়, মূল ধারার উচ্চশিক্ষা, যা ছিল গণমুখী ও নিম্নাকাঙ্ক্ষী, এটা ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নততর ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি ছিল। এগুলি উচ্চ হারে বেতন দাবি করেছে, তবে ক্ষতিপূরণ করেছে নির্দিষ্ট সময়ে ফল দিয়ে। এর শিক্ষাক্রমিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ। বর্তমানে ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্সগুলি চালু রয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর একপেশে চরিত্র ধরা পড়বে; কিছু বাণিজ্যবিষয়ক কোর্স, কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংরেজি, পরিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি। সংক্ষেপে, এ যাবৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, বাজারের কিছু উচ্চ বেতনের দাবিদার তরুণ কর্মকর্তা তৈরির জন্য শিক্ষা। যে সংকীর্ণ কর্মসূচি নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে, তার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হলে এদেশের জন্য তা ক্ষতিকর হবে।
ইতোমধ্যে প্রায় এক দশকের কার্যক্রমের পর বলা যায় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রভাব পড়েছে মূল ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, এরা এখন ওদের অনুসরণে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্সের দিকে ঝুঁকেছে। এ মুহূর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গোষ্ঠীর অবস্থান হলো, একটি প্রধান ব্যবস্থার প্রান্তবর্তী একটি অপ্রধান ব্যবস্থা। ইচ্ছায় হোক বা অবস্থার গতিকেই হোক, এগুলি এখনও নিজেদের মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। মঞ্জুরী কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এদেরকে সদস্যভুক্ত করেনি। কৌতূহলের বিষয় এই যে, ইউ.জি.সি-র অনুমোদন ক্রমেই এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ও ইউ.জি.সি-র আরোপিত কয়েকটি মৌলিক নিয়ম মেনে চলা এদের জন্য বাধ্যতামূলক। ১৯৯২-এর আইনই দিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ, কিন্তু এই আইন ব্যতিক্রমী। পরীক্ষামূলক কাজের প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু নতুনের প্রবর্তনীয় ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ব্যতিরেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর নামের অপলাপ মাত্র।
একটা শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমিকভাবে গড়ে উঠেছে, যার সূত্রপাত হয়েছিল পরাধীনতার কালে। শতাব্দীকাল এর অবয়বে ছিল বৈদেশিকতার ছাপ। ধীরে ধীরে স্বজাতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় উপাদানসমূহ স্থান পেয়েছে এর শিক্ষাক্রমে। ইংরেজির আধিপত্যের জায়গায় জনগণের ভাষা বাংলার ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও ইংরেজির আবশ্যকতাও স্বীকৃত হয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো জাতীয় শিক্ষার সঠিক দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের সম্মতি। সরকারি সেক্টরের পাশাপাশি একটি বেসরকারি সেক্টর এখনও আছে, বিশেষত মাধ্যমিক স্তরে। কিন্তু এ স্তরেও সরকারের অংশিদারিত্ব বেড়ে চলেছে এবং ক্রমেই অধিকতর অর্থবহ হয়েছে। উচ্চশিক্ষাঙ্গনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটা এবং আরও কিছু নতুনত্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ব্যবস্থাটি কোনক্রমেই সুস্থ নয়। এক অন্তঃশীল গতিশীলতা কাজ করে চলেছে, যার প্রকাশ ঘটছে শুধু ভাবের ও চিন্তার স্তরে নয়, সংস্কার ও পরীক্ষামূলক কাজের স্তরেও। এ মুহূর্তে এ এক সাধারণ প্রত্যয় যে, একটি স্বাধীন জাতির সার্থকতা অর্জনের একমাত্র পথ শিক্ষা। [আবদুল মমিন চৌধুরী, কে.এম মোহসীন, রচনা চক্রবর্তী এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী]
গ্রন্থপঞ্জি S Mahmood, A History of English Education in India, Aligarh, 1895; Nathan Committee Report, Calcutta, 1912; Calcutta University Commission Report, Calcutta, 1917; Niharranjan Ray, Bangalir Itihasa, Adi Parba, Calcutta, 1356 BS, 1402 BS; PN Banerjee (et al), Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta, 1957; A Karim, Social History of the Muslim in Bengal, Dhaka, 1959; Commission on National Education Report, Government of Pakistan, 1959; AR Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal 1757-1856, Dhaka 1961 & 1977; MA Rahim, Social and Cultural History of Bengal, 2, Karachi, 1967 and The History of the University of Dacca, Dhaka 1981; RC Majumdar, History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971; Rachana Chakraborty, Higher Education in Bengal (1919-1947): A Study of its Administration and Management, Calcutta, 1996; ZR Siddiqui, Visions and Revisions: Higher Education in Bangladesh, 1947-1992, Dhaka, 1997.
